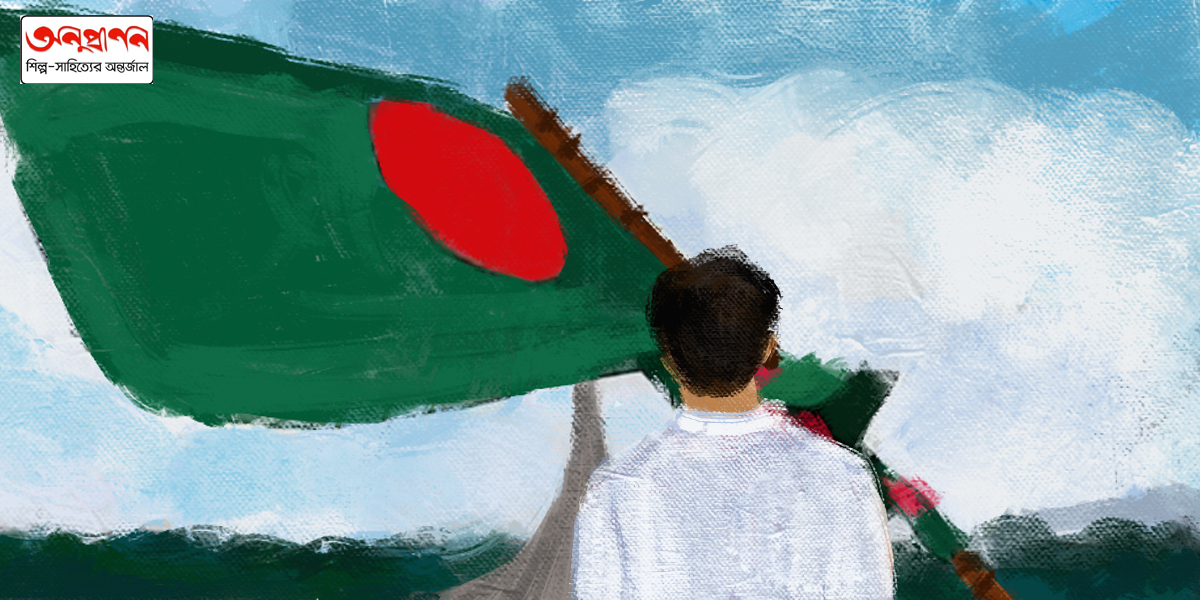
বিজয় দিবস এলে আমার মনে অনেক গল্প আর হাজারটা প্রশ্ন ভিড় করে। আলাদা করে আরও একটি প্রশ্নও ঘুরপাক খায়। বিজয় দিবস কি সত্যি আমাদের সকলের বিজয়ের দিন কিংবা স্বাধীনতা দিবস কি আমাদের সকলের স্বাধীনতা দিয়েছে?
তখন আমাদের সাত আট। মুক্তিযুদ্ধের তখন পাঁচ-ছয়। তখন আমরা গল্পস্বল্প বুঝি। তখনো আমাদের দিদিমা, বাবা-মা, প্রতিবেশী কাকি, জেঠি, ঠাকুরমাদের মনে মুক্তিযুদ্ধ যা তাদের ভাষায় সংগ্রামের স্মৃতি জ্বলজ্বল করে জ্বলে। তারা গল্প করেন আমাদের সাথে, পাড়া প্রতিবেশীর সাথে। তারা গল্প করেন বাড়িতে কোনো আত্মীয়স্বজন এলে। একই গল্প বছরের পর বছর ধরে বলে চলেছেন তারা। একই গল্প আমরা তিন চার পাঁচ বছর বয়স থেকে শুনে এসেছি। শুনতে শুনতে আমরা নিজেরাও ঐসব গল্পের ভেতরে ঢুকে যেন গেছি। যেন আমরাও সেসব গল্পের এক এটা চরিত্র। মনে হতো এবং সেই একই গল্প পঞ্চাশ বছর ধরে শুনতে শুনতে আজও মনে হয় আমরাও যেন মা, দিদিমা, বাবা, কাকা, জেঠা ও প্রতিবেশীদের সাথে সেইসময়ের সবকিছু নিজের চোখে দেখেছি। যেন এখনো সবকিছু আমাদেরও চোখে ভেসে ওঠে।
সেবছর বৈশাখ মাসের শেষ। মানে সময়টা তখন মে মাসের মাঝামাঝি। আমাদের আনন্দপুর গ্রামের মানুষ এতদিন খালি শুনেছে— দেশে পাঞ্জাবি হায়েনারা এসেছে। নির্বিচারে মানুষকে গুলি করে মারে। বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। মেয়ে, বউদের ধরে নিয়ে যায়। তারা শোনে আর ভয়ে ভয়ে থাকে। ভয়ে ভয়ে থাকে আর ঘর-গেরস্থালির কাজ করে। হাওরে তখন বোরো ফসল পেকেছে। সোনার ধানে ভরে আছে খেত। এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষের বলতে গেলে ঐ একটাই ফসল তোলার মৌসুম। কিন্তু সোনার ফসলও তাদের আনন্দ দিতে পারে না। কখন কী হয় এই আতঙ্কে মানুষ হাসতে ভুলে গেছে।
ফসল তোলা শেষ। গোলা ভরে গেছে ধানে। গাছে আম পাকার গন্ধ। কিন্তু পাকা ধান ও আমের গন্ধ কাউকে মাতাল করে না। উঠানে উঠানে সন্ধ্যা রাতে অন্ধকারে বসে আলোচনা হয়। কোথায় যাওয়া যায়? হানাদার পাঞ্জাবির হাতে ধন মান প্রাণ দেওয়ার থেকে পালিয়ে যাওয়াই কি উত্তম নয়? দেশের মানুষ নাকি পাকিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। কিন্তু আনন্দপুর গ্রামের কারও সাহস নেই যুদ্ধে যাওয়ার। কেউ জানেও না কীভাবে কোনপথে গেলে কার কাছে গেলে যুদ্ধের ময়দানের খবর পাওয়া যায়। পাশের গ্রাম উজানীগাঁও। সেখানে সাত্তার রাজাকার এক ত্রাসের নাম। কে রাজাকার আর কে নয় সেও তো কেউ জানে না। গ্রামের সাহসী তরুণেরা তাই নিয়ে খুব ভাবে। ভাবে প্রায় সকলেই। ভাবতে ভাবতে একদিন তারা শোনে যে উজানীগাঁওর পরের গ্রাম সাতবাড়িয়ায় পাঞ্জাবিরা এসে গেছে। সেদিন রাতে সাতবাড়িয়া গ্রামে আগুন লাগিয়েছিল সাত্তার রাজাকার। আগুনের লেলিহান শিখা তখন আকাশ স্পর্শ করতে মত্ত। আর কোনো পরিকল্পনা নয়। যে যার ঘরে বসে রুদ্ধশ্বাসে গাট্টি-বোঁচকা বাঁধে। যা না নিলে না হয় তার যতটুক নেওয়া যায়— কিছু কাপড়চোপড়, কাঁথা-বালিশ, থালাবাসন, সোনাদানা, টাকাপয়সা গ্রামের মানুষের কাছে কীইবা আর ছিল? তাও যতটুকু ছিল কোমরের খুঁটে বা জামার পকেটে বা আঁচলের গেরোতে বেঁধে বাচ্চা-বুড়া সকলকে নিয়ে জোয়ান মানুষেরা পথে বের হয়।
দিদিমারা সেই পথের গল্প করেন। গ্রামের পর গ্রাম, নদীর পর নদী, হাওরের পর হাওর, পাহাড়-টিলা পেরিয়ে কী করে তারা পৌঁছালেন মেঘালয় সীমান্তের মৈলাম কাম্পে। এক ত্রিপলের তলায় পঞ্চাশটি পরিবারের সহাবস্থান, ভাবা যায়! খোলা আকাশের নিচে তিনটি পাথর দিয়ে চুলা বানিয়ে আলু সেদ্ধ ভাত রান্না হচ্ছে। সেজন্য আমার মা-সহ অনেক নারীকে ছুটতে হচ্ছে লাকড়ির জন্য টিলায়, পানি সংগ্রহের জন্য ছড়ায়। সকলের পেট ক্ষুধায় জ্বলছে। ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে সেই বালিমাখা আলুসেদ্ধ-ভাত তখন অমৃত।
এসব গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে মাকে জিজ্ঞাসা করে প্রতিবেশী মামি— তারপর মৈলাম ক্যাম্প থাকি তুমরা কই গেছলায়?
বালাট ক্যাম্পোগো। তুমরা কৈ আছলায়?
বালাট ক্যাম্পোই। ছয় নম্বরে। আর তুমরা?
আমরা? আমরা আছলাম তিন নম্বর। ওখানো ত্রিপলের তলায় নায়গো দিদি।ছাতার পাতার ছাউনি আর বাঁশের বেড়ার ঘর আছিল। বাঁশের মাচাঙও আছিল ঘুমাইবার লাগি। তুমরারও আছিল নি?
অয় অয়, আমরারও ইলাকানই আছিল।আর জানোনি, দুই দিন পরে পরে আগুন লাগতোগো বইন। তুমরার লাগতো নি? ছড়ার পানি খাইয়া কলেরা অইয়া কত মানুষনু মরছইন। একজন মরছইন তেই শ্মশানো লইয়া গিয়া বাড়িত আইত না আইতে আরকজন শেষ। মাইগ্গো মাই কী দিন যে গেছে!
অয়গো সোনা। আমার বাপরেওনু বালুর তলে থইয়া আইলাম। মামির চোখে জল।
অয়গো বইন, এমলা হক্কলের ঘরই। কেউঅই আর আনাম আইতা পারছইন না। কেউ না কেউরে বালাটর বালুর তলে থইয়া আওন লাগছেউ। আমার মার পেটের ভাই, কাকা, কাকি, কাকার এক পুরি লইয়া চাইরজনরেনু থইয়া আইছইন গো। ইলাকাননু পরায় মাইনষের অইছেগো বইন।
অয়গো। মানুষ গেল। খেতের ধান গেল। তামা কাঁসা, ঘরের টিন গরু-বাছুর সব গেল। কী সংগ্রাম যে আইছিল গো বইন। সংগ্রাম কত মানুষরে শেষ কইরা দিল। কিন্তু তাও তো পোড়াবাড়িখান আইয়া পাইছি। যখন বাড়িঘর সহায় সম্পদ ফালাইয়া গেছলাম আশা করছিলাম না আর কোনোদিন নিজের দেশো ফিরৎ আইমু।
অয়গো বইন। যা গেছে তো গেছে। নিজের দেশো আইছি। স্বাধীন দেশো আইছি, ই বড় শান্তি।
আমাদের মা মাসি কাকি জেঠি ঠাকুরমা দিদিমারা সাধারণ মানুষ।দেশের খবর কিছু রাখতেন না। তাই স্বজন হারিয়েও স্বাধীন দেশে ফিরে নিজে পোড়াভিটায় ঠাঁই পেয়েও তাদের শান্তি। তারা বুঝতে পারেন না স্বাধীন দেশ অচিরেই স্বাধীন দেশের কিছু মানুষের দ্বারাই লুট হয়ে যাচ্ছে। সোনার ফসল কৃষকের চোখ জুড়িয়ে প্রাণ ভরিয়ে দেয় কিন্তু তাদের পেট ভরাতে পারে না। বছরের পর বছর যায়। শহরের চেহারায় চাকচিক্য বাড়ে। চাকচিক্য বাড়ে গ্রাম গ্রামান্তরেও। তবে সব মানুষের বাড়ে না। তারা ক্রমশ মলিন হয়। কিন্তু কিছু মানুষের এই চাকচিক্য আরও কিছু মানুষকে ক্রমশ লোভী করে তোলে। নগরে বন্দরে গ্রাম গ্রামান্তরে তারা আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়। ব্যবসা বাণিজ্য চলে দেদারসে। ব্যবসা হয় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। রাজাকারের বাচ্চাও মুক্তিযোদ্ধা বনে যায়। বছরের পর বছর তারা মুক্তিযোদ্ধার ভাতা নেয়। আসল মুক্তিযোদ্ধা পথে পথে ভিক্ষা করে।
আমাদের দিদিমা ঠাকুরমারা আজ আর কেউ নেই। মা জেঠি কাকি মামিরা কেউ কেউ আছেন। কেউ কেউ নেই। আজকাল ঘরে ঘরে টেলিভিশন। টেলিভিশন খুললেই চৌদ্দই ডিসেম্বর, ষোলোই ডিসেম্বর, ছাব্বিশে মার্চ উপলক্ষে যুদ্ধ দিনের ছবি ও প্রামাণ্য চিত্র দেখায়। শরণার্থীর মিছিল দেখায়। দেখায় কুঁজো হয়ে চলা বুড়ি, উদোম গা শিশু, স্তন্যপানরত শিশু কোলে মা, জোয়ান লোকদের মাথায় বোঁচকা নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে মানুষ। এসব দেখে তাদের সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। স্বজন হারানোর বেদনায় তারা আজও ম্রিয়মাণ হন। তখন কখনো আপন মনে কখনো পরিবারের নতুন মানুষগুলোর সাথে, প্রতিবেশির সাথে, বাড়িতে আসা নতুন আত্মীয়-কুটুম্বের সাথে সেই দুঃখময় দিনগুলোর গল্প বিনিময় করেন। তবে তারা রণাঙ্গণের যুদ্ধ দেখেননি। আমাদের গৌরব আমাদের অহংকারের মুক্তিযুদ্ধের বীরশ্রেষ্ঠ, বীরবিক্রমদের অমিত সাহসের, আত্মত্যাগের ও শত্রু নিধনের গল্প তারা সেভাবে জানেন না। তারা জানেন একদল বিদেশি হায়েনা আর এদের এদেশীয় দোসর রাজাকার আলবদররা এদেশের নিরীহ মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। মেয়েদের লাঞ্ছিত করেছিল। সম্পদ লুটেছিল। বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করেছিল। সেজন্য তাদের জীবন ও মান সম্ভ্রম বাঁচাতে পালাতে হয়েছিল বাড়িঘর সহায় সম্পদ ও দেশ ছেড়ে। তারা শুনেছিলেন দেশের সাহসী মানুষেরা যুদ্ধ করছে। একদিন তারা আবার দেশে ফিরে আসবেন। নিজের ভিটেমাটিতে ফিরে আসবেন বলে অধীর আগ্রহে শরণার্থী শিবিরের দুঃখ কষ্ট ও অভাব অনটনের যন্ত্রণা এবং কলেরা আমাশয়ে স্বজন হারানোর বেদনা সয়েছিলেন। তাই যখন শুনেছিলেন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, ফিরে এসেছিলেন এই মাটিতে। যার যার পোড়াভিটায়।
সেই পোড়াভিটায় ঘর তুলে ফল ফুলের গাছ লাগিয়ে আবার বছরের পর বসবাস করেছেন সুরধুনী। তার ছেলে এখানে বড় হয়েছে। সেই ছেলের বিয়ে হয়েছে তার ঘরেও আবার ছেলের জন্ম হয়েছে। তবু স্বাধীন দেশে আবার সেই বাড়ি ছেড়ে যেতে হলো তাকে। সুরধুনীর বাড়ি ছিল গ্রামের প্রান্তে। ছেলেটা বিদেশে থাকে। তার পাশের বাড়ির আসকর আলী সাত্তার রাজাকারের আত্মীয়। শরণার্থী শিবির থেকে ফিরে আমরাও শুনেছিলাম সেই আসকর আলী সাত্তার রাজাকারের লুটপাটের সাগরেদ হয়েছিল। শুনেছিলাম আমাদের যে দুধাল ধলা গাইটা ছিল বাছুরসহ তাকে নিয়ে গিয়েছিল আসকর আলী। আমাদের সেই প্রিয় ধলা গাইটাকে জবাই করে সে তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ফুর্তি করে খেয়েছে। দেশ স্বাধীনের পর কিছুটা ভয় পেয়েছিল বলে আমাদের সেই বাছুরটা সে ফেরৎ দেয়। কিন্তু শীঘ্রই অবস্থা পাল্টে গেল। আস্তে আস্তে একসময় তাদের সেই ভয় গেল কেটে। তারা পুনর্বাসিত হতে লাগল। ক্ষমতার অংশ হলো। বদলে যেতে লাগল দৃশ্যপট। তাই তো সুরধুনীও আর থাকতে পারেননি নিজের বাড়িতে। প্রথমে শুরু করেছিল একটু একটু করে জায়গা ঠেলা দিয়ে। তারপর একটু একটু করে সে সুরধুনীর বাড়ির এক তৃতীয়াংশ দখল করে নিল। না, কেউ কিছু বলেনি। তার সাত সাতটি লাঠিয়াল ছেলে। সে যে রাজাকার ছিল একথা কেউ বলে না কিংবা এ যে তার অপরাধ ছিল সেকথাও কেউ আর মনে রাখেনি। শেষপর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়াল যে সুরধুনী অবশিষ্ট বাড়িটুকুও ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।
সেই একাত্তরের শরণার্থী শিবিরে, সুরধুনীর ভাই— যে কিনা অনেক আগে থেকেই ইন্ডিয়ার নাগরিক হিসেবে স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল, এসেছিল তাদের সকলকে নিয়ে যেতে। সুরধুনী ও তার পরিবার দেশের মায়ার টানে ভাইয়ের সে ডাক শোনেনি। ফিরে এসেছিল। বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার দিন তুলসীতলার এক খাবলা মাটি আঁচলে বেঁধে আছড়ে-পিছড়ে কেঁদে সেসব কথাই বারে বারে বলছিল সে।
সুরধুনীর ভিটে ছেড়ে যাওয়ার দিনটি ছিল বিজয় দিবস। প্রায়ই ভাবি। কিন্তু ভেবে ঠিক করতে পারি না বিজয় দিবসে নিজের ভিটে থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়া কি সুরধুনীর পরাজয় ছিল, নাকি ছিল আমাদের বিজয়ের পরাজয়! প্রতি বছর বিজয় দিবস আসে আর যায় আর আমার মনে প্রশ্নটাই কেবল উঠাপড়া করে। কিন্তু সেখান থেকে কোনো উত্তর আসে না।
