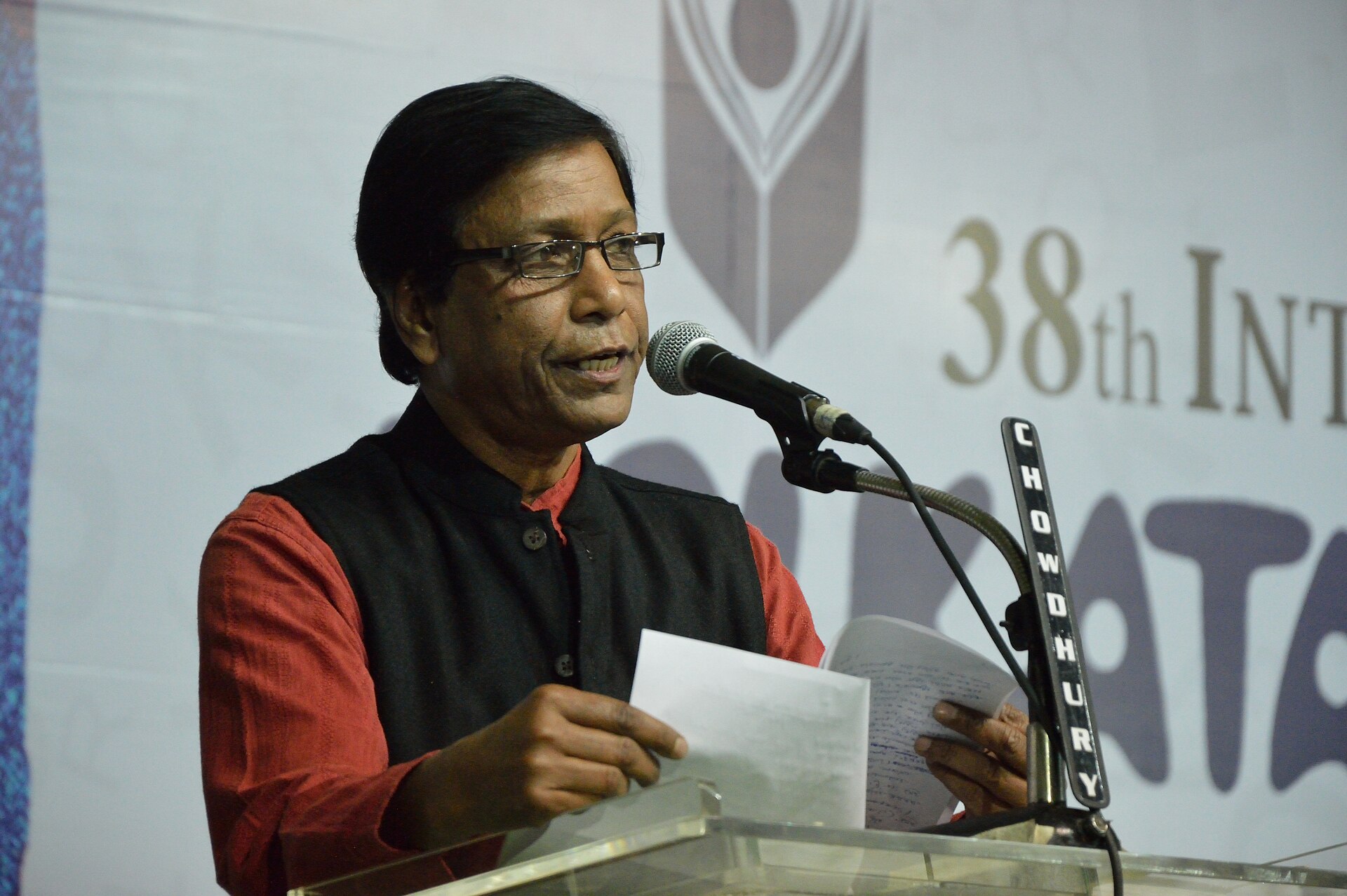
কবি রণজিৎ দাশঃ একটি ব্যক্তিগত পাঠপ্রয়াস
মণিপদ্ম দত্ত
অশ্রুর দেবতা আজ
ক্রমশ ঈশ্বর হয়ে উঠে
দৃষ্টি দান করে।
চিনতে পারি
অশরীরী শব্দমালা।
লিপিবদ্ধ চরাচর জুড়ে।
ইচ্ছেমত ফিরে যাই
পৃথিবীর গর্ভস্থ শিকড়ে।
মৎ প্রণীত
আমার ভাল লাগা, সীমাবদ্ধতা, সংলাপ, ও সংক্রমণ
শুরুর পংক্তিচয় কবি রণজিৎ দাশে র কবিতা পাঠের নির্যাস বলা যেতে পারে। অন্য রকম ভাবে বলা যায়, আমার কলমে কবির জগত কী ভাবে উঠে আসে বা আসতে পারে, তার আভাষ। রণজিৎ কে পড়ছি বেশ কিছু কাল ধরে। মূলত মুগ্ধতার সাথে। এবং তাঁর কবিতার পাঠক হয়ে ওঠার অনুভবি অভিজ্ঞতার সারাসার। এ লেখা কোন সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে লেখা নয়। এটি একটি নিখাদ পাঠ-প্রয়াস। আর ব্যক্তিগত জগতে জীবনানন্দের উচ্চারণের অন্ধ উত্তরাধিকারী। ‘বরং তুমিই না লেখো একটি কবিতা’। অবশ্যই কবিকে নিয়ে লেখার ব্যাপারে আমার কিছু সমস্যা আছে। আমি রণজিতের ভক্ত পাঠক। ফলে যে দূরত্ব আমাকে খানিকটা নির্মোহ করতে পারত তার সম্ভাবনা অনুপস্থিত। রণজিৎ এর সৃষ্টিকে মহত্তর করার দায় নেই আমার, কারণ এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। এই ভেবে এই লেখার শুরু। পাঠককেও এটি মনে রাখা জরুরি। নচেৎ কিছু অনভিপ্রেত প্রশ্ন ভীড় করবে। একজন তন্নিষ্ঠ পাঠক হিসেবেই বরং লিখেছি। কবিকে যতটা বেশি চিনে নেওয়া যায়। এটাই তো পাঠকের কাজ। এবাং এই প্রক্রিয়াটা কবির পাঠক-কুলের পক্ষেও প্রয়োজন। কী ভাবে একজন পাঠক হিসেবে আমি তাঁর কবিতা যাপন করি সেটুকুই ভাগ করে নেওয়ার জন্যে এই লেখা ও তাঁর উপক্রমণিকা । কবি তো নিজেই লিখেছেন-
এই অন্ধকার গ্রামে, কুপি জ্বেলে, পাঠকই কবিতা। (হাডুডু খেলার মাঠ/ ঈশ্বরের চোখ)।
কী অমোঘ উচ্চারণ! আজকের ভারত ও দুনিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে । মুল কবিতার অভিঘাত সময়ের ছাল ছাড়িয়ে আজকের দরজায় হানা দ্যায়। আজও তো একটি গরীব মেয়ে তৃতীয় পঙক্তির মতই হাঁটে, হাঁটতে হয়। আসমুদ্রহিমাচল। হেঁটেই চলেছে। কবির সাথে আমরাও দেখি। মনুবাদের জল্লাদ আজও আমাদের জীবনযাপন নিয়ে হাডুডুই খেলে । আমার রণজিৎ এভাবেই কাল অতিক্রম করেন। এভাবেই পাঠকের সাথে তাঁর সংলাপ গড়ে ওঠে। পাঠক কবিতা পড়ে, কবি পড়েন পাঠক। রণজিৎ পাঠে এই বিষয়টি বারম্বার মনে পড়ে। আমি ক্রমশঃ এক সংক্রমিত পাঠক হয়ে উঠি।
ফিরে যাওয়ার পথের ধারেই কবির বাড়ি
শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের গানের পংক্তি একটু বদলে নিলাম। ‘কবিতা তো কৈশোরের স্মৃতি । সে তো ভেসে ওঠা ম্লান আমার মায়ের মুখ; ………আব্বার ফিরে আসা, সাইকেলের ঘণ্টাধ্বনি- রাবেয়া, রাবেয়া।‘ (আল মাহমুদ, ‘কবিতা এমন’ /সোনালি কাবিন।) কবিতা যে শুধুই নস্টাল্জিয়া নয় আমারা জেনে গেছি । প্রকৃত পক্ষে ফিরে আসার ব্যাপারটাও নস্টালজিয়া দিয়ে পুরো ব্যাখ্যাত হয় না। মিলান কুন্দেরার কথা ধার করে বলা যায়, এই ফিরে আসার পরিভ্রমণটা আসলে স্মৃতি উদ্ধারের যুদ্ধ । কবিও তো এই যুদ্ধটাই করেন। সব সৃষ্টিশীল মানুষকেই তা করতে হয়। ফিরে আসার পথের ধারেই ঘর বাঁধতে হয় তাঁকে। ব্যাক্তিগত স্মৃতি খনন প্রক্রিয়ায় আত্মচেতনাকে আত্মমেহনের অন্ধ গলি থেকে উদ্ধার করে জনসিন্ধুর চেতনানুভবে অনুরণিত করে তোলাটাই কবিতা নির্মাণ কর্মসূচি । ‘কবিতার মুহূর্ত’ তে শঙ্খ ঘোষ বোধ হয় এই কাজটি ই করে দেখিয়েছেন। শঙ্খের জবানিতেঃ
‘ কবিতার মধ্য দিয়ে তাই পিছনের দিন গুলিতে একবার ফিরে যেতে থাকি। যেতে যেতে দেখি একটা পথরেখা চিহ্নিত হয়ে আছে, কিছু বা ব্যাক্তিগত কিছু বা ঐতিহাসিক স্মৃতি তে মিলেমিশে যাওয়া এক সময়পথ। কেবল সম্ভাব্য পাঠক কে মনে রাখতে বলি, সে পথের অনুসঙ্গে যে কথাগুলি এসেছে এখানে, সেটাই কবিতাগুলির পরিচয় নয়, সে হল এর সুচনাবিন্দু মাত্র। ‘
রণজিৎ কে পড়তে গিয়ে এই পাঠ পরিবর্তিত হয় নির্মোহ, সতর্ক ঘন্টাধবনিতে। কবি এই স্মৃতি উদ্ধারের কথোপকথোনের প্রতি বাঁকে অনেকটা প্রায় ব্রেখটিয় কায়দায় সতর্কবাণী তৈরি করেন। অন্যভাবে বললে, কবিতা প্রদক্ষিণের দ্রাঘিমা জুড়ে এই বাঁকগুলিই তাঁর কলমে কবিতার অনুপরমাণুর যোগান দ্যায়। ‘মৌলপ্রতারণাজাত’ সম্পর্কের নিহিত বেদনা ফিরে ফিরে আসে ও আমাদের প্রহার করে। কাব্য সংজ্ঞা বিস্তৃত হয়। তাঁর পাঠকের চক্ষুদান ঘটে। কবি আমাদের ঈশ্বরের চোখে দৃষ্টি রেখে মনে করিয়ে দ্যান, ‘কামিনী ফুলের গন্ধে সত্য আছে, ছলনাও আছে’। এই দ্বান্দিকতাই, আমার কাছে, কবি রণজিৎ দাশের কাব্য বিজ্ঞান হয়ে পৌঁছয়।
কবিতার পাঠক – এক শুদ্ধ, নির্জন, অলৌকিক মানুষ ।(রণজিৎ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রথম সংস্করণের ভুমিকা, দে’জ পাবলিশিং)। এই উচ্চারিত কবিমানস একটা স্পষ্ট বার্তা দ্যায়। পাঠক স্বস্তি পায়। কবিতা তাঁর জন্যেই লেখা হচ্ছে। পাঠক-ই কবির সৃষ্টি-বৃত্তের কেন্দ্রে রয়েছে। এই ঘোষণা কবির নিজস্ব ম্যানিফেস্টো যা এখনও তাঁর কাব্যকৃতিতে সততই বহমান। তিনি তা কখনই বিস্মৃত হন না। তাঁর দীর্ঘ পথপরিক্রমায় একটি সেরা উচ্চারণ বোধ হয় ‘ প্রতিটি মুহূর্ত ডাহা অলৌকিক’। (প্রতিটি মুহূর্ত, ঈশ্বরের চোখ।) কবিতা যে মুহূর্তের অলৌকিক লিপিবন্ধন এই বোধে পাঠকে জারিত হয়। তার মনও কবি হয়ে ওঠার উৎসাহ পায়। কবি-পাঠক সম্পর্ক দানা বাঁধে। আমি এই পাঠক-বান্ধবতার সরল বৈশিষ্ট্যটিকেই সামনে রেখে রণজিৎ এর অন্তরকে স্পর্শ করে থাকতে চাই।
কবির বাংলা কবিতার অঙ্গনে প্রবেশ যেই সময়ে যখন অসংখ্য প্রতিষ্ঠিত কবির উজ্জ্বল উপস্থিতি। কবি কিছুই কম পড়ে নাই। বিভিন্ন বিদগ্ধ পদচারণ সময়কে উদ্ধত রেখেছিল। লাজুক কবিতা নিয়ে রণজিৎ এর আগমন আসলে কিন্তু এক বিনম্র ছদ্মবেশী বিপ্লবের মত। ‘আমাদের লাজুক কবিতা, তুমি ফুটপাথে শুয়ে থাকো কিছুকাল’। কিছুকাল শব্দটি লক্ষণীয়। কারণ ধীরে ধীরে শীঘ্রই কবিতার মুখে পৃথিবীর তামাটে আভার অর্জন দেখে ‘ফুটপাথ শিশুরা ভারি ঝলমলে হাততালি দেবে’ । কবির আকুতি ‘তাদেরকে দিও তুমি ছন্দজ্ঞান, লজেন্স দিও না’। বড়ো মায়াময় আর প্রত্যয়ী এ উচ্চারণ। আজ পর্যন্ত কবি আমাদের লজেন্স সরবরাহ থেকে বিরতই থেকেছেন। সাম্প্রতিক কালের লেখায়ও, এত দীর্ঘ পথশ্রমের পরও তিনি বলতে পারেন ‘এই তো সংসার ।/ কোমলতার বর্ম পরে , কঠিনের সঙ্গে/ লড়াই দুর্বার’। ( শিশুর কোমল দুটি পা, অশ্রুর দেবতা)। এখানে আমি কবিকে তাঁর সময়ের কবিদের থেকে ভিন্ন উচ্চারণে দেখি। এই যে কোমলতার বর্ম পরে কঠিনের সঙ্গে লড়াইটা আমাকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। অনেক ফলিত অহঙ্কার যাত্রার পর ব্যাক্তি আমি শিখি এভাবেও ভাবতে পারতাম। জীবনের অপূর্ণতা প্রকট হলেও এই সায়াহ্নে কিছু স্বস্তি দ্যায় বৈকি । কোমলতার বর্মবিহীন যুদ্ধ ‘কেমন শূন্য মনে হয়’। মধুবংশীর গলিতেও সিন্ধু বারোয়াঁর তান বেঁচে রাখায় আমাদের। পৃথিবীর এহেন প্রতিহিংসার আবহে অক্ষ শক্তির সঙ্গে লড়াইয়ে যুদ্ধাস্ত্রের তূণে একটুকরো কোমলতার বড় প্রয়োজন আজ। ইতিহাস জেনেছে এর অভাব ও পরিনতি। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধের মর্মবাণীই যেন উচ্চারিত হয়। ‘অশ্রুর দেবতা’ তো রবীন্দ্রনাথ-ই । এখানে এসে অবধারিত ভাবেই রণজিৎ এরই একটি কথা মনে পড়ে যায়। তিনি নিজেকে আধুনিক কবি বলতে স্বস্তি পান না। এটাও ভাবায় আমাকে। ইনি কবি। শুধুই কবি। কবিকে সংজ্ঞায় বেঁধে রাখাটা অমুলক মনে হয়। সাত্যি ই তো কবি যদি কবিই হন, কাল গুন্ডী তো তাঁর সীমারেখা হতে পারে না।
কবির নিখিল চাহিদা
স্মৃতিচারণে কবি জানিয়েছেন শক্তি চট্টপাধ্যায়-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের শুরু ‘নিখিল চাহিদা’ ধরে। শক্তি ঐ শব্দদ্বয়ের ব্যাবহার দেখে চমকিত হয়েছিলেন, আকৃষ্ট হয়েছিলেন তরুণ কবির প্রতি। শব্দ ব্যাবহারে সে কালে, হয়ত এখনও, শক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রণজিৎ নিজেও বলেছেন, ‘প্রতিটি শব্দই ডাহা অলৌকিক’। শব্দ যে কবিতার প্রাণ এ আর নতুন কথা কী? আমার কাছে অবশ্য এটি এর চেয়ে বেশি বার্তা বয়ে আনে যখন দেখি তাঁর ব্যবহৃত শব্দরা বহু সময়ই প্রতিজ্ঞা হয়ে যায়।
‘আল্লা মেঘ দে ‘গাইলে যতটুকু নিখিল চাহিদা ফুটে ওঠে
নীলাঞ্জন তারও চেয়ে বেশি ………
সেজন্যেই আমি আজ শুদ্ধ অভিধান ছুঁয়ে শপথ জানাবঃ
প্রতিতি শব্দের নাম নীলাঞ্জন – আমৃত্যু খরা-র মধ্যে
এর কোনো বিকল্প হবে না।
এই ব্যাপারটা কিন্তু ঘটেছে এবং ঘটেই চলেছে তাঁর কবিতায়। প্রথম থেকেই। আমাদের লাজুক কবিতার কাল থেকেই। কবি শুধু শব্দের নির্মাণের নিরাপত্তায় সন্তুষ্ট না থেকে স্পষ্ট ভাবেই তাঁর অবস্থান ঘোষণা করেন। প্রথম লগ্ন থেকেই এই প্রত্যয়ী কবিকে পরিচিত-ও লাগে। প্রতিটি শব্দ নীলাঞ্জন হয়ে উঠতে চায় কবির নীল নির্জন হাত ধরে। বেরিয়ে আসে এইরকম আশ্চর্য পংক্তিমালা-
‘লঙ্কা পোড়ার গন্ধে বুড়ির ব্যাক্তিগত সঙ্ঘ উনুন ঘিরে জেগে ওঠে, আর
ভাতের গ্রাস তুলতে গিয়ে বুড়ির হাত বারবার
পাখির ভারে বেসামাল কচি গাছের মতো কাঁপে’
সঙ্ঘ উনুন ও পাখির ভারে বেসামাল কচি গাছের ডাল । পাঠকের চাহিদার নিখিল ব্যাপ্ততর হয়। আসলে লজ্জা, প্রেম, প্রকৃতি, কৌতুক, ব্যাঙ্গ, প্রতিবাদ, সময় সমস্ত কিছু দ্রবীভূত হয় কবির চরাচর জুড়ে। এযাবৎ তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিই এই আবহে আমাদের কাছে পৌঁছয়। আমাদের লাজুক কবিতা থেকেই এ যাত্রার শুরুয়াত। কিছু উদাহরণ দেওয়ার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।
১। আমূল গৃহিণী হয়ে যে আমার মর্মে বিঁধে আছে
ভীষণ অপরিচিতার সেই দীর্ঘাঙ্গীর সাথে
বার বার
মায়াভবনের পথে দেখা হয়ে যায়। (দেখা হয়ে যায়)
২। চরাচর জুড়ে তার লেলিহান আক্রনণে কতো দ্রুত পুড়ে যায়
তোমার শরীরজোড়া গৃহস্থালি, গান, মাটি, পূর্ণ ভালবাসা
শুধু পড়ে থাকে ছাই, যেন জ্ঞান, যেন শেষ কালো অট্টহাসি, আর
সৌরশ্মশানের বুকে শিলমোহরের মতো জেগে থাকে সেই দৃশ্যঃ
মায়ের মুখাগ্নি করে সন্তানের অকৃতজ্ঞ হাত। (শ্মশানছবি)
৩। আর সেই কিশোরীরা , ক্রমশ তাদের
চঞ্চল ফ্রকের ছায়া রতিপাথরের চিত্রে মিশে যেতে থাকে। (খাজুরাহ)
কিম্বা সেই অমোঘ আহ্বান
৪। সিম্বলিজম রাখো, কুলাঙ্গার, ট্রেণ-ভাড়া ফাঁকি দিয়ে চলে এসো
তরাই জঙ্গলে। (স্বপ্নে পিতামহ)
কী ভাবে তাঁর কবিতার নিখিল গড়ে ওঠে তার ভিত্ থেকে নির্মাণ প্রক্রিয়ার সাক্ষী থাকে পাঠক। চিত্রকল্প ও কবিতার রসায়ন গাঢ়তর হতে থাকে। কালের স্থানবদল ঘটে চলে অবিরাম। কবিতারা শিকড় ধরে উঠে আসে। পাতা মেলে। খাজুরাহ ও স্বপ্নে পিতামহকে বিপ্রতীপ অবস্থানে দেখি না। এই রকম বৈপরীত্বের ঐক্য রণজিৎ-এর কাব্যের এক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠতে থাকে।
নাগরিক কবিয়াল
‘জিপসিদের তাঁবু’, ‘সময়, সবুজ ও ডাইনি’ এবং ‘বন্দরের কথ্যভাষা’ এই তিনটি কাব্যগ্রন্থ আমার অনুমানে রণজিতের সৃষ্টি-পরিক্রমণে একটি বড় অধ্যায়। সময়টাও বেশ বিস্তৃত । ১৯৭৮ থেকে ৯৩। পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের রাজনীতি ও সমাজ-কাঠামোর অনেক কিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে তখন। কবিতাও ভাঙ্গছে তার শরীর। শঙ্খ-বীরেন্দ্রর ঋজুতর কাব্যভাষা তখন প্রতিষ্ঠিত। একটা নতুন আকাঙ্ক্ষা রূপ নিচ্ছে। ইন্দিরার স্বৈর শাসন ও নকশাল-বাদের কোলাহলে একটু ক্লান্ত মানুষ। এই সময়টাকে কীভাবে দেখছেন কবি? সময়ের ছাপ কীভাবে দুলছে তাঁর কবিতায়? এ সময়টা কবির এক ধরণের উত্তরণকাল যেন। ‘জিপসিদের তাঁবু-র ‘পার্কে মেহের আলি’ শুরু হচ্ছে-
পার্কে এসেছো, কিন্তু এই সন্ধ্যা ক্ষণস্থায়ী’……
অনিশ্চিত সময়ে ‘সন্ধ্যা ক্ষণস্থায়ী’। বিগত দিনগুলি আমাদের বিশ্বাসকে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে নাভিমুল থেকে। কবির উচ্চারণ ঈষৎ কষায়িত। তির্যক নাগরিক। কবির মেহের আলি কিন্তু ‘সব ঝুট হ্যায়’ বলে না। মুহূর্তটিকে অমরত্ব দিতে এই মেহের আলির আহ্বান-
পার্কে এসেছো, কিন্তু এই সন্ধ্যা ক্ষণস্থায়ী, ঠাণ্ডা, অসহায়-
যত পারো চুমু খেয়ো, লোকচক্ষু ফাঁকি দিয়ে, সুস্বাদু জিহ্বায়’।
এভাবেই কবির এক নিজস্ব ভাষা ও ভাষ্যের ইমারৎ একটু একটু করে প্রতীয়মান হয় পাঠকের কাছে। হাডুডু খেলার মাঠের অনুষঙ্গ ফিরে আসে গলফের মাঠে আমাদের একমাত্র অধিকার, বল কুড়িয়ে দেবার, অভিঘাতে।
‘পাছা ঝেড়ে ছুটে গিয়ে সেই বল
আমাকে কুড়িয়ে দিতে হয়।
এভাবেই, বলা যায়, আমিও কিছুটা গলফ খেলি’।
নাগরিক শোষণের একটি অনিবার্য চিত্রকল্পের বুনোট ঘনীভূত হয়। ‘বাবাকে’ কবিতার মধ্যে এক নিজস্ব এলিয়েনেশনের গন্ধ পাই।
‘আপনার কথা লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব।
আপনি আমার লেখার জগৎ থেকে একটু দূরে রয়েছেন,
যেমন শহর থেকে একটু দূরে থাকে পাওয়ার স্টেশন’।
ব্যাক্তিগতভাবে এই কবিতাটি আমাদের প্রায় সকলকেই এক নিদারুণ বিচ্ছিন্নতা বোধে বিষণ্ণ করে। পিতা ও সন্তানের সম্পর্কের এই দ্বান্দ্বিকতা প্রাচীন ও এক নাগরিক নিষাদ হয়ে আমাদের তীরবিদ্ধ করে। যখন সুভাষ লিখছেন ‘রাম গেছে বনবাসে, দশরথ বাপ, দুঃখ যা পেলেন, চার রাত্রেই সাফ’। রণজিৎ- এর উচ্চারণ সেখানে বেশ অন্যরকম। আজ একটা বয়সে পৌঁছে পেছনপানে তাকিয়ে দেখি, কষ্টটা বাবামায়ের বুকেই দেগেছিল বেশি। দেশের কি করতে পারিনি তাতো প্রমাণিত। তবে আপনজনকে কতটা বিপদ ও কষ্টের মধ্যে রেখে জীবনযাপন করেছি সে ইতিহাস অলিখিত আজও। কবির এই সংবেদনশীলতা, ঐ সময়ে দাঁড়িয়ে, মহত্তর মনে হয় আজ।
এই তিক্ততা যে কী অনুপম ব্যাঙ্গোক্তি হয়ে বেরিয়ে আসে ‘আপেল’ কবিতায়-
‘আপেলে কামড় দিয়ে মনে হল, চতুর্দিকে স্যানেটরিয়াম ।
……
এগারো বছর পর আজ আমি আপেল খেলাম।
খুব হাসি পেল। যদি প্রত্যহ আপেল
খেতাম, তাহলে এই জীবন সফল হতো নাকি?
এগার বছর পর আজ যেন মনে হলো-
প্রেরণা নারীতে নেই, আপেলে রয়েছে’।
এই পংক্তিচয় এক আশ্চর্য বিন্যাসে পাঠক্ কে নাগরিক চাবুক হানে। কী অদ্ভুত ক্ষুরধার আত্মদংশন! এই পরিপ্রেক্ষিতে ‘বিশ্বাসকাকু’-র একটুখানি উদ্ধৃতির লোভ সামলাতে পারলাম না।
‘তখনই সন্দেহ হবে, সূর্যাস্তের পথে যারা ছোলাভাজা খায়, তবে তারাই কি
পাখি?
নির্বাক পাথরে শুয়ে সমস্বরে হেসে উঠবো-
আবার বিশ্বাসকাকু, আবার চালাকি’।
সেই উত্তাল সময়ের কান্ডারীদের চালাকি এতো দূরে এসেও কী নির্মম পরিহাস হয়ে বুকে লেগে আছে। কবির চালাকিকে আনখ আক্রমণ তাঁকে ঋজু রেখেছে জীবনভর। পাঠকের অবয়বহীন ঘৃণা রূপ পায় এইরকম দুঃসহ পঙক্তিতে । এ কাব্য ভীষণ নাগরিক। তাই ‘কবিকে’ কবিতায় এই সত্য উঠে আসে-
‘মৃতদেহ কাঁধে তুললে কতটা ওজন –তুমি এখনও জানো না’
তাঁর প্রেমবোধও নাগরিক। কী রোম্যান্টিক অনুভুতি ছড়ানো ‘নার্স’ কবিতাটিতে।
‘পুরোপুরি সেরে উঠলে ডিসচার্জড—
সেই ভয়ে ভয়ে
বাকিটা জীবন তাই
অর্ধেক অসুখ নিয়ে হাসপাতালে থেকে যেতে হয়’।
প্রকৃতপক্ষে ‘জিপসিদের তাঁবু’ কাব্যগ্রন্থ একটি অদ্ভুত সংকলন। জিপসিদের মতোই কবিতা ক্ষণে ক্ষণে তাঁবু বদল করে। এই কাব্যগ্রন্থটিতে একটু অদ্ভুত পাগল-পাগল বিভোরতায় পাঠক সংক্রামিত হয়ে পড়ে। কবিও আমাদের নিয়ে একটু খেলাই করেন। অবশ্য এই প্রবণতা রণজিৎ-এর এক স্বভাব বৈশিষ্ট্য যেন। প্রতিটি কবিতাই যেন এক একটি স্বতন্ত্র অনুভবের দলিল। কবির যাপিত দর্শন-ও। আমার পাঠের সমর্থনে কয়েকটির উল্লেখ জরুরি। শীর্ণ ছায়া, পাঁচ পংক্তিতে যে গভীর বোধ উঠে আসে তা পরবর্তী কালের ‘অশ্রুর দেবতা’-তে ভালবাসা নিবেদনে ধর্ম হয়ে উঠবে; যার উল্লেখ আমি আগেই করেছি। কবি লিখছেন-
সমস্ত মুক্তির পথে অন্ধ ভিখারির মতো
ভালবাসা ঠায় বসে থাকে।
পথের ওপরে তাঁর ক্ষুদ্র, শীর্ণ ছায়া
নিঃশব্দে ডিঙ্গিয়ে যেতে হয়।
সমস্ত মুক্তির পথে, এতুকুই, মূল পরিশ্রম।
তার পরেই পাই বিচ্ছেদবীজ।
যত শক্ত করে বাঁধো অন্তর্বাস,
চোখের ইঙ্গিতে খুলে যায়।
………এই দেহ, সম্পূর্ণ সন্দেহ।
‘অনুসরণ’-এ
মাটি ও সূর্যের মধ্যে যে ক্ষুদ্র শেফালিশাখা, তাই বেয়ে বেয়ে
শুঁয়োপোকাটির সঙ্গে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছি, ঠিক তারই মতো
স্থূল ও মন্থর, ও পাখিদের খাদ্য হয়ে, আত্মবিষসহ
যদি তার মতো কোন অবিশ্বাস্য রূপান্তর পেয়ে যাই, শুধু এই লোভে।
গ্যারেজ কবিতায় এসে পাঠক নির্বাক যন্ত্রণার চাবুক খায়।
মোটর মিস্তিরি তার মোটরের নিচে শুয়ে একদিন অদৃশ্য হয়েছে।
…………………………
মিস্তিরির বউ-বাচ্চা তিনদিন পরে এসে
ধুলোর ভিতরে ঢুকে আতিপাঁতি খুজেছিল তাকে।
পরে তারা ফিরে গেছে, চুপচাপ। গ্যারেজে তো এরকমই হয়।
দিব্যেন্দু পালিতের গল্প ‘মূকাভিনয়’, বা রমাপদ চৌধুরির ‘খারিজ’ একসাথে মনে পড়লেও, এতটা আক্রান্ত বোধ করি না। মনিভুষণ ভট্টাচার্য একদা লিখেছিলেন, ‘ জেনেও যখন জাননা তখন জানাতে হবে জ্বর করে’। কবি সেই কাজটিই করেন। কর্তব্যবোধের নির্মমতায়।
এবার ‘জিপসিদের তাঁবু’ গোটাই।
সময়, সবুজ ডাইনি
রণজিৎ-এর কবিতার একটি মুল প্রাণাংশ প্রকৃতি, নারী ও যৌনতায় প্রোথিত। এই রসায়ন নিবিড় হয়ে ধরা আছে সময়, সবুজ ডাইনির শব্দাবলীতে। যদিও তাঁর কাব্য-কৃতি জুড়ে এই অনুষঙ্গগুলি বিভিন্ন ইঙ্গিতে ঘুরেফিরে এসেছে, এই কাব্যগ্রন্থে তা যেন অনেক উজ্জ্বলতায় উচ্চারিত। বিশেষতঃ, শীর্ষ নামের কবিতায়। এখানে, সময় ডাইনি, তবে সবুজ। এটি একটি আশ্চর্য কবিতা। যেন গ্রন্থের সমস্ত কবিতার নির্যাস। সময় এক মোহময়ী নারী, যার সন্নিকট উপস্থিতি অমোঘ, অবধারিত তার আহবানও। সে যেন এক প্রাণদায়িনী ঘাতিকা। একই সঙ্গে সে উন্মুক্ত ও ব্যাপ্ততর জীবনের আহ্বান। তাকে অস্বীকার করে যারা তারা মাটির বামন, হলেও বা শক্তিমান।
‘যারা ঘরে ফেরে তারা শক্তিমান
মাটির বামন
জুতো ঘষে মুছে ফ্যালে যেকোনো দুর্বোধ্য ছবি
তারপর হাতে নেয় স্তন’
………
‘পাটাতন আঁকড়ে তারা ভেসে থাকে
আকাশগঙ্গায়
পুজোপার্বণের দিনে তাদের প্রচ্ছায়া দেখা যায়’।
এখানে আংশিক ভাবে হলেও আরনেস্ট হেমিংওয়ের দর্শন মনে পড়ে যবে। হয়তো সমরেশ বসুর গঙ্গার কথাও। কিন্তু এই যে বিচিত্র অনুভবের সঙ্গম, সেটাই রণজিৎ-কে পৃথক করে। এবং এটাও লক্ষণীয়, কী তুমুল তাচ্ছিল্যও বটে সকল খর্বতার প্রতি। কবিতাটি শেষ হয় এই উচ্চারণে-
‘আর যারা ঐ ছবি- ভাঙ্গা জাহাজের ছবি
উল্কি দিয়ে এঁকে নেয় বুকে
এবং ফেরে না ঘরে, তাদের মৃত্যুকে
লোকগাথা দিয়ে তুমি ঢেকে দাও
ভোরবেলা, শান্ত উপকূলে
নিজেও ঘুমিয়ে থাকো সেইখানে
সারাদিন, রৌদ্রে, এলোচুলে’
কবি মারের সাগর পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেছেন সবুজ ডাইনির বুকে। যে এই পৃথিবীর উপকণ্ঠে থাকে। যে এই প্রথানুগামী দুনিয়ার অংশ নয়। অংশ নয় বলেই সে মুক্ত। মুক্ত সময়ের প্রতিধ্বনি। এলোচুলে আলুথালো উদ্দাম নারী আমার। তাঁর কাজ সময়ের আল্পনা আঁকা।
‘নাবিকের হাড় দিয়ে
সন্ধ্যার উঠোনে তুমি
ভাঙ্গা জাহাজের ছবি আঁকো’
এভাবেই কবির স্বপ্নের যৌনতা আমাদের স্বতঃসিদ্ধ স্তন স্পর্শের অধিকারকে ব্যাঙ্গ করে।
এই প্রসঙ্গে ‘কবন্ধ মিথুন’ এবম্বিধ আলচনার পরিসরকে আরও পোক্ত ও প্রসারিত করবে।
‘যে স্ত্রী-পতঙ্গ তাঁর সঙ্গী পুং-পতঙ্গের
মুন্ডচ্ছেদ করে নেয়, অতর্কিতে, সঙ্গমের আগে-
…………
উদগীর্ণ মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সম্ভোগের, বীজনিক্ষেপের
চূড়ান্ত কম্পনগুলি উপভোগ করে,
ছিন্নমস্তা উল্লাসের প্রত্যক্ষ বিস্ময় সেই
পতঙ্গের তৃপ্তি, তাঁর গর্ভ, অবসাদ’
কী অলীক চামুন্ডা উচ্চারণ! সঙ্গম ও সম্ভোগকে এভাবেও দেখা যায়! বলা যায়, ‘এবং মিলিত হয় মগজের রাশমুক্ত শুদ্ধ দেহটির সঙ্গে। কবিতা শেষ হয় এইভাবে-
‘জীবনের ক্ষুদ্র সত্য ; কল্পনার অন্তিম প্রবাদ’। এই সক্রিয় তান্ত্রিকতাও তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। সমস্ত মিলনই বোধ হয় কবন্ধের উন্মুক্ত আগুনে পুরুষের আত্মসমর্পণ। হায় রে পুরুষ!
কবিতায় আণবিক ইঙ্গিত
কবিতা বলে কম। কিন্তু রেখে যায় অগনিত সম্ভাবনা। উন্মুক্ত করে দেয় কালের স্বপ্নকণ্ঠ। বুনেও দেয়। তাই কবিতা এতো আণবিক। লুক্কায়িত বহু সমুদ্র মন্থনের বীজ। এবং তা এতটাই যে রাষ্ট্রও কখনো কবিকে সহজ ভাবে মেনে নিতে পারেনি। অশীতিপর কবি তাই আজও কংসের কারাগারে। হয়তো ঠিক এই কারণেই আমার গ্রামশিকে একজন ছদ্মবেশী কবিও মনে হয়। তাঁর যোগাযোগের ভাষার আণবিকতা তো বহু স্বীকৃত আজ। এই প্রসঙ্গে আমার পড়া একটি বইয়ের কথা অবশ্য-উল্লেখ্য মনে হয়। বহু যুগ আগে সন্তোষ কুমার ঘোষের লেখা ‘ রবির কর’। একটি অতি ক্ষীণকায় রচনা। শুধু রবীন্দ্রনাথের একটি গান নিয়েঃ মনে কী দ্বিধা নিয়ে গেলে চলে…। ঐ একটি লিরিকে যে কী অপার সম্ভাবনা লুক্কায়িত, কতো সহস্র না-বলা কথা, কতো অগুন্তি গল্প, আইডিয়া ও তার সম্ভব-অসম্ভব পরিণতির কথা সন্তোষ কুমার খুঁড়ে বার করেছেন! এবং তাও সে খনন পূর্ণ হবার নয়। এ যেন সেই ঈশোপনিষদের প্রারম্ভের শান্তিপাঠের সত্য। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে । পূর্ণের পূর্ণত্ব গ্রহণ করলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন। আনন্দ প্রকাশন এই বইটি আর ছাপেনা। বাজারে প্রাপ্তব্য নয়। ভীষণই দুঃখের কথা। এমনকি ঐ সংস্থায় ব্যাক্তিগত ভাবে খোঁজ করে দেখেছি এই বইয়ের নামটিও শাঁসালো কর্তা ব্যাক্তিরদের কাছে আজ অজ্ঞাত। হায় বাদল বসুরা আজ পাকাপাকি ভাবেই মৃত ।
কবিতাতো এই পূর্ণত্বেরই সাধনা। কবি রণজিৎ দাশের কবিতায় এই উপাদান ছড়ানো। মেঘের চুলের মতো। ঈশ্বরের চোখ এর অন্তর্গত কবিতা ‘ট্রাফিক পুলিশ’ দিয়ে শুরু করা যাক। প্রয়োজন বিধায় পুরো কবিতাটাই উদ্ধৃত করছিঃ
‘শহরে যখন কেউ পাগল হয়, তখন সে ট্রাফিক পুলিশ হয়ে যায়। নিজের খেয়ালে, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে, দিনের পর দিন। নিখুঁত তাঁর হাতের মুদ্রা, অটুট তাঁর গাম্ভীর্য। কেবল তার নিয়ন্ত্রিত গাড়ি-ঘোড়াগুলি সম্পূর্ণ অলীক। যেসব গাড়ি-ঘোড়া কাউকে চাপা দেয় না, কোনো প্রিয়জনকে বাসস্টপে নামিয়ে দিয়ে যায় না …’
এই প্রসঙ্গে আরও একবার ফিরতে হবে ‘হাডুডু খেলার মাঠে’।
এবার হাডুডু-মাঠে
স্বগতোক্তি মুছে গিয়ে সংলাপের জন্ম হয়, ঝিঁঝিঁ ডাকে, জনাকি আলোয়
তৃতীয় পঙক্তির মতো একটি গরীব মেয়ে হেঁটে যায়, ছেঁড়া ফ্রক, লোকচক্ষুভীতা —
যখন সংলাপের জন্ম হয়, ঠিক তখনই তৃতীয় পঙক্তির মতো…। এই সংলাপ ধরে তৃতীয় পঙক্তির গল্প শুরু হয়! কী সেই গল্প? প্রতিটি শব্দ যেন এখানে একই সাথে একত্রিত ও পৃথক পৃথক অর্থবাহী। সংলাপ, তৃতীয় পঙক্তি, একটি গরীব মেয়ে, লোকচক্ষুভীতা। শেষ দুই পঙক্তির, ভয়ে ভয়ে তুমি দ্যাখো ,/ এই অন্ধকার গ্রামে, কুপি জ্বেলে, পাঠকই কবিতা, জন্যে প্রাগুক্ত শব্দের ব্যবহারটুকুর অপরিহার্যতা মেনে নিয়েও কবিতা আমাদের কল্পনার জন্যে বেশ বিচিত্রতর ও বৃহত্তর পরিসর রচনা করে। স্বগতোক্তির পরে যে সংলাপের সুচনা হয়, তার দায় আর কবির থাকে না। পাঠকের দায় ও দায়িত্ব দুটোই বেড়ে যায়। কবির অভিসন্ধি সার্থকতা পায়। পাঠকের কবি এভাবেই বোধ হয় তাঁর পাঠ ও পাঠক দুইই নির্মাণ করেন।
আমাকে যদি মাত্র একটি কবিতা দিয়ে কবিকে চিহ্নিত করতে বলা হয়, অবধারিত ভাবে ‘ঘণ্টাধ্বনি’ কে বেছে নেব। রণজিৎ সে অর্থে কোনো আখ্যান কাব্য রচনা করেন নি। কিন্তু তাঁর কবিতা জুড়ে যে কাব্য দর্শন ছড়ানো তা এতটাই স্তরবাহী (layered) যে ঘণ্টাধ্বনির মতো আট পঙক্তির ছোট্ট কবিতা সঠিক অর্থেই একটি পারমাণবিক বিষ্ফোরণ ঘটায়। প্রতিটি ছত্র গুরুভার ধাতব সম্ভাবনা বহন করে।
…… দুলে- ওঠা ধাতব পাল্লায়
ডুবন্ত নৌকোর ছায়া; ঊর্ধ্বে, ঝড়ে অস্থির কাঁটায়
তোমার আমূলবিদ্ধ চোখ, চির-অবিশ্বাসী; দস্যুর মাস্তুলে
গাঁথা নৃমুণ্ডের মতো তিক্ত, গুরুভার।
প্রতিটি শব্দই এখানে ‘প্রশ্নাতীত বাটখারা’ কে বহুমাত্রিক সংশয়ের দ্যোতনায় আবদ্ধ ক’রে আমাদের বিপন্ন সত্তাকে প্রহার করে ও ব্যবহৃত উপমা-শৃঙ্খলে পাঠকের জানালা খুলে দ্যায়। কারণ,
‘এই ঠোঙ্গা -ভর্তি নুন ঘিরে ক্রোধে দুলে- ওঠা সমুদ্র- পাল্লার
যেটুকু কপালফের, সেটুকুই মৌল প্রতারণা’-
কোন টুকু? কতো টুকু? কোন কপালফেরের মৌলতা? বিপুল রহস্য রেখে যায় কবিতাটি। একটি নির্মম ও নিষ্ঠূর দায় অর্জন করে পাঠক। কবিতা শেষ হয়-
‘মুদি ও তোমার মধ্যে সম্পর্কের নিহিত বেদনা।‘
ঘণ্টাধ্বনিকে একটি কবিতার এক মহত্তম সৃষ্টি হিসেবে বিস্মিত উপভোগ করেও পরবর্তী প্রস্তাবে পাঠক এই রহস্য দর্পণের মুখোমুখি না হয়ে পারে না। ঘণ্টাধ্বনি ভিতরে বেজে যেতেই থাকে। অবিরাম। এবং জীবনের নানা মোড়ে নানা মোড়কে তা অন্যতর রূপে ফিরে ফিরে আসতেই থাকে। অন্তত আমার অভিজ্ঞতায় তাই হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য, stories/ ideas in absentia’ এক পাঠকের রসাস্বদনের বিশিষ্ট হাতিয়ার। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। এ পর্যায় শেষ করি অসমাপ্ত আলিঙ্গন থেকে আরও একটি পারমাণবিক কবিতা উঠিয়ে এনে, ‘খরা’-
‘গ্রামের শুকনো মাটির বুকে
স্তন্যহীন খরা
শহর জুড়ে লিসিয়া ব্রা
দুষ্টুমিতে ভরা’
এর প্রত্যেকটিই সার্থক কবিতা যা পাঠককেও কবিতার জমি দেয়। ‘একাকী গায়কের নহে তো গান’। কবির এই শিক্ষকতার প্রচ্ছন্ন ভুমিকার কথা তো শুরুতেই বলেছি। কবির তীব্র ব্যঙ্গ ও হাহাকারও একই বিভঙ্গে প্রকটিত হয়। ‘শরীরের ঘামগন্ধে আমাকে জড়াও/ সারা রাত্রি, আজীবন, প্রতীকের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও’।
আঁধার রাতে একলা পাগলঃ অশ্রুর প্রতিবাদ
মহাকবি রিল্কের দুঃখ ছিল এতো চেষ্টায়ও একটি পূর্ণ কবিতা লেখা হল না তাঁর। এ দুঃখ তো সব কবিরই। তাই তো সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। অশ্রুর দেবতা পড়তে পড়তে এই কথাগুলো বারবার মনে আসে। কবির একলা পাগল রহস্য-মহাসাগরের কুলে বসে কাঁদে। বুঝিয়ে দে। যেন এক অনন্ত বালকের বিস্মিত জিজ্ঞাসা। এই পৃথিবীর এতোটা পথ হেঁটে এসে কবির সংশয়াত্মাই তাঁর কাব্য বিজ্ঞান হয়ে ওঠে আমার কাছে। আর আমরা পেয়ে যাই অরূপ- স্বরূপ- সগুণ- নির্গুণের সঙ্গে লিপিবদ্ধ নিরন্তর সংলাপ। এই কাব্যগ্রন্থটিকে আমি নানা অভিধায় ভাবতে পারি, যার একটি হল প্রতিবাদের ভাষার অন্যতর মেরুদণ্ড নির্মাণ। রণজিৎ যে একজন চূড়ান্ত প্রতিবাদী কবিও এ কথাটি খানিকটা অবহেলিত সত্য। এই অনন্যতার জন্যই বোধ হয় গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন কবি। চিরকালীন প্রতিবাদী আমাদের কাছে আর কেই বা আছেন! আজকের এই অদ্ভুত আঁধারে রবীন্দ্রনাথের কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় কোথায়? কবিদের মধ্যে পাগলের চরিত্র গঠনে রবীন্দ্রনাথ এখনো পথিকৃৎ। কারণ পাগল ও তার পাগলামিই তো এই অসাম্য বিস্তৃত সমাজে সবচেয়ে বড় প্রতিবাদী সত্তা। এ প্রসঙ্গে ‘ধানখেতে বৃষ্টির কবিতা’ এবং ‘অসমাপ্ত আলিঙ্গন’ এর স্পষ্ট সুচনাধ্বনি পাই। এর মানে এই নয় যে অন্যত্র পাই না। কিন্তু উল্লেখিত কাব্যগ্রন্থ দুটির রচনাকাল নক্ষ্যণীয়ঃ ২০১০-২০১৫। আঁধারের মধ্য গগনের বিকাশকাল। কবিতা দুটিও উদ্ধৃত করিঃ
লবণ
ঈশ্বর, অদৃশ্য তুমি,
অশ্রুমধ্যে লবণের মতো
তোমাকে আস্বাদ করি
গভীর ক্রন্দনে, অবিরত…
গান
প্রতিটি মানুষ তার
নিজস্ব গানের মধ্যে বেঁচে থাকে- মাথা-নাড়া পাগলের মতো
সে-গান শুনতে চাও?
শুধু তার বুকে কান পাতো !
এ কুহক সময়ে বড় প্রয়োজন ঈশ্বর ও পাগলের বুকে কান পাতার। একটু হয়তো খাপছাড়া লাগতেও পারে। ইদানিং, ভারতে এসে মার্কিন পলিটিকাল থিঙ্কার মাইকেল স্যান্ডেল-এর অনুধাবন ভাবনাযোগ্য। পলিটিক্স অফ হোপ-এ উনি জনগণের স্পিরিচুয়াল হোপ কেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এখানে আধ্যাত্মিকতা শব্দটি ইচ্ছে করেই পরিহার করলাম। রবীন্দ্র দর্শনের অন্তর্নিহিত বাণীর প্রতিধ্বনি শুনি। প্রতিবাদের কণ্ঠ নাদহীন উচ্চারণে যে প্রাণ হারায় অনেক আন্তরিক স্লোগানের অপমৃত্যুতে তা প্রমাণিত। তাই রবীন্দ্রনাথে ফিরে আসতে হয়। কবিও।
কবি ও বাস্তবতার যৌন মিলনে কবিতার সৃষ্টি। নিউজপেপার ধরে রাথে তাকে।
সকালের রৌদ্র হল
ঈশ্বরের নিউজপেপার
ভরের জানালা দিয়ে
এই আলকবার্তা কেউ ছুঁড়ে দিয়ে যায়-…
এবার কাগজ আসে পৃথিবীর –
সারা মেঝে ধর্ষণ আর খুনের
লাল রক্তে ভাসে
নিঃসঙ্গতার শপিং মল এর তিন নম্বর কবিতায়-
আমার দক্ষতা শুধু একটিই,
জলভরা চোখে আমি
পৃথিবীকে স্পষ্ট দেখতে পারি-
নদী ও শ্মশান, বৃক্ষ, লোকালয়, পাগলিনী নারী
পাঁচ-এর কবিতায়
চারদিকের চোখগুলো সমস্তই শপিং মলের চোখ,
নীরবে তোমাকে দেখছে- কাল্পনিক শোকেসে, উত্তেজক অন্তর্বাসে,
বিশাল মহার্ঘ বিপণিতে-
আত্মগোপন করো হিমালয়ে, তীব্র শীতে, ভুটিয়া বস্তিতে
শেষ কবিতায় মন্ত্রোচ্চারিত হয়-
আমার ‘জাগ্রত চিত্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্মল
কঠিন সন্তোষ’ আমি কখনও করেছি অনুভব?
কখনও বুঝেছি এই কবিত্বের বীজমন্ত্র-
হৃদয়ে তুফানশঙ্খরব?
এরই জন্য দিবারাত্রি প্রকৃতির স্তব
এরই জন্য দিবারাত্রি মানুষের স্তব
এরই জন্য দিবারাত্রি হৃদয়কে ঘিরে
মুনিসম নিঃসঙ্গতা সৃষ্টির উৎসব।
হৃদয় মানে কী? যার কাছে/ সব হিংসা ব্যর্থ, অবনত।
এ পৃথিবী শঠতা, রিরংসা, মৃত্যু নিয়ে কবে সমস্ত অন্ধকারকে ছুঁড়ে ফেলে বলতে পারবে, চলব আমি নিজের আলো ধরে? ‘আপ্পো দীপ ভব’ সঙ্কটে সন্ত্রাসে এই মন্ত্র কবিরও অন্তরস্থ প্রতিবাদী উচ্চারণ।
রণজিৎ এর প্রবন্ধ গ্রন্থ ‘ডিজিটালের শয়তান ও কবিতা’-র বীজ মন্ত্র পাই সেক্স-রোবট কবিতাটির শেষ চরণ কটিতে।
…… স্মার্টফোন কিনেছি, হোয়াটসঅ্যাপ শিখেছি। কিন্তু গোপনে সেই শয়তানের বিরুদ্ধে কিছু হ্যান্ডবিল লিখে চলেছি। যেমন, এই হ্যান্ডবিলটি হল সেক্স-রোবটদের বিনাশের জন্য আমাদের চিরন্তন শ্রীরাধিকার হ্যান্ডবিল। ‘প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর’। ভালবাসাই তো সর্বশক্তিমান।
পাপীর সাজায় কবি আর ঈশ্বরের সংলাপে গভীর সংশয় সরল ভাষা পায়-
একটা কথা বলো সাধু
একটা কথা বলো-
ঈশ্বরের জীবদ্দশায়
পাপীর সাজা হলো?
রবীন্দ্রনাথে জারিত হয়েও কবির অশ্রুর দেবতা ঈশ্বরত্ব পান না। এও তো আর এক প্রতিবাদ। আমি ও সমুদ্রঝড় এর বিপরীতে কবির আত্মার প্রয়োজনীয় আত্মস্থতার কথা বলে। যে প্রতিবাদ স্বর পেয়েছে বিভিন্ন কবিতায় আজীবন তা পুঞ্জীভূত আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের দীর্ঘশ্বাস হয়ে পরাজিত করে ‘ঘূর্ণ্যমান, মদমত্ত ঝড়’ কে।
সেই ঝড় ছুটে এল সবেগে আমার দিকে,
স্ফীতপেশী কালো মেঘে মুষ্টি পাকিয়ে,
ভয়ংকর আগ্রাসী বাতাসে-
এবং লুটিয়ে পড়লো আমার পায়ের কাছে,
নক-আউট হয়ে গেল…
আমরা পাঠকেরাও।

One Comment
দীর্ঘ সময় নিয়ে আপনার দীর্ঘ প্রবন্ধটি পড়লাম। অসাধারণ পাঠ ও বিশ্লেষণ। মুগ্ধ হলাম।