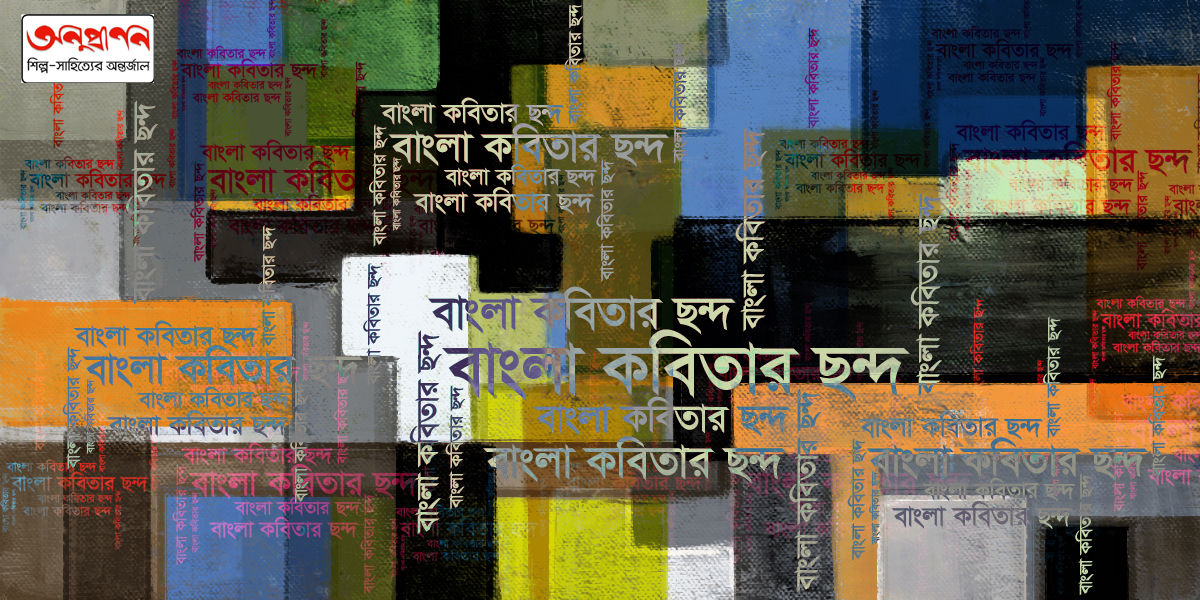
সাহিত্য সৃষ্টির মূলে আছে নান্দনিকতা। এই নান্দনিক অনুভূতিই পাঠকের কাছে সাহিত্যকে আকর্ষণীয় করে তোলে। কবিতায় শব্দসজ্জা, সুষম বিন্যাস এবং সৃজনশীলতার প্রকৌশলই একমাত্র এই নান্দনিকতা নিয়ে আসতে পারে। নিরস শব্দ হয়ে ওঠে রসবতী। শব্দবিন্যাসের এই নান্দনিকতা থাকে না বলেই পাঁজি, রান্নার বই ইত্যাদির ভাষাকে সাহিত্য বলা যায় না। এখন একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। বর্তমান কালের এক কবির (রুমকী দত্ত) কবিতার দুটি লাই হলো—
একলা দুপুর পায়ের নূপুর পুকুর ভরা জল।
সৃষ্টি সুখে মিষ্টি মুখে বৃষ্টি ভিজি চল।
উনি যখন এই কবিতা লিখব ভাবলেন তখন প্রথমেই ধ্বনিতত্ত্বের রীতিনীতি আর বিন্যাস হিসাব করে লিখতে বসেননি। যেটাকে প্রাথমিকতা দিয়েছিলেন তা হলো শব্দগুলো যাতে কবিতার লাইন বরাবর এমন একটি ধ্বনিপ্রবাহের সৃষ্টি করে যা পাঠক মনকে দোলায়িত করে তুলবে। আর এটা করতে গিয়ে তিনি বর্ণ তথা শব্দগুলোকে মনের মতো করে এক অভিনব কৌশলে সাজিয়ে তুললেন। শব্দগুলো আপনি ছন্দবদ্ধ হয়ে উঠল। কিন্তু যে কোনো ভাষাই এভাবে ছন্দবদ্ধ হয় না, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘অনুভবের ভাষাই ছন্দবদ্ধ’। এর পেছনে থাকে কবির বিশেষ অনুভব। এই বাঁধনের জন্যই আকাঙ্ক্ষিত ‘দোলা’ বা ‘ধ্বনিপ্রবাহ’কে পাওয়া গেল। এভাবেই সৃষ্টি হলো ছন্দের। অর্থাৎ কিনা বলা যায় ছন্দ তৈরি হলো পাঠকের তাগিদেই, উচ্চারণ বা কবিতা আবৃত্তির কথা মাথায় রেখে। যেমন—
ফুল কলি রে ফুল কলি
বলতো এটা কোন গলি।
এখানে পাঠক মনকে দ্রুত লয়ে একটা দোলা দিয়ে ভাসিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এটাই হলো ছন্দের যাদু। ছন্দ শুধু কবিতাতেই সৌন্দর্য সৃষ্টি করে না, নদীর কুলু কুলু ধ্বনিতে যে আমরা রোমাঞ্চিত হই, বাতাসের মর্মরে শিহরিত হই, সঙ্গীতের সুরমূর্ছনায় আন্দোলিত হই সব এই ছন্দের জন্যই। এমনকি মানুষের জীবনও এই ছন্দেই চলে, তাই দীর্ঘ রোগভোগের পর বলা হয় মানুষটি ছন্দে ফিরে এসেছে। ছান্দসিক জীবেন্দ্র সিংহ রায় ছন্দের সংজ্ঞা দিয়েছেন— কাব্যের রসঘন ও শ্রুতিমধুর বাক্যে সুশৃঙ্খল ধ্বনিবিন্যাসের ফলে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় তাকে ছন্দ বলে।
কিন্তু ছন্দ তো এমনি এমনি সৃষ্টি হয় না। তার কিছু উপকরণ আছে। একজন মহিলা এমনি এমনি ‘সুন্দরী’ হন না, নির্ভর করে শারীরিক গঠন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গড়ন, ত্বক, রঙ ইত্যাদির উপর। ছন্দেরও তেমনি কিছু উপকরণ আছে। ধ্বনি, অক্ষর, মাত্রা, মিল, পর্ব এগুলো হচ্ছে ছন্দের উপকরণ।
রুমকী দত্ত যদি কবিতার লাইন উপরোক্তভাবে না লিখে এমনিভাবে লিখতেন—
শুনশান দুপুরে পায়ে নূপুর পরে মিষ্টি খেতে খেতে ভরা পুকুরের ধারে প্রকৃতির সৃষ্টি উপভোগ করতে করতে চল গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজি
তাহলে সেটা পাঠক মনে তেমন কোনো দোলা দিতে পারত না আর লাইনটির প্রয়োজনীয়তাও পাঠকের কাছে পড়ার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু লাইনগুলো সজ্জিত হয়ে যখন মন দোলনকারী কবিতার রূপ নিল তখন সেটি সহজেই আমাদের মনে দোল খেতে থাকল। এখানেই ছন্দের প্রয়োজনীয়তা। তাহলে দেখা যাক কবি রুমকী দত্ত লাইনের মধ্যে কী এমন করলেন যে এরকম হলো। কবিতাটিকে যদি এভাবে সাজানো হয়—
একলা দুপুর। পায়ের নূপুর। পুকুর ভরা। জল
সৃষ্টি সুখে। মিষ্টি মুখে। বৃষ্টি ভিজি। চল
উপরের লাইনটিকে এখানে ভাগ ভাগ করে দেখানো হয়েছে। শব্দসজ্জা এমন হয়েছে যাতে শব্দগুলোকে একনিঃশ্বাসে দ্রুত না পড়ে বাকযন্ত্র আপনাআপনি কিছু বিশেষ জায়গায় গিয়ে থেমে যায় এবং লাইনটি বোধগম্য হয় ও শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ উচ্চারণে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর বাকযন্ত্রকে একটু বিরতি বা বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। দাঁড়ি চিহ্ন দিয়ে এই বিরতিকে বোঝানো হয়েছে। একে বলে যতি। দুই যতির মাঝখানের অংশকে বলে পর্ব। উপরের কবিতাটিতে প্রতিটি লাইনে তিনটি পর্ব আছে আর একটি উপপর্ব আছে (জল, চল)। পর্বের ভেতরের শব্দগুলোকে বলে পদ (একলা, দুপুর)। তিনটি পর্ব নিয়ে যে লাইনটি তাকে বলে চরণ। অর্থ স্পষ্ট করার জন্য অনেক সময় একটি পর্বের মাঝেও খানিক বিরতির প্রয়োজন হয়। কমা, সেমিকোলন দিয়ে তাকে বোঝানো হয়। একে বলে ছেদ। এরকম ছেদ ও যতির সাহায্যে মাইকেল মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি করেছিলেন—
ধন্য ইন্দ্রজিৎ, ধন্য। প্রমীলা সুন্দরী।
ভিখারি রাঘব, দূতি। বিদিত জগতে।
তাহলে কবিতার ভেতরে কিছুটা ঢোকা গেল। কিন্তু ছন্দ উদ্ঘাটনের জন্য এবার পর্বের ভেতরে ঢুকতে হবে। যেমন ‘একলা দুপুর’ পর্বটিকে যদি এভাবে সাজানো হয়—
।এক্ লা দু পুর্। বা পরবর্তী পর্বটিকে এভাবে—
।পা এর্ নু পুর্।
তাহলে এক একটি পর্ব আরও চার ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এই চার ভাগের একেকটি অংশকে ( এক্, লা) বলা হয় ‘মাত্রা’, যা হলো ছন্দের এক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। এভাবে ভাঙলে দেখা যাবে প্রতিটি পর্বেই চারটি করে মাত্রা রয়েছে
।পু কুর্ ভ রা। সৃস্ টি সু খে। মিস্ টি মু খে। বৃস টি ভে জা।
সুতরাং কবিতার মধ্যে একটা বাঁধন আছে বোঝা গেল। পর্বের মধ্যে এরকম বাঁধন উচ্চারণের পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছে। ‘একলা’ এই শব্দটিকে আমরা উচ্চারণের সময় পুরোটা একঝোঁকে বলি না, একঝোঁকে ‘এক্’ বলি তারপর বলি ‘লা’। এই শব্দাংশগুলো আসলে একেকটি অক্ষর। স্বল্প বা ন্যূনতম প্রয়াসে শব্দের যেটুকু অংশ একঝোঁকে পড়া সম্ভব তাকেই বলে ‘অক্ষর’। ‘কম্পন’ একটি শব্দ। এর হরফ তিনটি ক,ম্প ও ন, কিন্তু এর অক্ষর সংখ্যা দুটি কম্ ও পন্। শব্দে যতগুলো বর্ণ থাকে ততগুলো অক্ষর নাও থাকতে পারে। অক্ষরের আরও প্রকারভেদ আছে সহজ আলোচনার জন্য সেদিকে আমরা গেলাম না।
বর্তমান কবিতাটিতে দেখা যাচ্ছে প্রতিটি পর্বে যতগুলো অক্ষর আছে ততগুলোই মাত্রা আছে। প্রতিটি মূল পর্বে এখানে ৪টি করে এক একটি চরণে মোট ১২টি মাত্রা আছে। বলা হয় একটি অক্ষর উচ্চারণ করতে এক মাত্রা সময় লাগে। সুতরাং মাত্রা আসলে সময়ের পরিমাপক। মাত্রা হলো ছন্দের একক। এটি উচ্চারণ কালের ক্ষুদ্রতম অংশ। এই মাত্রাই ঠিক করে ছন্দটি কী প্রকার হবে। আমরা জানি ছন্দ মূলত তিন প্রকার— স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত আর অক্ষরবৃত্ত। স্বরবৃত্ত ছন্দে মূল পর্বে সব সময় ৪টি করে মাত্রা থাকে। যেমন—
বাঁশ বাগানের। মাথার উপর। চাঁদ উঠেছে। ওই
মাগো আমার। শোলোক বলা। কাজলা দিদি। কই
বর্তমান আলোচ্য কবিতাটি তাই একটি স্বরবৃত্ত ছন্দের উদাহরণ। মূলপর্বে মাত্রা সংখ্যা ৪, ৫, ৬ বা ৭ হলে তা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ হয়ে যাবে। আবার ৮ বা ১০ মাত্রার হলে তা হবে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। সুতরাং মাত্রা দেখে ছন্দ নির্ণয় করা সম্ভব।
এবার একটু অক্ষরের ভেতরে ঢোকা যাক। আমাদের আলোচ্য রুমকী দত্তের কবিতাটিতে প্রতিটি চরণের শেষ অপূর্ণ পর্বে একটি করে একমাত্রার অক্ষর আছে। জল ও চল। দুটি বর্ণ থাকলেও এখানে অক্ষর ১ মাত্রাও ১। কারণ উচ্চারণ। আমরা যখন বলি ‘বল কী খাবে?’ তখন ‘বল’কে যেভাবে উচ্চারণ করি ,’বল কী খাবি?’ বলার সময় একইরকম উচ্চারণ করি না। এখান বল্ এভাবে উচ্চারিত হয়। তাই চল্ ও জল্ একমাত্রার। এখানে উচ্চারণ জোর করে একটু থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন অপ, রাম, স্ক্রুপ শেষে অ বলি না অর্থাৎ স্বরান্ত নয়। অ, আ, ই এরা একটি বর্ণ হলেও অক্ষর। কিন্তু ক্, খ্ প্রভৃতি হোল ব্যঞ্জনখণ্ড এগুলো অক্ষর নয়, এগুলোকে বলা হয় ধ্বনি। এরা কোনো না কোনো স্বরবর্ণের সাহায্যে উচ্চারিত হয়। আলোচ্য কবিতাটিতে ‘সৃষ্টি’ একটি শব্দ আছে। এটার ধ্বনি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়— স্+র্+ই+স্+ট্+ই কিন্তু অক্ষর দুটিই। মাত্রাও দুটি-সৃস, টি।
এখন আলোচ্য কবিতাটি যদি এভাবে লেখা হতো—
তপ্ত দুপুর। পায়েতে নূপুর। ভরা পুকুরের। জল (প্রথম লাইন)
তাহলে প্রতিটি পর্বে মাত্রা সংখ্যা বেড়ে যেত। এখানে যেমন ৪-এর জায়গায় ৬ হয়েছে। সুতরাং এটি একটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দ হয়ে গেছে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে যুক্তাক্ষর বা বদ্ধাক্ষর সবসময় ২ মাত্রার হয়। ত(১) প্ত(২) দু(১)পুর্(বদ্ধাক্ষর)(২) মোট ৬ মাত্রা। এভাবে। পা এ তে নূ পুর। সব মূল পর্বেই মাত্রা সংখ্যা ৬ পাওয়া যাবে। এই ছন্দে মাত্রা নির্ণয়ের একটি সহজ ফর্মুলা শ্রদ্ধেয় বিনয় মজুমদার বের করেছেন। তাঁর মতে বাংলা অক্ষরের উপর যে মাত্রা দেওয়া থাকে তাই ছন্দের মাত্রা। যেমন ‘হঠাৎ’ একটি শব্দ। এখানে হ ও ঠ এর উপর মাত্রা আছে কিন্তু ৎ এর উপর নেই, সুতরাং এটি দুই মাত্রার। তবে ব্যতিক্রম আছে। পদের শুরুতেই ও প্রভৃতি অক্ষর থাকলে তার উপরে মাত্রা না থাকলেও তাকে এক মাত্রা ধরতে হবে। যেমন—। ওলো প্রিয় সখি। রাত আছে বাকি। ৬মাত্রা।
এবার কবিতাটিকে আরেকটু ঘুরিয়ে দেওয়া যাক।
।তাপিত দুপুর বেলা। পায়েতে নূপুর খেলা। ভরা পুকুরের মাঝে। জল (প্রথম লাইন)
এখানে মূল পর্বে মাত্রা সংখ্যা ৮। সুতরাং এটি হয়ে গেল অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। অবশ্য এই ছন্দে কিছু বাড়তি নিয়ম আছে। মুক্তাক্ষর বদ্ধাক্ষর নিয়ে। অ হচ্ছে মুক্তাক্ষর কারণ এর উচ্চারণ মুক্ত কিন্তু বান্ বা তর্ হচ্ছে বদ্ধাক্ষর কারণ এদের উচ্চরণের শেষে বাধা আছে। অক্ষরবৃত্তে শব্দের প্রথমে বা মাঝে বদ্ধাক্ষর থাকলে এক মাত্রা কিন্তু শেষে থাকলে দুই মাত্রা।এই হিসেবে ‘অবান্তর’ (অ বান্ তর) ১+১+২ মোট ৪ মাত্রার।আলোচ্য কবিতাটিতে ‘দু-পুর্’ বা ‘পু-কুর্’ ১+২ =৩ মাত্রা। (তা পি ত দু পুর বে লা মোট ৮ অক্ষর)। অক্ষরবৃত্তে যতগুলো অক্ষর ততগুলোই মাত্রা। যেমন—
নিশীথিনী ভোর হয়ে আসে
আলো ফোটে পুবের আকাশে
(১০ মাত্রা)
যুক্তাক্ষর যোগ করে যদি এটাকে করা যায়—
অমারাত্রি ভোর হয়ে আসে
আলো ফোটে পূর্বের আকাশে
তবুও এটা ১০ মাত্রারই থাকে।
এখন ‘অ বান্ তর’ শব্দটির তিনটি ছন্দে মাত্রা নির্ণয় করা যাক। স্বরবৃত্তে এর মাত্রা সংখ্যা ১+১+১=৩, মাত্রাবৃত্তে ১+২+২=৫ এবং অক্ষরবৃত্তে ১+১+২= ৪।
এই তিনটি ছন্দ ছাড়াও বাংলায় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ‘অমিত্রাক্ষর’ ছন্দের প্রচলন করেন। এতে চরণের শেষে অন্তমিল থাকে না, চরণের মাঝেও বাক্য শেষ হতে পারে। ভাব এক চরণ থেকে আরেক চরণে প্রবাহিত হয়। অন্তমিল না থাকলেও এই ছন্দে প্রতি চরণে মাত্রা সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে সাধারণত ১৪ এবং পর্বেও মাত্রা সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে সাধারণত ৮+৬।
সনেট আরেকটি ছন্দ, এটিও বাংলায় প্রথম ব্যবহার করেন কবি মাইকেল মধুসূদন। পরে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি কবিরাও ব্যবহার করেন। এতে ১৪ বা ১৮ মাত্রার চরণ হয়। দুই স্তবকে ১৪টি চরণ থাকে (৮+৬)। প্রথম স্তবকে ভাবের প্রকাশ থাকে আর দ্বিতীয় স্তবকে তার পরিণতি অথবা বলা যায় প্রথম স্তবকে কোনো সমস্যার কথা থাকলে দ্বিতীয় স্তবকে তার সমাধান থাকে।
এছাড়াও আজকাল গদ্যছন্দের ব্যবহার হচ্ছে। যা প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ই ব্যবহার করেন। এখানে অন্তমিল তো থাকেই না, পর্বগুলোও নানা মাত্রার হয়। ছেদ বা বিরাম সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়। এতদসত্ত্বেও যখন গদ্যছন্দে কবিতা লেখা হয় তখন শেষ পর্যন্ত তাতে ছন্দের তৈরি হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘গদ্যের মধ্যে যখন পদ্যের রঙ ধরানো হয় তখন গদ্যকবিতার জন্ম হয়’।
এই প্রসঙ্গে বলা উচিত, এটি একটি ছন্দের সীমিত আলোচনা, তাই গভীর আলোকপাত নেই, ছান্দসিকদের পিপাসা মেটানোর মতো নয়, তাই ত্রুটি থাকতে পারে, থাকলে মার্জনীয় ও পরামর্শ প্রার্থনীয়। পরিশেষে আরেকটি কথা—অনেকেই ছন্দকে কবিতা লেখার ক্ষেত্রে একটা সীমাবদ্ধতা বলেছেন, স্বাধীন কৌশল ব্যবহারের বাধা। তার ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ সুন্দর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন সেতারের তার বাঁধা থাকে বলেই সুরের মূর্ছনা মুক্তি পায়। ছন্দে বাঁধা থাকে বলেই তেমনি কবিতার সৌন্দর্য ফুটে ওঠে।
ঋণস্বীকার
কবিতার ক্লাস/ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
বাংলা ছন্দ/ সুধীভূষণ ভট্টাচার্য
আসানসোল, ভারত থেকে
