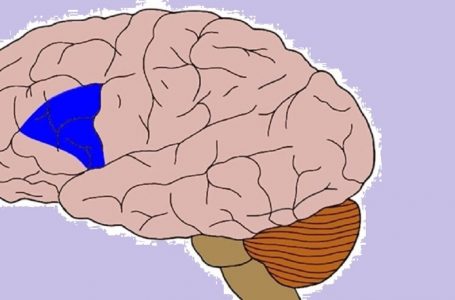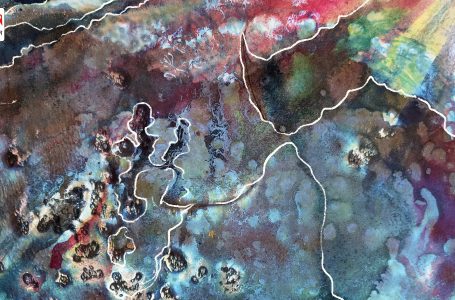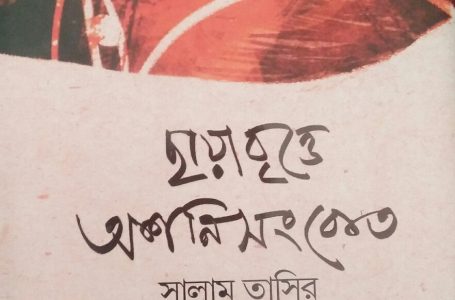বাংলা ছোটগল্পের আকাশে অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০০) এক নক্ষত্র। শুধু গল্প লেখার জন্য গল্প লেখেননি তিনি, গল্পে এনেছেন চমৎকারিত্ব— ভাষায় বা কাঠামোতে অভিনব স্টাইল লক্ষণীয়। গল্পের গঠনে-উপসংহারে বিশেষভাবে দৃষ্টি তার প্রখর। ভাষাসম্পদ সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ, কাব্যের সুর গল্পের সুরের বাঁধনে মিলেমিশে একাকার হয়ে অন্য একটা সূর্যালোকের সৃষ্টি করেছে। জীবনের জয়গান যেমন করেছেন, আনন্দ-উচ্ছ্বাসে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন। আবার জীবনের পরাজয়-দুঃখকে সাজিয়ে তুলেছেন, গ্রাম বা গ্রামীণ অথবা নাগরিক জীবনের কাহিনী স্বচ্ছন্দে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনের বাস্তবতাকে ছুঁয়ে যায়। তার গল্পে সময়ের চাহিদার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদি যেমন সাবলীলভাবে এসেছে, তেমনি সাতচল্লিশ পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন অনুষঙ্গ প্রখরভাবে চিহ্নিত হয়েছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই যে চড়াই-উৎরাই, এই যে নিরন্তর তার ভেসে চলা, তার পারিপার্শ্বিক ভিন্নমাত্রিক বিস্তৃতি তার গল্পে চিত্রায়িত হয়েছে বিশ্বস্ত এবং অন্তরঙ্গ পরিচয়ে। তার গল্পে জীবনের খ্ণ্ড-খণ্ড অংশগুলো চিরন্তনভাবে প্রতিভাত হয়। জীবনের প্রতি মুহূর্তকে যেমন এনেছেন তেমনি প্রতি ক্ষুদ্র অংশকে অমিয়ভূষণ বিষয়ের ছাঁদে চিত্রঙ্কণ করেন, হয়তো কখনো তা বিন্দুকে সিন্ধুতে রূপান্তরিত করেছেন অথবা সিন্ধুকে অবলীলায় বিন্দুতে রূপায়ণ করে গল্পের চমৎকারিত্বের বিমূর্ত ছবি এঁকেছেন, তাতে গভীরতার সিন্ধু আরও খানিক বৃদ্ধি পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের যে তত্ত্ব, ছোট কথা, ছোট ব্যথা… নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ… শেষ হয়েও হইলো না শেষ— সেখান থেকে সরে এসে নরেন্দ্রনাথ মিত্র বলছেন, ‘ছোটগল্প মানে কিন্তু সেই অর্থে ছোট নয়, সুবুদ্ধির বিকাশ, ছোটগল্পে হাজার পাখি এবং হাজার-হাজার ফুল, একেক ফুলের যেমন একেক রকম গন্ধ. তেমনি একেক পাখির একেক রকমের ডাক, সব মিলিয়ে বন এবং আমাদের জীবন’। মোটকথা জীবনের একটা অংশকে ছোটগল্পের ক্যানভাসে পরিপূর্ণতার সঙ্গে তুলে ধরাই ছোটগল্প রচয়িতার মোক্ষম কাজ, যে কাজটা অমিয়ভূষণ সার্থকভাবেই পেরেছেন, নিজস্ব শৈলী বা স্টাইল তার গল্পের ভুবন সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাসাহিত্যের আকাশটাকে করেছে সমৃদ্ধ এবং সাবলীল।
বিংশ শতকের ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ দশক বাংলা সাহিত্যের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটা যুগ, কবিতা-গল্প-উপন্যাসের যে জন্মবেদনা এবং কবি-সাহিত্যিকদের উঠে আসার সময়, নতুন চেতনায়-নতুন ভাবনায়-নতুন আঙ্গিকে তাদের প্রাণের কথা ব্যক্ত করে, তাদের চিন্তার রেশটাকে ছড়িয়ে দেয় সমগ্র মানবজগতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯, যার শেষ হয় ১৯৪৫ আনুষ্ঠানিকভাবে, ১৯৪৩-এর প্রথম দিকে প্রাকৃতিক ঝড় দুর্যোগ এবং মন্বন্তর, ১৯৪৬-এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বাস্তুহারাদের সহায়-সম্বল হারানোর তীব্র বুকভাঙা যন্ত্রণা, ১৯৪৭-এ দেশভাগ, দুটো স্বাধীন দেশের মানচিত্র অর্থাৎ ধর্ম এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তি করে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা প্রপ্তির পর বিভাজিত দেশের উদ্বাস্তু সমস্যা, সেই গভীর সমস্যা থেকে অবক্ষয়-অনন্বয়-অস্তিত্বের সংকট, উদ্ভব ঘটে নতুন ধনিক শ্রেণির, প্রান্তিক মানুষকে চুষে খাওয়ার সেই রক্তচোষার দলেরা ঐক্যবদ্ধ হয়, মুখোশ খুলে সামনে এসে দাঁড়ায় পুঁজিবাদী-কালোবাজারি-মুনাফাখোর-মজুতদার-দাদনব্যবসায়ী, ১৯৫০ অবধি এদের দৌরাত্ম্যের কাছে হার মানে রাষ্ট্র, ক্রমে-ক্রমে তা আবার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়, এ-সময় মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে ওঠে, ভাত-কাপড়-বাসস্থানের অভাবের সাথে আরও কিছু প্রয়োজনীয় অভাব দেখা দেয়, বাঁচার মতো বাঁচার জন্য বিনোদন-সংস্কৃতি চায়, এসময়ে মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ থেকে গজিয়ে ওঠে একঝাঁক সাহিত্যিক, মূলত যারা সাহিত্য-সংস্কৃতির নেতৃত্বে আসীন হন, এদের পদচারণে এসময় বাংলাসাহিত্যের ভূমি উর্বর হয়, নতুন অভিনব জীবনের কথাকারেরা বেরিয়ে আসে তিক্ত-অভিজ্ঞতায় বলিষ্ঠ হয়ে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) লালসালু (১৯৪৮), আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) সূর্যদীঘল বাড়ী (১৯৫৫), হুমায়ুন কবীর (১৯০৬-১৯৬৯) নদী ও নারী (১৯৫২), অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৯০৭-১৯৬২) চরকাশেম (১৯৪৯), অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০০) গড় শ্রীখণ্ড (১৯৫৭), সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫) কিনু গোয়ালার গলি (১৯৪৯-৫০ সালে ‘দেশ’ প্রকাশ করে ধারাবাহিকভাবে), কাজী আবদুল ওদুদ (১৯৯৬-১৯৭০) নদীবক্ষ (১৯১৯), আবদুল জব্বার (১৯৩৩-২০১১) ইলিশমারীর চর (১৩৬৮ বাংলা), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮২) বারো ঘর এক উঠোন (১৯৫৫), অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫২) তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৫৬), শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৫-১৯৭১) সারেং বৌ (১৯৬১) প্রভৃতি উপন্যাসে ব্যক্তিক ও পারিবারিক অস্তিত্বের সংকট নিয়ে যে কাহিনী গড়ে উঠেছে তা এককথায় মর্মস্পর্শী।
পাঠক নিশ্চয় অবগত আছেন, ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ এর মধ্যে বাংলাসাহিত্যে বিশেষ করে ছোটগল্পে বাস্তববোধ-প্রগতি চেতনা-সমাজমনস্কতা ও প্রতিবাদী চেতনার অভূর্তপূর্ব সমন্বয় দেখা দিয়েছিল এবং এই সময়ের মধ্যে এসেছিলেন অনেক ছোটগল্প সাহিত্যিক, যাদের শ্রমে-মননে ও প্রতিভায় প্রকৃতপক্ষে গড়ে উঠেছিল বাংলাসাহিত্যের নতুন প্রভাত। দেশভাগকে অবলম্বন করে এবং ছিন্নমূল জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মহৎ সাহিত্য।
‘পলদহ’ গল্পটিতে অমিয়ভূষণ মজুমদার কায়দাস্টিক গল্পের ছলে একটা সত্যগল্প বয়ান করেছেন, গল্পের মোদ্দা কথা হলো দাঙ্গার চিত্রবর্ণনা, যেখানে রাজনীতি-সমাজবিজ্ঞান ও আবহাওয়া নিয়ে জোরসে একটা আলোচনা চলছিল সেখানে একসময় মজুন্দার সত্য একটা গল্প বলে উপস্থিত সবাইকে হতবাক করে দিলো, যে কিনা ইনভেস্টিগেশন বা তদন্তকারী অফিসার জাতীয় কোনো কর্মকর্তা, তার জীবনে অনেক কিছুই ঘটে বা দেখার সুযোগ আসে, তার চিত্র এ-গল্পের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি, সাতচল্লিশে দেশভাগ হলো, দুটো দেশ পরিচয় পেলো, এপার-ওপারে কত মানুষ নিজের বাড়ি-ঘর ভিটা-মাটি ছেড়ে দেশান্তরী হলো, কে কার খোঁজ রাখে, কত পরিবারকে কত দাম দিতে হলো তার মূল্য কি শোধ করা যায়, এমনই একটা গল্প ‘পলদহ’, খবরের কাগজে প্রকাশ, এক ইঞ্চি/ দেড় ইঞ্চি অক্ষরে লেখা, ‘গাদিপোতা গ্রাম লুট’ পাকিস্তান থেকে লোক এসে গাদিপোতা লুট করে গেছে, এবং একজন নিহত আর অন্তত দশজন আহত। এবং সেই থেকে এলাকায় যে উত্তেজনা-ভয় ভয় একটা আতঙ্ক, তার তদন্ত করতে যে অভিজ্ঞতা, ডিটেইলস গল্পে তারই আলোকচ্ছটা দেখতে পাওয়া যায়। গাদিপোতা গ্রামে যে লুট তার প্রভাব কিন্তু থেমে থাকেনি, তার পাশে ‘পলদহ’ অর্থাৎ মুসলমান ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম লুট হবে, যার কারণে পলদহের মুসলমান চাষিরা গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে, মানুষ যে কতটা নির্মম কতটা ভয়াবহ হতে পারে কখনো-সখনো, তার চিত্র অংকন করতে গিয়ে মজুন্দার সর্বশেষে আবার একটা চুরুট ধরাল, ধর্মের জন্য যুদ্ধ বা জাতিগত যুদ্ধ পৃথিবীতে কখনো সুখ-শান্তি দিতে পারে না, আর যুদ্ধের প্রতিশোধ যুদ্ধ এই নীতি হয়তো মধ্যযুগে ছিল কিন্তু বর্তমান সভ্যতার এই দ্বারপ্রান্তে মানুষ তো ধর্মের জন্য যুদ্ধ কেন চাইবে, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি মৈত্রীত্বের কি কোনো দাম নেই, মানুষের জন্য মানুষ, এ-নীতি তো বিশ্বসভ্যতার একটা অংশ। গল্পের ভেতরে মানুষের যে মানবিকতা এবং হীনতা, সেই মুখোশটা খুলতে গিয়ে কখনো হয়তো দ্বিধা করেছেন কিন্তু কোথায় একটা যন্ত্রণা তা টের পেয়েছেন, দেশভাগের ফলে মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের যে কষ্ট, সহায়-সম্বলহীন হয়ে ভিখিরির দশা, আর্থিক এবং মানসিক দিক থেকে চরমভাবে ভেঙে পড়া, এবং একটা ক্ষত সারাজীবন বয়ে বেড়ানোর যে কষ্ট তারই নির্মম চিত্ররূপ পাঠক এ-গল্পে অনুধাবণ করতে পারে। নিটোল একটা ভ্রমণকাহিনী ‘পলদহ’, কিন্তু গল্পের যে কলাকৌশল এবং ভাষার শক্তি তাতে ছোটগল্পের মর্যাদায় আসীন করেছে।
‘দুলারহিনদের উপকথা’ গল্পে একটা মানবিক চিত্র উঠে এসেছে, ভূখন এবং দুলারহিনের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক হলো উভয়ে তারা সৎ ভাইবোন কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে গায়ে গা ঘেঁষে বড় হয়েছে, কেউ কাউকে ছাড়া যেমন বাঁচবে না, বাঁচার চিন্তাও করে না, বাপ-মা মারা যাওয়ার পর থেকে তাদের সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়েছে এবং ক্রমে-ক্রমে তা গাঢ়-গভীর, দুলারহিন অপেক্ষা ভূখন বয়সে ছোট, আর তাই দুলারহিন একসময় মনে করে ভূখনকে বিয়ে দেবে, অনেক অনুনয়-বিনয় করে ভূখন রাজি হয় যে সে বিয়ে করবে, সারাদিন ভূখন খেতির কাজ করে, মাঝরাত অবধি কেরোসিনের কুপির আলোয় পুতুল খোদাই করে, এভাবে সে বাড়তি রোজগার করে টাকা জমাতে থাকে। এরমধ্যে দুলারহিনের মারাত্মক অসুখ হয় এবং ভূখন জমানো টাকা দিয়ে বোনের অসুখ সারিয়ে তোলে, অসুখ থেকে সেরে উঠে দুলারহিন, এবং কিছু দেনাও হলো, দুলারহিন স্থির করল, চার কুড়ি টাকা দিয়ে যে তাকে শাদি করবে এমন পাত্রের গলায় মালা দেবে, কারণ চার কুড়ি টাকা হলে ভূখনকে বিয়ে দিতে পারবে, গল্পের মধ্যে বিনা সুতোর ভেতর যে ভালোবাসা তারই চিত্ররূপ দেখা যায়, রক্তের সম্পর্কই সব কিছু নয়, তার বাইরে সম্পর্ক থাকে, মানুষ হয়তো তার মূল্য দিতে জানে না, অথচ ‘দুলারহিনদের উপকথা’ গল্পে মা-বাপ মরা ভাইবোনের একটা মানবিক সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়, জমানো টাকা বোনের অসুখের পেছনে খরচা হলেও ভূখনের কোনো আফসোস ছিল না, অথচ দুলারহিন মনে ভারী কষ্ট পেল, শেষ উপায় বের করল, নিজে একটা বিয়ে করবে টাকার বিনিময়ে, তারপর সেই টাকা দিয়ে ভূখনের বিয়ের জন্য পণের টাকা শোধ করবে। এই উদ্দেশ্যে বেরিয়ে বিভিন্ন ছলনায় পড়ে, অবশেষে দুলারহিন ধর্ষিত হয়, ফেরার পথে ভূখনের সঙ্গে দেখা, সেদিন উন্মুক্ত নীলাকাশের নিচে ছেলেবেলায় ফিরে কাকতালীয়ভাবে কোনো এক নিষিদ্ধ ফলের স্বাদ নিয়েছিল, ভূখন মর্মান্তিক লজ্জিত হয়েও ভেবেছিল এরপরও তাদের পুরোনো ভাইবোনের সম্পর্ক ফিরিয়ে আনা সম্ভব, অথচ দুলারহিন পরিষ্কার বুঝে যায়, তার আর কখনো সম্ভব নয়। এরপর একদিন সকালবেলা দুলারহিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় ভূখনের বিয়ের ব্যবস্থা করতে, শেষাবধি নিজে বিয়ে বাজারে বিক্রি হলো কিন্তু ভূখনের বিয়ে দিতে সংসার ফেলে আর ফেরা হলো না। ভূখনের বিয়ে হলো না, সে দুলারহিনকে খুঁজে চলল, অপেক্ষা আর সন্ধান, তারপরও সে ব্যর্থ, কিন্তু খোঁজা তার আর শেষ হলো না। তিন/চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে মাটিতে শিকড় বসিয়ে ফেলে দুলারহিন, একটা সময় পাঠক দেখে, ভূখন আর দুলারহিনকে খুঁজে বেড়ায় না, তবু কী একটা খোঁজে, দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ানো নেশায় দাঁড়িয়েছে, দু-এক বছর পর-পর শহর বদলে কাজ করে বেড়ায় সে, ভালো লাগে না অনেকদিন এক জায়গায় থাকতে, কিছুদিন সে বাংলাদেশের গ্রামে মাটিকাটার কাজ করে বেড়ালো পথের ধারে-ধারে, সন্ধ্যার অন্ধকারে কুপি জ্বেলে কড়াইয়ে ভাত চাপিয়ে সঙ্গীরা যখন দিনজমানার গল্প করে, দেশের গল্প করে, কোনো কোনোদিন সে চাটাই বিছিয়ে নীরবে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকে, তারপর শুধু গল্পটাই থাকবে। এভাবেই গল্পটা শেষ হয় ঠিকই, কিন্তু একটা রেশ থেকে যায়, মানুষের প্রতি মানুষের যে কৌতুহল তার চিহ্ন এভাবেই রেখে দিতে হয় হয়তো, গল্পে যে জীবনকে ছুঁয়ে দেখার আকাঙ্ক্ষা, তার রেশ অনুভূত হয় অনেকটা সময়। ভূখন খুঁজে চলে, সে খোঁজার শেষ নেই, তারপরও সে বিরতিহীন, আরো যে খুঁজবে তার ইঙ্গিত এখানে স্পষ্ট।
বোদলেয়ার যেমন বলেছেন, ‘মানুষ প্রতিনিয়ত প্রতীকের অরণ্যের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করছে’। ‘তাঁতী বউ’ গল্পে অন্য আরেক জীবনের সন্ধান পায়, যে জীবন হয়তো একটা যুগের কথা বলে, সেই যুগটাকে পিকাসোর মতো তুলে এনে ছবির ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন, বলা চলে অমিয়ভূষণ সেখানে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন, অভিমন্যু বসাকের ছেলে গোকুল বাপের ব্যবসায় তেমন উন্নতি করতে পারল না, অবশেষে মসলিন বুনবার মতো কাজটা পছন্দ হলো, গোকুল মাঝারি গোছের গুণী বটে, শীতের গোড়ায় ইদিলশাহীতে পরগণার মেলা বসত একমাসের জন্য, সবহাটে বা মেলায় সেকালে নানা ধরণের পণ্য আসত, জমিদারেরা নিজে যেমন আসত তেমনি উজিরেরাও কেউ-কেউ হরহামেশা আসত, টাকা দিয়ে বাঁদী-বান্দা পাওয়া যেত, একবার ক’খানা মসলিন নিয়ে গোকুল যায় সেখানে বিক্রি করতে, বিক্রি শেষে, একেবারে মেলা শেষের দিকে গোকুল স্থির করল কিছু একটা ক্রয় করবে, পর্দা তুলে একটা দোকানে গোকুল দেখল কোনো মাল নেই, একটি মেয়ে শুধু বসে আছে, মেয়ে নয়, মেয়ের কাঠামো যেন, শুধু হাড়গুলো দেখা যায় সারা গায়ের শ্যামলা চামড়ার নিচে, গোকুল বুঝল কীসের দোকান এটা, কিন্তু হঠাৎ সে বলে বসল, আমি কিনব! তারপর মসলিন বিক্রির টাকা বুড়ো বিক্রেতার হাতে গুঁজে দিয়ে গোকুল বলল, আমার কেনা হলো। তারপর সেই বাঁদিকে বাড়ি নিয়ে ফিরল, পথে যেতে তার উপলব্ধি হতে লাগল, মুচিরা মাঝে-মাঝে যেমন বুড়ো গরু হাঁটিয়ে নিয়ে যায় রাস্তা দিয়ে, এও যেন তেমনি, কিন্তু বাড়ি এনে আরেক বিপাকে পড়ল গোকুল, কারণ এমন সে, যাবে বসতে বললে বসে, শুতে বললে শোয়, খেতে বললে খায়, এমনি করে দিন যায়, একদিন রাত্রে প্রদীপের আলোয় গোকুল নির্বাক হয়ে লক্ষ করল, বিশ্রী-বিশ্রী করে চোখ ফিরিয়ে নিলেও ওর বক্ষের বৃত্তাভাস-নিতম্বের বিস্তৃতি-উরুর মসৃণতা আর সব ছাপিয়ে তার চোখ দুটো। গোকুল মোহিত হলো, নিজেকে অন্য জগতে হারিয়ে ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায়, স্বপ্নের জাজিমে রাত্রির মতো অন্ধকারে হারিয়ে নির্বাক প্রতিচ্ছবি, একদিন বাঁদির কানের কাছে মুখ এনে বলল, একটা ছেলে না হলে চলছে না… বাঁদি হতবাক হয়, থরথর করে কাঁপে, সব কথা তার হারিয়ে গেছে, একদিন ঘোর অন্ধকারে গোকুলের নির্দেশে বাঁদি গাঁয়ের মাঠের এক ফকিরের কাছে যায়, ভোরের আগে বাড়ি ফেরে, গোকুল দেখে খয়েরি টিপ নেই, চোখের কাজল লেপ্টে একাকার, পরিক্লান্ত-সর্বহারা দৃষ্টি। তারপর রাত করে ভয়ের মধ্যে যাওয়া চলতে থাকে। এরমধ্যে হঠাৎ ফকিরটা মরে গেল, একদিন বাঁদি কথা বলল— হবে তুমি পাবে একটা ছেলে!
পাঠক দেখতে পায়, বাঁদির ছেলে হয় কিন্তু পাঁচ মাস-সাত মাস এমনকি বছর গেল কিন্তু ছেলে বাড়ল না, দেখলে মনে হয় কতকালের বুড়ো, হাসে না, গোকুল কবিবাজ-বদ্যি সবই করে কিন্তু ফল শূন্য রয়ে যায়, একবার সিদ্ধস্থানের ঠাকুরাণীকে নিয়ে এল, সে তাঁতীবউকে দেখে বললো, তুই বউ বদলা, গোকুল, এ বউয়ের রিষ্টি যোগ আছে, এর কাছে ভালো ছেলে তুই সাতজন্মেও পাবি না। গোকুল এতটাই ভালোবাসত তাঁতীবউকে যে সিদ্ধার কথা শুনে বিশ্বাস তো করলই না বরং মাথায় আগুন চেপে বসল, বাড়ি থেকে খিস্তি-খেউড় করে বের করে দিল। এদিকে বাঁদি কিন্তু বলতে থাকল, বোধহয় আমার রিষ্টি যোগ আছে, বউ বদলাও, গোকুল হাসির কথা ভেবে উড়িয়ে দিল, অথচ তাঁতীবউ নাছোড়বান্দি, একদিন সকালবেলা ভীষণ বিরক্ত এবং রাগ করে গোকুল বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল, তারপর অনেক অপেক্ষা করেও তার কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না, সে সত্য সত্যি নিরুদ্দেশ হলো, কঙ্কালসার ছেলেকে কোলে নিয়ে তাঁতীবউয়ের দিন কাটতে লাগল, পয়সা উপার্জনের ফিকির বার করল, জোলারা আসে কাটা সুতো নিতে, একদিন গাজনের মেলা থেকে কয়েক সাথীর সঙ্গে বাড়ি ফিরতে ছোট-ছোট ছেলেদের দেখে সে থমকে যায়, কার ছেলে গো! দেবশিশুর মতো দেখতে, এমন ছেলে যদি তার হতো, কিন্তু সঙ্গের ঝি-টিকে প্রশ্ন করতেই রক্তহীন মুখে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। সেই রাজবাড়ির জমিদার বাবুর ছেলে ওরা, যে বাবু দশগুণ মূল্য দিয়ে কিনতে চেয়েছিল, যাকে তাঁতীবউ ঘৃণায় বলেছিল, ছি ছি, তোমাকে দেবতা বলেছি, ছি ছি ছি…
সচেতন পাঠক দেখে, তারপর একদিন গোকুল বাড়ি ফেরে, কিন্তু সে রকমটি নেই, কেমন ভেঙে গেছে, অনেক কবরেজ বাড়ি হাঁটাহাঁটি করলেও একদিন গোকুল চলে গেল, পৃথিবীটা তখন কেমন তোলপাড় হয়ে গেল তার কাছে। নারীসত্তার ক্রমবিকাশের ছবিটা আমরা তাঁতীবউয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ দেখতে পায়, গাজনতলার হাটে দেবশিশুদের মুখ দেখার পর ওর মন আঁকুপাঁকু করতে থাকে, একটা সুস্থ শিশু তার চায়, তারপর অন্ধকারের বুকে লাথি মেরে নিজেকে যথাসাধ্য সাজিয়ে তুলে ভবিষ্যতের পৃথিবীর দিকে হেঁটে গেল, ঠাণ্ডা জলো হাওয়ায় উঠোন পার হয়ে জমিদারবাড়ির বাগান ধরে ঘরে ঢুকল, প্রবল প্রতিরোধে হৃৎপিণ্ডকে ঠেলে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়, জমিদারের সঙ্গে যৌনমিলনের ফলে যে ছেলে আসবে সে হবে ওমন দেবশিশু, তার রিষ্টি যোগের কলঙ্ক মুছে যাবে, সুস্থ-সুন্দর অনাগত পৃথিবী মুখ বাড়িয়ে আছে, সেখানে তাঁতীবউ একজন সার্থক মা হবে, সমস্ত অপবাদ মুছে আগামী সূর্য ঝলমল করে হাসবে।
‘উরুন্ডী’ গল্পে বাহান্নজনের মধ্যে বাইশজন যাত্রী, যদিও সবাই উরুন্ডী ছেড়ে যেতে চায় না, পুলিন অবশ্য এক্রোডাস শব্দ ব্যবহার করে বুঝিয়েছে মিশররাজ ফারাও-এর অত্যাাচার থেকে বাঁচতে একদল লোক যখন পিতৃভূমির খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল, তাকে এক্রোডাস বলা হয়ে থাকে। এই যাত্রাপথে পুলিনদের দলে এসেছে মৃত্যু, যার ফলে যাত্রীর সংখ্যা কমেছে, যদিও বরাবরই শোভার কাছে উরুন্ডী অন্যরকম জায়গা, সে চায় থাকতে এখানে, বিশ বছরেই তার সিঁথি মুছে ফেলতে হয়েছিল, উরুন্ডীর জল যেমন তার কাছে মিষ্টি, সুপেয় আর ঠাণ্ডা, শেষ অবধি এই মায়াবী আকর্ষণ বড় হয়ে ওঠে, শোভার প্রশ্ন ওই একটাই, এই উরুন্ডী, একি ভালো না বলো…
এ-গল্পে মানুষের মনের ভেতর দিকের কথাগুলো উঠে এসেছে, নিজ বাসভূমি ছেড়ে কেউ কি অন্য কোথাও থাকতে পারে, জন্মভূমি টান হয়তো একেই বলে, মানুষ জন্মভূমির টানে বারংবার ছুটে আসে এবং এটাই একজন মানুষের প্রকৃত প্রবৃত্তি, গল্পে একটা চিত্র উঠে এসেছে, সে চিত্র আমাদের অন্দরমহলের চিত্র, আমাদের মনস্তাত্ত্বিক চেতনার চিত্র, যারা ভালোবাসতে জানে, ভালোবাসা এখনো হয়তো তাদের কাছে উপেক্ষার কিছু নয়, তারপরও একটা প্রশ্ন সবার কাছে, জীবন কেন এতটাই ছোট, গল্পের শরীরে যে ভাষাবিন্যাস দেখতে পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যায় অমিয়ভূষণ মজুমদার কতটা শক্তিশালী সাহিত্যিক।