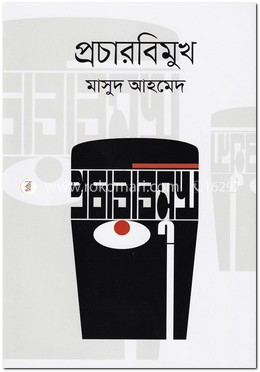
গ্রন্থ: প্রচারবিমুখ, লেখক: মাসুদ আহমেদ, প্রকাশক: অন্যপ্রকাশ, প্রচ্ছদ: ধ্রুব এষ, মূল্য: ৳২২৫/, প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি- ২০২০
খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিক মাসুদ আহমেদের ‘প্রচারবিমুখ’ গ্রন্থটি একটি বহুমাত্রিক জীবনালেখ্য। এই গ্রন্থে রকমারি স্বাদের মোট সাতটি গল্প আছে। প্রথম চারটি গল্পের পটভূমি মুক্তিযুদ্ধ। বাকি তিনটি গল্পের পটভূমিতে রয়েছে সমাজের বিচিত্র অসঙ্গতি, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও অসংযত মুনাফার নেশা। প্রথম গল্প ‘মসি’ শুরু হয়েছে এভাবে-
‘ঢাকা সেনানিবাসের সিগনাল সেন্টার। ১৯৭১-এর পয়লা পৌষ, ১৬ই ডিসেম্বর। খাকি পোশাক পরনে দশ-বারোজন দীর্ঘদেহী পুরুষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে। পাশের বিল্ডিং এদের হেড কোয়ার্টার ছিল। মিত্রবাহিনীর বেদম বিমান আক্রমণে ওটি এখন বিধ্বস্ত। তাই এই বিল্ডিংয়ের কনফারেন্স রুমে এরা স্থান নিয়েছে। একজন ছাড়া এদের বাকি সবার বাড়ি অনেক পশ্চিমে এগার শ’ মাইল দূরে। ওই একজন বাঙালি। এরা সবাই পাকিস্তান মিলিটারির কমিশন অফিসার। সিনিয়রিটির দিক থেকে বাঙালি কর্তাটির স্থান সপ্তমে। একটা সিঙ্গেল সোফায় বসা একজন তাকে বললেন, ‘আচ্ছা হুদা, তুমি না আমাদের কবিতা আর গানের কথা শোনাতে প্রায়ই! তো আজকে আবহাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে সেরকম কিছু শোনানোর নেই তোমার থলেতে?’
এই অংশটুকু পড়ে পাঠকের মনে হবে এটি একটি রসঘন হালকা স্বাদের গল্প। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হয়েই পাঠক বুঝতে পারবেন এটি একটি চরম আগ্রাসী অশুভ শক্তির অন্তিম পরিণতির সকরুণ চিত্রকল্প- একটি রক্তক্ষয়ী নাটকের অন্তিম দৃশ্যায়ন। দখলদার পাকবাহিনী ততক্ষণে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেছে। বিবিসি’র দুজন ঢাকা প্রতিনিধি পরাজিত পাকবাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল নিয়াজীকে ছেঁকে ধরেছেন; প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছেন। লে. জেনারেল নিয়াজী অধিকাংশ প্রশ্নেরই কোনো সদুত্তর দিতে পারছেন না। তার মধ্যে বিবিসি সাংবাদিকের একটি প্রশ্ন ছিল এমন- ‘কলম ও তরবারির মধ্যে শক্তিশালী কোনটিকে মনে করেন?’ উত্তরে নিয়াজী বললেন, ‘আমরা তরবারির লোক।’ বিবিসি সাংবাদিক সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলেন, ‘আজ বিকাল ৫.০০ মিনিটে হাতে কি কলম ছিল না তরবারি?’
নিয়াজী স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, ‘লিখতে তো কলম লাগবেই।’
দ্বিতীয় গল্পের পটভূমিও মুক্তিযুদ্ধ। গল্পের নাম ‘ভাইয়া’। ঘটনাস্থল তৎকালীন অধিকৃত বরিশাল জেলার মুলাদী থানা। সময়কাল ঊনিশশ’ একাত্তরের অক্টোবর মাস। যুদ্ধের কৌশলগত কারণে মুলাদী থানার দারোগার চেয়ারে অধিষ্ঠিত আছেন পাঞ্জাবি লে. কর্নেল গুলজারী ভাট্টি। তাঁর হাতে তিনজন মুক্তিযোদ্ধাসহ ছয়জন বাঙালি বন্দী হয়েছে। সেই মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্য থেকে মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর নামের এক যুবক কর্নেল গুলজারীর সাথে দেখা করতে চায়। নিজের পরিচয় দিয়ে বলে গুলজারীর ঘনিষ্ট বন্ধু জামরুদ দুর্গের সাঁজোয়া কোম্পানির কমান্ডার মেজর আলমগীর তার আপন বড়ো ভাই। কর্নেল গুলজারী তথ্য যাচাই করে নিশ্চিত হন জাহাঙ্গীরের দেওয়া তথ্য সঠিক। তিনি মেজর কোরেশীকে ডেকে জাহাঙ্গীরকে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দেন। গল্পটি শেষ হয়েছে এভাবে, জাহাঙ্গীর কৃতজ্ঞতার হাসিতে মুখ ভরিয়ে থানা থেকে বের হয়ে আসে। পনেরো সেকেন্ড পরে থানার বিজন উঠোনের মধ্যে একটা গুলির শব্দ পাওয়া যায়।
তৃতীয় গল্প ‘শাসক’ এর কাহিনি আবর্তিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পরিচালনা ও পরিণতির দোলাচল নিয়ে। ঘটনার তারিখ সতের ডিসেম্বর ঊনিশশ’ একাত্তর। মুক্তিযোদ্ধা লে. কর্নেল এবাদুর রহমান ও লে. ঠান্ডু মিয়ার মধ্যে যুদ্ধের কৃতিত্ব ও দায়ভার নিয়ে বিতর্ক চলছে। সেই বিতর্কের এক পর্যায়ে এবাদুর রহমান উপসংহার টানছেন এভাবে- ‘আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় যেসব দেশ ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশ ও ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে শুধু নিজেরা লড়াই করে স্বাধীন হয়েছে সেখানে নিজেদের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে অনেক বছর ধরে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ চলেছে। তাতে অনেক প্রাণহানি ঘটেছে। আমাদের তা হবে না।’
মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা চতুর্থ গল্প ‘জীবিকা ও আততায়ী’-তে চিত্রায়িত হয়েছে ৪২নং ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের অধিনায়ক লে. কর্নেল শরীফ মোহাম্মদ কানোয়ার বনাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নিবেদিত প্রাণ ইংরেজির অধ্যাপকের গুরুশিষ্য সম্পর্কের টানাপোড়েন, দখলদার অধিনায়কের জাত্যাভিমান, অতীতচারিতা ও নিষ্টুর আগ্রাসী স্বভাবের আন্তঃক্রিয়া। ১৯৬৯ সালের এক শরৎকালে এই অধ্যাপকের কাছেই তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ নিয়েছিলেন। গল্পের শেষাংশে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অখণ্ড রক্ষার অজুহাতে সেই অধ্যাপককেই তিনি গুলি করার নির্দেশ দেন।
গ্রন্থের পঞ্চম গল্প ‘স্থপতি’তে সকল মানবিকতা, মমতা ও ভালোবাসাকে ছাপিয়ে অসংযত মুনাফার কদর্য লোভ ও পিপাসার ছবি চিত্রায়িত হয়েছে। সামাজিক সমস্যার সমাধান নয়, অব্যাহত মুনাফার লোভে তাকে জিইয়ে রাখার যে কায়েমী প্রয়াস ও তৎপরতা, তারই দালিলিক প্রমাণ যেন এই গল্প। গল্পের অক্ষরে অক্ষরে ছড়িয়ে আছে সমাজের অসাধু বণিক শ্রেণির অন্তঃসারশূন্য প্রতিশ্রুতি ও মানবিকতাশূন্য মুনাফার বেসাতি। নিঃসন্দেহে এটি একটি নির্মম সমাজচিত্র।
ষষ্ঠ গল্প ‘বাহির পানে’র কাহিনি নির্মিত হয়েছে দুই সম্প্রদায়ের দুই প্রতিবেশীর পারস্পরিক সম্পর্ক, মানবিকতা ও শ্রেণিস্বার্থকে কেন্দ্র করে। গল্পের মূল দুই চরিত্র ফয়জুল ও দেবনাথ। ফয়জুল পেশায় আইনজীবী। দেবনাথ একজন নিরীহ হোটেল ব্যবসায়ী। ২০১৪ সালের এক সাম্প্রদায়িক হামলায় দেবনাথের বাড়ি ও সম্পত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। দেবনাথ পরিবার-পরিজন নিয়ে সীমান্ত পাড়ি দেন। প্রতিবেশী ফয়জুল প্রতিবেশীসুলভ চিন্তায় দেবনাথের সম্পত্তি রক্ষা করেন। পরবর্তীতে দেশান্তরী দেবনাথের কাছ থেকে নগদ মূল্যে সেই সম্পত্তি হাতিয়ে নেন। এখানে দীর্ঘদিনের একজোড়া প্রতিবেশীর মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস, লোভ, হীনম্মন্যতা ও আদিম মনোবৃত্তির নান্দনিক চিত্র আঁকা হয়েছে।
গ্রন্থের নামকরণের নেপথ্যের গল্পটি হলো সপ্তম গল্প ‘প্রচারবিমুখ’। এটি একটি অসাধারণ স্যাটায়ার। গ্রন্থকার তাঁর স্বভাবসুলভ রম্য ও রঙ্গরসের মাধ্যমে সমাজের বিচরণশীল নানা চরিত্রের বিচিত্র অসংগতি, দ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধিতাকে চিত্রায়িত করেছেন। গল্পের মাদানী আল সাবরী চরিত্রটি যেনো এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজেরই একজন প্রতিনিধি, যার অর্থহীন চটকদার বাক্যের ফুলঝুড়ি ছাড়া দেবার আর কিছু নেই।
গল্পটি কিংবদন্তিতুল্য রম্যসাহিত্যিক সমারসেট মমের ‘দি লাঞ্চিয়ন’ গল্পের সেই চরিত্রটিকে মনে করিয়ে দেয়, যে রসনাবিলাসী রমণী একটার বেশি কিছু খাবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্রমাগত একটার পর একটা খাবার গলাধঃকরণ করতে থাকেন। ফলশ্রুতিতে নিমন্ত্রণকারী ভদ্রলোক প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েন। ‘প্রচারবিমুখ’ গল্পের মাদানীও মাইকের সামনে গিয়ে ‘আমি আজ তেমন কিছু বলব না’ বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্রমাগত দীর্ঘ, বিরক্তিকর ও অসত্য আত্মপ্রচারণামূলক বাগাড়ম্বর করতে থাকেন। পাঠক এই গল্পে চারপাশের এমন এক চেনা জগৎকে অভিনব চিত্রকল্পে আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন, যে জগৎ আমাদের প্রাত্যহিক সুখদুঃখ ও বিড়ম্বনার নৈমিত্তিক অনুষঙ্গ।
‘প্রচারবিমুখ’ গ্রন্থের প্রতিটি গল্পই প্রকৃতি, পটভূমি ও বিষয় বৈচিত্র্যে অনন্য। পাঠক এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে আবারও আবিষ্কার করবেন গ্রন্থকারের একটি নিজস্ব গদ্যশৈলি আছে, যা একেবারেই স্বতন্ত্র। বর্ণনার বাহুল্য নেই, আবার তথ্যের ঘাটতিও নেই। মানবজীবনের যে অংশগুলো সাধারণের লেখায় বিশদ উল্লেখ থাকে, সেখানে তিনি সংক্ষিপ্ত। আবার অন্যরা যেখানে সংক্ষেপ করেন, সেখানে তিনি বিস্তৃত। কখনও কখনও দেখা যায়, সাধারণের উপেক্ষিত বিষয়গুলোই তাঁর রচনার মূল নির্যাস। বর্তমান গ্রন্থেও গ্রন্থকারের এই স্বকীয়তা বিশেষভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পাঠক লক্ষ্য করবেন, লেখকের স্বকীয় গদ্যের মায়াবী বর্ণনায় কাহিনি যেনো আরও সৌকর্যময় হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটি লাভ করেছে এক ভিন্নমাত্রা, যা পাঠককে নিয়ে গেছে কল্পরাজ্যের এক প্রতীকী জগতে।
শাহেদ ইকবাল

