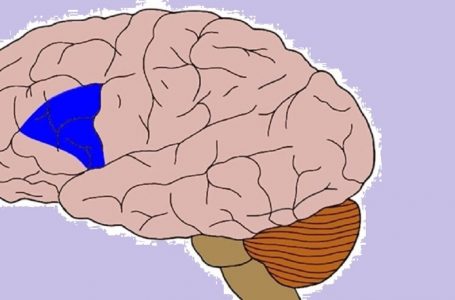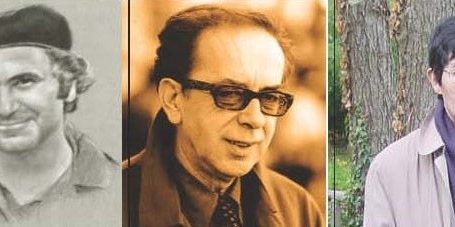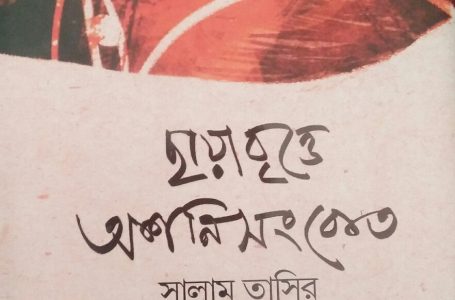আকবর আলি খান গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি ছিলেন একজন সম্মানীয় মুক্তিযোদ্ধা। দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক সমস্যায় তিনি সবসময় বস্তুনিষ্ঠভাবে জাতিকে পরামর্শ দিয়েছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি হবিগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক বা এসডিও ছিলেন এবং যুদ্ধকালীন সক্রিয়ভাবে মুজিবনগর সরকারের সাথে কাজ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান সরকার তার অনুপস্থিতিতে তার বিচার করে এবং ১৪ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি সরকারি চাকরি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার সাথে যুক্ত ছিলেন। ২০০৬ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন উপদেষ্টা ছিলেন। পরবর্তী সময়ে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়ার আশঙ্কায় তিনি তিনজন উপদেষ্টার সাথে একযোগে পদত্যাগ করেন। তিনি রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন।
তার প্রয়াণে শ্রদ্ধা-স্মরণে তরুণ প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক শফিক হাসানের নেওয়া একটি সাক্ষাৎকার এখানে প্রকাশ করছি।
সাক্ষাৎকার-
সমাজবিজ্ঞানী আকবর আলি খানের জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে। নবীনগর হাইস্কুল থেকে পাস করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। ১৯৬১ সালে আইএসসি পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে ১৯৬৪ সালে সম্মান ও ১৯৬৫ সালে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। শিক্ষকতা করেছেন, সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়েছেন; নানামুখী দায়িত্ব পালন করেছেন। শেষ জীবনে আবার ফিরেছেন শিক্ষকতায়, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন। ২০১৩ সালের ১০ জুলাই গুলশানস্থ আকবর আলি খানের বাসা থেকে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন শফিক হাসান
আপনার ছোটবেলা কেমন ছিল?
আমি ১৯৪৪ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে জন্মগ্রহণ করি। ঐ সময় নবীননগর খুবই একটা ছোট শহর ছিল। এলাকার লোকসংখ্যা ছিল হাজার দশেক। খুবই প্রাকৃতিক ও নিবিড় পরিবেশে আমরা বড় হয়েছি। সেখানে সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক সম্প্রীতি ছিল। সব মিলিয়ে নবীননগরে একটা আনন্দময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমাদের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে।
শৈশবের কোন স্মৃতিটি এখনো টানে?
স্মৃতির মধ্যে যা আছে তার সবটুকুই নবীনগরের প্রাকৃতিক পরিবেশকে ঘিরে। ওখানে অনেক গাছ ছিল, নদী ছিল। গাছপালাতে ঘিরে থাকত চারপাশ। এখন তো সব মরুভূমির মতো। কষ্ট লাগে। জনসংখ্যা বেড়েছে অনেক। সেই তুলনায় মানুষের আয় বাড়েনি। ফলে এটা এখন একটি ঘিঞ্জির মতো শহরে পরিণত হয়েছে। শহরেরও সৌন্দর্য নেই, পাশের তিতাস নদীটিও মরে গেছে।
বাল্যবন্ধুদের কথা মনে পড়ে?
আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই মরে গেছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্স করেছেন। কিন্তু পরে অর্থনীতিতে পিএইচডি করলেন কেন?
আমি আসলে মানুষকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলাম। মানুষ সম্পর্কে জানতে ও তাকে বিশ্লেষণ করতে হলে সমাজবিজ্ঞানই আসল মাধ্যম। সমাজবিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে অর্থনীতি। তাই আমি অর্থনীতিচর্চার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।
লাহোরের সিভিল সার্ভিস একাডেমি থেকে এসডিও হিসেবে বদলি হয়ে হবিগঞ্জে ফেরেন। ১৯৭০-এর নির্বাচন পরিচালনা করেছিলেন। সেই সময়ের প্রেক্ষাপট ও নির্বাচনের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?
আমি সত্তর সনের নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার ছিলাম। সেখানে তিনটি নির্বাচনী এলাকা, পাঁচটি প্রাদেশিক এলাকা ছিল। নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে সেখানকার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পর্যাপ্ত সহযোগিতা পেয়েছি। রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকেও মোটামুটিভাবে সহযোগিতা পাওয়া গেছে। সুতরাং নির্বাচনের সময় কোনো সহিংসতা হয়নি। নির্বাচনে কারচুপিরও কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। এই নির্বাচনের প্রাদেশিক বিধানসভার একটি আসনে আওয়ামী লীগ পরাজিত হয়েছিল। এছাড়া বাকি সব আসনেই আওয়ামী লীগের জয় হয়।
সত্তরের পরে অনেক নির্বাচন দেখেছেন বাংলাদেশে। বর্তমান সময়ের নির্বাচনের সঙ্গে যদি তুলনামূলক মূল্যায়ন করেন…।
সত্তরে আমরা যখন নির্বাচন করেছি তখন কেন্দ্রীয় সরকার রিটার্নিং অফিসারদের প্রতি কোনো ধরনের প্রভাব ফেলত না। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে কোনো রকম বেআইনি নির্দেশ পাইনি। তখন তো পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনামল। তখনও নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পেরেছে। নির্বাচন কমিশন থেকে আমাকে লিখিতভাবে একটা উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের বিভাগীয় প্রধান আমার কাছে এসে বলেন, নির্বাচনে স্কুটিং করার সময় আমি যেন যেই প্রার্থী নির্বাচন করতে চায় তাকেই যেন নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ দিই। তো স্কুটিংয়ের সময় দেখা গেলো এমন একজন দরখাস্ত করেছেন যিনি সিলেট জেলা প্রশাসনের কন্ট্রাকটর। তখন তো নির্বাচনী নিয়ম অনুযায়ী সরকারি কোনো কন্ট্রাকটর জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। সে কারণে আমি তার মনোনয়নপত্র বাতিল করি। এরপর ঐ ভদ্রলোক নির্বাচন কমিশনে আপিল করেন। হাইকোর্টেও আইনজীবীর মাধ্যমে আইনি প্রক্রিয়ায় বিষয়টি মোকাবেলা করে। অবশ্য পরে আমার সিদ্ধান্তই বহাল ছিল।
সরকারি কর্মকর্তা হয়েও তখন অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। চাকরি হারানোর ভয় ছিল না?
চাকরি যাওয়ার ভয় ছিল কিন্তু ওই সময় আমার মতো অনেক চাকরিজীবী চাকরি রেখে আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। নিজের যেটা বক্তব্য ছিল সেটা হচ্ছে— আমি নিজে দেখেছি আমার হাত দিয়েই তো নির্বাচনে জনগণের মনোনীত প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে। একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার কোনো যৌক্তিক কারণ ছিল না। তখন ইয়াহিয়া খান অনৈতিকভাবে ক্ষমতা দখল করে রেখেছিলেন। সে কারণে ঐ সময় বঙ্গবন্ধু যেসব নির্দেশ দিতেন সেগুলো ছিল বৈধ নির্দেশ। কারণ তখন তিনিই ছিলেন জনপ্রতিনিধি।
মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার আগেই আপনি তো গেরিলা যোদ্ধাদের অস্ত্র জোগান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং লিখিত আদেশ তৈরি করেন। এর পেছনে কারও পরামর্শ, সাহস বা অনুপ্রেরণা কাজ করেছে কি?
কারও পরামর্শ বা অনুপ্রেরণা ছিল না। তবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে আমার বেশ সময় লেগেছিল। কারণ অর্থ কার মাধ্যমে দেওয়া হবে এটা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক ছিল। যারা আওয়ামীপন্থী গেরিলা ছিল তাদের পক্ষ থেকে অর্থ চাওয়া হচ্ছিল আবার ঐ সময় খালেদ মোশাররফ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তাদের পক্ষ থেকেও অর্থ চাওয়া হচ্ছিল। তখন মূলত এই দুই গ্রুপের মধ্যে এটা নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। তখন আমাকে সহযোগিতা করেছিলেন কর্নেল রব। তিনি তখন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনিই আমাকে পরামর্শ দিলেন— অর্থ দিতে চাইলে আওয়ামী সমর্থকদের দাও।
মুক্তিযুদ্ধের তহবিল সংগ্রহের জন্য ব্যাংকের ভল্ট থেকে টাকা, খাদ্য জোগানের জন্য গুদামঘর খুলে দিয়েছিলেন…।
খাবারের জোগান দিতে হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বিবেচনায় রেখে। আমার ওদিক দিয়ে তখন মুক্তিযোদ্ধাদের যাতায়াত ছিল। ঐখানে একটি সরকারি খাদ্য গুদামও ছিল। আমি গুদামের কর্মকর্তাকে বললাম, এদের (মুক্তিযোদ্ধাদের) খাবার দিতে হবে। সে তখন বলল, আপনি লিখিত অনুমতি দিলেই কেবল আমি খাবার গুদাম উন্মুক্ত করতে পারি। আমার লিখিত অনুমতির ভিত্তিতে খাদ্য গুদাম খোলা হল। এই গুদাম থেকে আমরা চাল, আটা, গম, চিনিসহ বেশকিছু খাবার সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। পরে দেখলাম ওইখানে অবস্থান করাটা আমার জন্য বিপদজনক। ওখান থেকে চলে এলাম। ওই খাদ্য গুদামের কর্মকর্তাকেও আসতে বললাম। কিন্তু সে আমার কথা শুনল না। দুঃখজনক ঘটনা হল, পরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাকে হত্যা করে। আমার জন্য এটা খুব বেদনাদায়ক ঘটনা, যদিও আমি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছি। ব্যাংকের বিষয়টা হচ্ছে, আগরতলা থেকে আমাকে টাকা সংগ্রহের জন্য বলা হল এবং সেখান থেকে একটি ট্রাকও পাঠানো হয়েছিল। আমি সেই ট্রাকে করে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। এক্ষেত্রে ব্যাংক ম্যানেজারও টাকা দিতে ইচ্ছা পোষণ করেনি। আমি জোর করলে সে বলল, আপনি লিখিত আদেশ দিন। আমি এখানেও লিখিত আদেশ দিয়েছি। এরপর এখান থেকে আমি চলে আসি। তবে ব্যাংক ম্যানেজারকে মরতে হয়নি।
মুজিবনগর সরকার গঠনের মাস খানেক পর আপনাদের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ হয়। কে প্রথম যোগাযোগ করেছিলেন?
এখানে নেতৃত্বে ছিলেন হোসেন তৌফিক ইলাহী, কাজী জহির উদ্দীন, খসরুজ্জামান চৌধুরী। আরও বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তা ছিলেন আমাদের সঙ্গে। রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ছিলেন এম আর সিদ্দিকী, জহুর আহমেদ চৌধুরী। এ সময় আমাকে এখানে দুই সপ্তাহকালেরও বেশি সময় অবস্থান করতে হয়। তখন আমার প্রধান কাজ ছিল শরণার্থীদের ক্যাম্প থেকে খবর সংগ্রহ করা। এক্ষেত্রে ভারতের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ত্রিগুণা সেনের সঙ্গে আমি বিভিন্ন স্থানে যাই। আগরতলা থেকে শিবচর পর্যন্ত যারা শরণার্থী ছিল তাদের সমস্যা এবং যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য ট্রেনিংয়ে আছে তাদের খোঁজ রেখেছি। এসময় সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমাকে চা সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে আমি ও কাজী জহির উদ্দীন সাহেব প্রায় দশদিন চা বাগানে থেকেছি। ম্যানেজারদের সঙ্গে কথা বলে উৎপাদিত চা সেখানে যতটুকু ছিল তা সংগ্রহ করেছি। পরে চা-গুলো বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আমরা বিক্রি করতেও পেরেছি কিন্তু ভালো দাম পাইনি। অনেক চা নষ্ট হয়ে গেছে। আসলে ত্রিপুরায় তখনো চায়ের প্রচলন ওভাবে শুরু হয়নি। তখন চা জনপ্রিয় ছিল কলকাতায়। আমাদের পক্ষে কলকাতায় যাওয়া খুব সহজ ছিল না।
পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসন গড়ে তোলার প্রয়োজন কেন অনুভব করলেন?
আমরা যখন আগরতলায় যাই তখন বাংলাদেশ সরকারের কোনো প্রশাসন ছিল না। তখন মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ, রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও অন্যান্য কাজের জন্য একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা খুব জরুরি হয়ে পড়ে। প্রথমত আগরতলায় আমাদের কার্যক্রম শুরু হয়। তখন আমাদের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ ছিল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার জন্য। পরে মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসন তাদের অধীনে চলে যায়। তারা তখন পূর্বাঞ্চল প্রশাসন বাদ দিয়ে সারা দেশকে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করে। তখন মুজিবনগর সরকারের সচিবালয়ে যোগ দিই।
পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসনের সঙ্গে কোনো জনপ্রতিনিধির সম্পর্ক ছিল কি?
শুরুর দিকে জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এম আর সিদ্দিকী ছিলেন। পরে জহুরুল কাইয়ূম ও কর্নেল রউফ সাহেবও ছিলেন। যারা ছিলেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। এছাড়া আরও কয়েকজন স্থানীয় এমপি আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।
ঐ সময় ত্রিপুরার প্রাদেশিক সরকার আপনাদের কেমন সহযোগিতা করেছে?
ত্রিপুরা সরকার আমাদের নানানভাবে সহযোগিতা করেছে। তবে ত্রিপুরা সরকার আমাদের যতটা সহযোগিতা করেছে তার চেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছে ত্রিপুরার সাধারণ জনগণ। তারা আমাদের প্রাণঢালা সমর্থন দিয়েছেন। যখন আগরতলায় যাই তখন আমাদের কোনো বাড়ি ছিল না। তখন স্থানীয় এক ভদ্রলোক তার বাগান বাড়ি আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। এভাবে যখন যেখানে গিয়েছি ত্রিপুরার মানুষ তখন অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছে। এক্ষেত্রে একটি বিষয় ইতিবাচক ছিল, আমাদের বাংলাদেশের অনেক অভিবাসী সেখানে ছিলেন, যারা আবেগ আপ্লুত হয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। আর কলকাতার অভিজ্ঞতাটা কিন্তু এমন সুখকর ছিল না। আমরা কলকাতার যেদিকটায় ছিলাম সেটি ছিল মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা। কলকাতার মুসলমান মুক্তিযোদ্ধাদের খুব একটা ভালো চোখে দেখতেন না।
মুজিবনগর সরকারে আপনার কর্মজীবন শুরু হয় উপসচিব হিসেবে। ঐ সময়ের কাজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যদি বলতেন?
আমাদের মুজিবনগর সরকারের অফিস যেখানে ছিল সেখানে জায়গা ছিল খুব সামান্য। পর্যাপ্ত চেয়ার টেবিলও ছিল না। সব সময় বিভিন্ন কারণে সেখানে মানুষের ভিড় লেগেই থাকত, বিশেষ করে শরণার্থীদের। এসব কারণে আমরা অফিসিয়াল কাজ অফিসে করতে পারতাম না। আমাদের অফিসের বিপরীত দিকে ব্রিটিশ কাউন্সিলের একটি অফিস ছিল, অনেক সময় সেখানে বসেই আমরা সাচিবিক দায়িত্ব পালন করেছি। এসব সমস্যার পরেও আমরা সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পেরেছি। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আমরা সবাই ছিলাম একই আদর্শে ও চেতনায় বিশ্বাসী। এ কারণে একজন অন্যজনকে সহযোগিতা করতাম। অন্যদের সঙ্গে কথা বললে নিজেদের সাহস ও মনোবল অনেক বেড়ে যেত।
মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সংবাদ আপনারা কীভাবে সংগ্রহ করতেন?
আমাদের নিজস্ব লোকবল তথ্য আদান প্রদানের জন্য নিযুক্ত ছিল। এ বিষয়ে ভারত সরকারও সহযোগিতা করেছে।
১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে আপনি কোথায় ছিলেন?
১৬ ডিসেম্বরে আমি ছিলাম কলকাতায়। ঐদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমি খবরটা শুনলাম। পাকিস্তানি বাহিনী আজ আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ করবে। মনের ভিতরে অন্যরকম একটি অনুভূতি কাজ করছিল তখন। আমি প্রথমে মুজিবনগর সরকারের অফিসে যাই। এরপর সোজা বাসায় এসে রেডিও নিয়ে বসি। অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি।
বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আপনার কর্মজীবন কীভাবে শুরু হয়?
বাংলাদেশ সরকার শুরুতে আমাকে সিলেট জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেয়। কিন্তু আমি ঐ পদে জয়েন করিনি। এর কারণ ছিল আমাকে সিলেটের ডিসি হিসেবে যোগ দেওয়ার পর বিশেষ এক ব্যক্তির স্বার্থে কাজ করতে অনুরোধ জানানো হয়। আমি এতে আপত্তি করি এবং ঢাকাতেই থেকে যাই। পরে আমাকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ দেওয়া হয়।
১৯৭৩ সালে সরকারি চাকরি ছেড়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। এটা স্বেচ্ছায় করেছিলেন নাকি কোনো চাপের মুখে?
না কোনো চাপের মুখে নয়। আমি নিজে থেকেই চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু বঙ্গবন্ধু আমাকে বাধা দেন। তিনি চাকরি ছেড়ে দিতে নিষেধ করেন। পরে আমি শিক্ষকতা শুরু করলেও বঙ্গবন্ধু সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আমাকে বহাল রেখেছিলেন এবং বলেছিলেন যে কোনো সময় তোমার ইচ্ছা হলে ফিরে এসো।
বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আপনার বিশেষ কোনো স্মৃতি আছে?
বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমি খুব একটা ঘনিষ্ঠ ছিলাম না। আমি যেসব মন্ত্রণালয়ে কাজ করেছি বঙ্গবন্ধু এসব মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ করতেন না। দু’চারটি সভায় আমি তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি এবং এক সভায় শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আমি তাঁকে সমর্থন দিয়েছি। স্মৃতি বলতে এটুকুই।
কানাডায় যখন পিএইচডি করতে গেলেন, ওখানকার শিক্ষা পরিস্থিতির সঙ্গে বাংলাদেশের কী পার্থক্য অনুধাবন করেছিলেন?
কানাডায় যখন পিএইচডি করতে যাই তখন মানগত দিক ওখানকার শিক্ষামান অনেক উন্নত ছিল। আমাদের দেশের তুলনায় কানাডায় ছাত্রদের জন্য মাথাপিছু ব্যয় অনেক বেশি। ওখানে তো পড়াশোনার জন্য আলাদাভাবে অর্থ ব্যয় করতে হয় না। সরকারই সব ব্যবস্থা করে। ওদের শিক্ষকরাও অনেক বেশি দক্ষ। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অনেক আন্তরিক। আমাদের দেশে তো এমনটি দেখা যায় না খুব একটা।
কানাডা থেকে দেশে ফিরে কর্মজীবন শুরু করলেন কীভাবে?
দেশে আসার পরে আমি প্রথমে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন কাজ করেছি। এরপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ছিলাম ৩ বছর। তখন মন্ত্রিপরিষদ সচিব ছিলেন কেরামত আলী। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি এখন প্রয়াত। তারপর আমি পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে যুক্ত হই। এরপর কাজ করেছি পানি উন্নয়ন বোর্ডে। এরপরে বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স অ্যাডমিনিস্ট্রিতে ছিলাম ৩ বছর।
কর্মজীবনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। দীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার কথা যদি বলতেন?
একেক মন্ত্রণালয়ে একেক রকমের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। আমি যেখানেই কাজ করেছি, চেষ্টা করেছি তার একটা পরিবর্তন আনার। সবসময় আমার এই চেষ্টা অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স অ্যাডমিনিস্ট্রিতে আমরাই প্রথম নানান ধরনের পরিবর্তন আনি। এর আলাদা ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন, পাঠাগার স্থাপন এসব অনেক জোরালোভাবে করেছি। পানি উন্নয়ন বোর্ডেও তাই করেছি। কোন প্রকল্পের সঙ্গে কোন প্রকল্প ভালো হবে সেটি নির্ধারণ করে অনেক নতুন প্রকল্প আমরা বাস্তবায়ন করেছি।
ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাস কর্মরত ছিলেন। দূতাবাসে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?
ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে আমার কাজ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সহযোগিতা পাওয়ার জন্য স্থানীয় দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করা। দ্বিতীয় কাজ ছিল বিশ্বব্যাংকের জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তৈরি করা। বাংলাদেশের পক্ষে ঐ দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং সেটি বাংলাদেশ সরকারকে প্রতিনিয়ত জানানো। আমার আরেকটি বড় কাজ ছিল সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারকে যে খাদ্য সহায়তা দিত আমি তার স্ট্যান্ড তৈরি করতাম।
রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। বাংলাদেশের রাজস্ব বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন?
রাজস্ব বোর্ডের ভাবমূর্তি উদ্ধারের জন্য আমাদের নতুন উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের রাজস্ব বোর্ড নিয়ে মাঝে-মধ্যেই নানান অনিয়ম, অন্যায়ের অভিযোগ শোনা যায়। আমার একটা মতামত হচ্ছে আমরা যেসব পদে রাজস্ব বোর্ডে নিয়োগ দিই ঐ সব পদের একটা পরিবর্তন আনা দরকার। যেমন ইনকাম ট্যাক্স ক্যাডারে যারা আসবে সেটা আমরা বিসিএস পরীক্ষার মধ্যে নির্ধারণ করি। এখন কেউ যদি আরবিতে এমএ করে বিসিএস করে তারপর ইনক্যাম ট্যাক্স অফিসার হিসেবে যোগ দেয় তাহলে তাকে দিয়ে কী উপকার হবে আমার জানা নেই। সে তো আর ইকোনোমিক্স জানে না। সে বড়জোর বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞান পড়েছে। বিসিএস পরীক্ষাটাও বদলানো দরকার। এটাকে বিষয়ভিত্তিক করা উচিত। যে যে বিষয়ে ক্যারিয়ার গড়তে চায় সে সেই বিষয়ে সেই নির্দিষ্ট বিভাগেই তাকে পরীক্ষা দিতে হবে। তাছাড়া ইসলামিক স্টাডিজে বা আরবিতে পড়া কোনো শিক্ষার্থী যখন ইনকাম ট্যাক্সের অফিসার হয়ে যায় তখন বলাই বাহুল্য তাকে দিয়ে প্রতিষ্ঠান খুব একটা উপকৃত হয় না।
জীবনে বিভিন্ন ধরনের পেশায় যুক্ত ছিলেন। কোন পেশায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন?
আমি ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকতা পেশায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। এজন্য এই বয়সে এসেও শিক্ষকতা করছি।
১৯৭২-এর সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?
ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে পশ্চিমা দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা আর আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা এক নয়। আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে যে যার ধর্ম ইচ্ছেমত পালন করবে কেউ তাতে বাধা দেবে না। পশ্চিমা দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে কিন্তু তা নয়। সেখানে ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের কেউ কেউ ভাবেন আদৌ ধর্মের প্রয়োজন আছে কি না। সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে এক ধরনের নাস্তিকতার ব্যাপার আছে। আমাদের দেশে এই ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল পারস্পরিক ধর্মানুসারীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখা। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হল, সেই ধর্ম নিরপেক্ষতা বজায় থাকেনি। যখন ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই আমি মন্তব্য করেছিলাম, যদি এটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয় তাহলে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা ঠিক হবে না। তাতে ধর্মনিরপেক্ষতার চরিত্র নষ্ট হবে। তারপরও ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য হয়েছিল। এটাও তো ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আপনি কী মনে করেন?
না, এটাকে ঠিক সাংঘর্ষিক বলা যাবে না। কারণ ভারতও কিন্তু ওআইসির পর্যবেক্ষক সদস্য। সুতরাং আন্তর্জাতিক ফোরাম বিবেচনায় এটা ঠিক আছে। কিন্তু ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা, এটা কিন্তু পুরোপুরিভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল। সে সময় এটা কেন ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্য নয়— এ ব্যাপারে আমি ৫০ পৃষ্ঠার একটি নোট লিখেছিলাম।
৬৯, ৭১ ও ৯০-এর গণআন্দোলনের অভিজ্ঞতায় (২০১৩ সালের) শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলনকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?
নব্বইয়ের গণআন্দোলন আমি দেখিনি কারণ তখন দেশের বাইরে ছিলাম। তবে শাহবাগের তরুণদের যে আন্দোলন এটার বিষয় হিসেবে একটি মাত্র ইস্যুতে এ আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। তবে অন্য আন্দোলনগুলো ছিল দেশের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে। সে তুলনায় এ আন্দোলনের ক্ষেত্র অনেকটা সংকীর্ণ। আর অন্যসব আন্দোলনে দেশের সব শ্রেণি পেশার মানুষ অংশ নিয়েছিল। কিন্তু শাহবাগের গণজাগরণ ছিল প্রধানত তরুণদের কেন্দ্র করে। তবে বাংলাদেশের অন্য আন্দোলনের মতো এ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হল আবেগের বিচারে এই আন্দোলন অন্য আন্দোলনের তুলনায় কম ছিল না।
৪২ বছর পর ‘জয় বাংলা’ স্লোগানটি সাধারণ মানুষের মাঝে ফিরে এসেছে গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এটাকে কীভাবে দেখেন?
জয় বাংলা স্লোগান সবসময় এদেশের মানুষের ছিল। এটাকে কেউ কখনো কেড়ে নিতে পারেনি। বাংলাদেশের মানুষের বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন কেউ সহজেই ঘটাতে পারবে না। এটা আমি বিশ্বাস করি।
বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হেফাজতে ইসলামের উত্থান কীভাবে দেখছেন?
হেফাজতে ইসলাম কিন্তু এখানে কোনো নতুন প্রতিষ্ঠান নয়। কারণ এরা হল ঐ দেওবন্দি আন্দোলনের অংশ। দেওবন্দি আন্দোলন এখানে বিগত একশ’ বছর ধরে হচ্ছে এবং ওরা এ ধরনের কথা বলেই যাচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এসব কথা গ্রহণ করছে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সম্প্রতি তাদের বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে তারা সরাসরি রাজনীতিতে চলে এসেছে। আমি আসলে হেফাজতের চেয়ে বেশি চিন্তিত হিজবুত তাহরীরের মতো সংগঠনগুলো নিয়ে— এরা ধর্মান্ধতা ছড়াচ্ছে। কারণ হেফাজতিদের ধ্যানধারণা ঊনবিংশ শতাব্দীর। তাদের বক্তব্য একটা সীমাবদ্ধ জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে। কিন্তু যেভাবে হিজবুত তাওরীরের মতো গোষ্ঠী শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মান্ধতা ছড়াচ্ছে সেটা খুবই ক্ষতিকর। যে কোনো রাষ্ট্রের জন্য এটা হুমকিস্বরূপ। এখানে মুশকিল হল, আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর আদর্শিক দৈন্য। একসময় কমিউনিস্ট পার্টি ছিল আদর্শিকভাবে শক্তিশালী। এখন কমিউনিজমের সেই আধিক্য নেই। এখন দেশের সব রাজনৈতিক দল সুবিধাবাদী। ফলে মৌলবাদী শক্তি যদি আদর্শিকভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে এগোয় তাহলে এটা দেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তবে হেফাজতের কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের বড় কোনো ক্ষতি হবে না। তবে সম্প্রতি তাদের জনসমর্থন বেড়েছে। এ ক্ষেত্রে বলব, বাংলাদেশের মানুষ যখনই কোনো গোষ্ঠীকে উত্তেজিত হতে দেখেছে তখনই সেই গোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছে। তার মানে এই নয়, মানুষ তাদের আদর্শকে মেনে নিয়েছে। গ্রামের সহজ সরল গরিব মানুষ তাদের পুলিশের হাতে নির্যাতিত হওয়ার খবর শুনে এক ধরনের সহানুভূতি জানিয়েছে মাত্র। এই হেফাজতিদের প্রতি যদি কোনো রকম অন্যায় অত্যাচার করা না হয় তাহলে এরা একটা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।
তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন পাঁচ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে হেফাজতের প্রভাব পড়েছে?
এখানে শুধু হেফাজতের প্রভাবই পড়েনি, জাতীয় রাজনীতির সামগ্রিক প্রভাব পড়েছে। যেমন পদ্মা সেতুর ব্যাপার। এই পদ্মা সেতুর দুর্নীতির বিষয়ে গত দেড় বছর ধরে নানান প্রচারণা মানুষের মধ্যে ছড়িয়েছে। সরকার এটার একটা সহজ সমাধান করতে পারলে জনগণের মনে দাগ কাটত না। কিন্তু দেড় বছর ধরে এটি বিতর্কিত বিষয় হিসেবে চলে আসায় জনগণের মনে বিষয়টি দাগ কেটেছে। আবার সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনী হত্যাকাণ্ড নিয়ে সাংবাদিকরা নানান আন্দোলন করে এসেছে। সরকার দুই এক মাসের মধ্যেই এর একটা সমাধান করলে এই বিষয়টা জনগণের মনে এভাবে দাগ কাটত না। এ রকম অজস্র বিষয় আছে। আমি শুধু হেফাজতকে দায়ী করব না। আমি বলব, গণমাধ্যমেরও কিছুটা দায় আছে। কারণ সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের একটা ভূমিকা আছে। এই সংবাদ প্রচারের মধ্যেই অনেক বিষয়ে মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে। আরেকটি বিষয় আমাদের মনে রাখা উচিত, মনোস্তত্ত্ববিদরা বলে থাকেন আপনি যে বিষয়ে লাভবান হবেন তাতে আপনার আগ্রহ বেশি থাকবে; আর যে বিষয়ে লোকসানের শিকার হবেন তাতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন। কিন্তু সরকারের কিছু কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর ক্ষতিগ্রস্তরা সব সময় অনেক বেশি সক্রিয় হয়। আর লাভবান মানুষ মনে করে আমার তো লাভ হয়েছে, কোনো সমস্যা নেই। সুতরাং সরকার যে উন্নয়নের কথা বলছে সেটা নির্বাচনে বড় কোনো বিষয় না। কিন্তু সরকারের কারণে যদি কোনো জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সেটা হবে বড় ক্ষতির কারণ। যেমন গ্রামীণ ব্যাংকের আশি লাখ মানুষের মধ্যে পঞ্চাশ লাখ মানুষও যদি মনে করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাহলে এটা সরকারের জন্য ক্ষতিকর।
ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ক্ষুদ্র ঋণ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?
আমার কথা হচ্ছে পৃথিবীতে এমন কোনো ফর্মুলা নেই যে ফর্মুলায় সব ধরনের সমাধান সম্ভব। তবে এতে অনেক দরিদ্র মানুষ উপকৃত হয়েছে। আশি লাখ দরিদ্র মানুষ এখান থেকে ঋণ নিয়ে উপকৃত হয়েছে। এটা তাদের প্রতিষ্ঠান, তাদের হাতে ছেড়ে দিক। তারা তাদের প্রতিষ্ঠান তাদের মতো পরিচালনা করুক।
আপনি ব্যক্তি জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতা চর্চা করেন। এই দর্শনের উৎস সম্বন্ধে বলবেন?
ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করি এটা বলা ঠিক হবে কি না জানি না। কিন্তু আমি ধর্মনিরপেক্ষতাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা না থাকলে গণতন্ত্র টিকবে না। সুতরাং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষতা থাকতে হবে। আর ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিতে যদি আপনি দেখে থাকেন তাহলে আরও অনেক বিষয়ে অনেক গভীর বিশ্লেষণ সম্ভব। আমি একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে এসব বিষয়ে অনেক বিশ্লেষণ করতে পারি।
ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা কীভাবে বাড়ানো যায়?
ধর্ম নিরপেক্ষতার চর্চা বাড়ানোর জন্য গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে হবে। গণতন্ত্রকে সুসংহত মানে হল একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। আমরা যদি একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই এবং যারা আমাদের সঙ্গে একমত হয় না তাদের প্রতিও যদি শ্রদ্ধা থাকে তাহলে পরে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসারিত হয়। আর যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিপন্ন হয় তখন কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা টিকিয়ে রাখা যায় না। ধর্ম নিরপেক্ষতা চাইলে গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে হবে।
মিথ্যাচারের রাজনীতির ভবিষ্যৎ কী?
এখন সেই আশঙ্কা একটা বেশি নেই। কারণ বাংলাদেশের মানুষ অনেক সজাগ হয়েছে। যেমন গাজীপুর নির্বাচনের সময় শুনলাম সেখানে টাকার খেলা অনেক হয়েছে। কিন্তু ভোট দেওয়ার সময় তো মানুষ পছন্দমতো ভোট দিয়েছে, টাকার জন্য ভোট দেয়নি। এখন মানুষ অনেক সচেতন হয়েছে, গণমাধ্যমের ফলে অনেক তথ্য তারা জানতে পারছে, মানুষের চোখ খুলে গেছে। আপনি চিন্তা করে দেখেন ঘরে ঘরে টেলিভিশন আছে রেডিও আছে এবং খবরের কাগজের বিক্রি অনেক বেড়ে গেছে। এসব নিয়ে মানুষ অনেক সজাগ।
সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারে উপদেষ্টা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। এর পেছনে কী যুক্তি ছিল?
পদত্যাগ করাটা অবশ্যই যৌক্তিক ছিল। আমাদের সংবিধানেই তো পদত্যাগের কথা আছে। প্রথম কথা হল, আপনি আপনার কাজ ঠিকমতো করতে পারছেন না। তখন আপনি অবশ্যই পদত্যাগ করতে পারবেন। সেটাতে সংবিধানে আপনাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে এটা কেউ করে না। এটা নিয়ে প্রশ্ন করার আমি তো কোনো কারণ দেখছি না। কারণ আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকারে গিয়েছিলাম অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার জন্য। ইয়াজউদ্দিন সরকার অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করবে না। সুতরাং সেই সরকারে থাকাটা আমার যে শপথ সেটা ভাঙার সামিল। কারণ আমি শপথ নিয়েছি সংবিধান অনুসারে কাজ করব। দেখতে পেলাম এখানে সংবিধান অনুসারে কাজ হচ্ছে না। সুতরাং সেখানে যদি পদত্যাগ না করতাম তাহলে আমি বরং সংবিধান বিরুদ্ধে কাজ করতাম।
আপনি কী বলতে চাচ্ছেন ২০০৮-এর সংসদ নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়নি?
ইয়াজউদ্দিন সাহেব যেটা করতে চেয়েছিলেন সেটা নিরপেক্ষ হত না। আমাদের পদত্যাগের মূল সাফল্য হল আমরা ইয়াজউদ্দিন সাহেবকে সেটা করতে দিইনি। আর পরবর্তীকালে যে নির্বাচন হয়েছে সেটা করেছেন ইয়াজউদ্দিন করেননি সেটা ফখরুদ্দীন সাহেবরা করেছেন। আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকারে ছিলাম তার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন ইয়াজউদ্দিন আহাম্মদ আর যে সরকার নির্বাচন করেছে তার প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন। নির্বাহী ক্ষমতা প্রধান উপদেষ্টার হাতে ছিল।
জীবনে কখনো প্রেম এসেছিল?
দেখুন আমি আবেগে বিশ্বাস করি না। আর প্রেমটা হল অধিকতর হৃদয়ের বা মনের ব্যাপার মগজের চেয়ে আমি মূলত মগজ পরিচালিত মানুষ। সুতরাং সবকিছু প্রশ্ন করি সবকিছু নিয়ে পড়াশোনা করি, কোথাও আমি বন্দি হয়ে থাকতে রাজি নই। আমি কোনো ধারণায় বন্দি হয়ে থাকার পক্ষে নই।
বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনি কেমন আশাবাদী?
বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি আশাবাদী। কারণ হল, আমাদের জনশক্তির একটা বড় শ্রেণি হল কম বয়সী, মানে যুবক শিশু-কিশোর। কম বয়সী মানুষ বাংলাদেশের সম্পদ। আর পৃথিবীর যতগুলো উন্নত দেশ আছে তার অধিকাংশ মানুষই হল বয়স্ক মানুষ। এই বয়স্ক মানুষ দিয়ে তাদের পক্ষে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয়, কাজেই আমাদের একটি বিরাট জনশক্তি আছে যাদের উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব। সেহেতু দেশের বাইরে বা ভেতরে তাদের সুশিক্ষিত করে কাজে লাগানো যায় তাহলে দেশ একটি বড় ধরনের অর্থনৈতিক পরিবর্তন হবে। আরেকটি হল, ৮৬ লক্ষ প্রবাসী আছে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে এটাও বড় কারণ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিশ্বায়নকে আমরা আত্মস্থ করতে পারবো ততই আমাদের জন্য মঙ্গল। আমাদের জনসম্পদকে ব্যবহার করে অনেকদূর যেতে হবে।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন আপনি। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান ভাবমূর্তি হারাচ্ছে…।
তা ঠিক। রাজস্ব বোর্ডের ভাবমূর্তি উদ্ধারের জন্য আমাদের নতুন উদ্যোগ নিতে হবে। রাজস্ব বোর্ড নিয়ে মাঝে-মধ্যেই নানান অনিয়ম, অন্যায়ের অভিযোগ শোনা যায়। আমরা রাজস্ব বোর্ডে যে পদ্ধতিতে এখন কর্মকর্তা নিয়োগ দিই সেই পদ্ধতিটার একটা পরিবর্তন আনা দরকার। যেমন ইনকাম ট্যাক্স ক্যাডারে কারা আসবে সেটা আমরা বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করি। এখন বিসিএস পরীক্ষার যে নিয়ম তাতে কেউ যদি আরবিতে এমএ করে বিসিএস পরীক্ষায় ভালো করেন তাহলে তিনি ইনকাম ট্যাক্স অফিসার হিসেবে যোগ দিতে পারেন। কারণ বিসিএস পরীক্ষায় ইংরেজি, বাংলা ভাষা, সাধারণ জ্ঞান— এই সমস্ত বিষয়ের উপর পরীক্ষা হবে। এগুলোতে ভালো করলে আরবিতে এমএ পাস করেও ইনকাম ট্যাক্স ক্যাডারে আসতে পারেন। এখন এভাবে কেউ নিয়োগ পাওয়ার পর ইনকাম ট্যাক্সে কতটুকু সফল হবেন? তাকে দিয়ে কী উপকার হবে আমার জানা নেই। আপনার তো অ্যাকাউন্টেন্সি জানতে হবে, আপনার তো ট্যাক্সেশন ল জানতে হবে। এখন এগুলো আমরা একাডেমিতে পড়ানোর চেষ্টা করছি, এটাতে কতটুকু লাভ হয় এটা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই। একবার কেউ কোনো রকমে পাস করে ফেললে তার যদি আগ্রহ না থাকে তাহলে সে কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। সুতরাং আমি মনে করি, এই ধরনের ক্যাডারগুলোতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংস্কার আনার দরকার।
বিসিএস নিয়ে প্রায়ই আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। বিসিএস-এর পরীক্ষা ও নিয়োগ পদ্ধতি কতটা সঠিক?
বিসিএস পরীক্ষা এখন যেভাবে হচ্ছে আমি এই প্রক্রিয়ার বিরোধী। আমি মনে করি, প্রত্যেক ক্যাডারের জন্য আলাদা আলাদা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। যিনি ইনকাম ট্যাক্স ক্যাডারে আসবেন তিনি আরবি বা বাংলা যে বিষয়েই পাস করে আসুন তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই— তাকে পরীক্ষা দিতে হবে অ্যাকাউনটেন্টে, তাকে পরীক্ষা দিতে হবে ইনকাম ট্যাক্স ল’তে। এগুলোতে তিনি যদি ভালো করতে পারেন তাহলে তিনি ইনকাম ট্যাক্সে আসতে পারেন। আর যদি এসব বিষয় তিনি ভালোভাবে না জেনে থাকেন তাহলে চাকরিতে নিয়োগ দেওয়ার পর আর তো কাউকে চাকরি থেকে বের করে দেওয়া যায় না। কোনোমতে হাতে-পায়ে ধরে পাস করে যায় কিন্তু কাজগুলো আর শেখা হয় না। কাজগুলো ভালো করে না শিখলে তাকে দিয়ে প্রতিষ্ঠানের খুব একটা যে উপকৃত হবে একথা বলা যায় না। সুতরাং আমি মনে করি ইনকাম ট্যাক্স বা কাস্টমস ক্যাডারে হোক অথবা যে কোনো ক্যাডারে নিয়োগের ক্ষেত্রে যে বিসিএস পরীক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্তন জরুরি। কারণ বর্তমান পদ্ধতিতে আমরা তাদের নিয়ে তিন চার মাস পড়িয়ে যে বিশেষজ্ঞ করতে পারব তার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং আমরা যে বর্তমানে নির্বাচন করছি বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে এটা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। পৃথিবীর কোনো দেশে এইভাবে কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয় না। ইসলামিক স্টাডিজে এমএ বা ইতিহাসে এমএ করে কারও ট্যালেন্ট শিট দেখলে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। ইনকাম ট্যাক্সে ল জানা নেই অথচ অফিসার হয়ে বসে আছেন। এটা তো দেশের জন্য ক্ষতিকর। এটা তো চলতে পারে না। এমন লোককে নির্বাচন করা উচিত, যার কাজে আগ্রহ আছে। আর যেভাবে বিসিএস-এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় তাতে নিশ্চিত করা যায় না— তার সেই কাজে আগ্রহ আছে কি নেই।
তাহলে নিয়োগ পদ্ধতিটা কেমন হওয়া উচিত?
কেউ এমবিবিএস পাস করে প্রশাসনে কাজ করলেও আমার কোনো আপত্তি নেই। শুধু তাকে ম্যান ল বা সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় পাস করে আসতে হবে, সে যদি ডাক্তারিও ভালো জানে সে যদি ম্যান ল ভালো জানে আসুক। সে ম্যান ল ভালো জানে বলেই আসছে। আমি তাকে ডাক্তার হিসেবে সেখানে বিবেচনা করব না। তাকে বিবেচনা করব বিসিএস এক্সামের জন্য যে বিষয়গুলো দরকার সেগুলো জানে কি না। সেই বিষয়গুলোতে সে যদি ভালো করতে পারে তাহলে আমি প্রশাসনে ডাক্তার নিতেও রাজি আছি, আরবি পাস করা নিতেও রাজি আছি কিন্তু আমরা তো সেটা করি না। আমরা যেটা করি সেটাতে দেখি সে বাংলা, ইংরেজি লিখতে পারে কি না, সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা আছে কি না। এতে করে সবচেয়ে বেশি যে ক্ষতিটা হচ্ছে তা হল আমরা একই পদ্ধতি অনুসরণ করছি ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তারদের ব্যাপারে। একজন ইঞ্জিনিয়ার বাংলা রচনা লিখতে পারে কি না পারে, তাতে তো আমার মাথাব্যথার কথা না। সে কনস্ট্রাকশন করতে পারে কি না সেটা আমার দেখতে হবে। দেখতে হবে সে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় জানে কি না। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের গুরুত্ব হল কুড়ি শতাংশ আর আশি শতাংশ হল বাংলা-ইংরেজি আর সাধারণ জ্ঞান। এই পদ্ধতিই হল একটা ভ্রান্ত পদ্ধতি। সে জন্য কোনো বিশেষায়িতের দিকে আমাদের ঝোঁক নেই। এই যে আমাদের দেশের বিসিএস পরীক্ষার পদ্ধতি, এটা বিশ্বের কোথাও বিংশ শতাব্দীতে তো নয়ই বরং ঊনবিংশ শতাব্দীতে ছিল। আমাদের দেশে এখনো বিদ্যমান আছে, আমরা বিংশ শতাব্দীতে এসে এই পদ্ধতিতে সংস্কারে আদৌ হাত দিইনি।
বিদ্যমান সংকট থেকে কীভাবে উত্তরণের পথ কী?
এজন্য পরীক্ষা পদ্ধতিতে যেটা করতে হবে প্রত্যেক ক্যাডারের জন্য আলাদা আলাদা পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন আপনি ডাক্তার হতে চাইলে ডাক্তারি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। তার মধ্যে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ নম্বর বাংলা ইংরেজি আর সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক থাকতে পারে। বাকি পঞ্চাশ শতাংশ নম্বর ঐ বিষয় সংক্রান্ত পরীক্ষা হওয়ার দরকার। এটা হলে দুটো লাভ হবে। এক. তাকে নিয়ে আমাদের পড়ানোর চেষ্টা করতে হবে না। সে নিজেই তার জ্ঞান সংগ্রহ করে আসবে। দুই. আমাকে রিস্ক নিতে হবে না, আমি খুব ভালো একটা বাংলার ছাত্রকে নির্বাচন করতে পারি যে খুব ভালো বাংলা লেখে। একটা ক্যাডারের জন্য কিন্তু দেখা গেছে, তার ওই ক্যাডারের মধ্যে কোনো আগ্রহ নেই, কোনো কিছু শিখল না। তাকে নিয়ে আমাদের সারা জীবন কাটাতে হবে। সুতরাং আমাদের যে পরীক্ষাপদ্ধতি এটা একেবারেই অযোগ্য। বাকি দুনিয়ার লোক এই পদ্ধতির কথা শুনলে হাসবে। অন্যান্য দেশে অনেক পেশাদারিত্ব করা হয়েছে, আমাদের এখানে মোটেও পেশাদারিত্ব করা হয়নি।
আরও অসুবিধার বিষয়— সাধারণ জ্ঞান, গণিত, বিজ্ঞান এগুলোর লেভেল হল এসএসসির লেভেলে। এসএসসির লেভেল যদি না হয় তাহলে আরবিতে এমএ পাস করে কেউ তো বিজ্ঞানে পাস করতে পারবে না। আর যারা বিজ্ঞানের ছাত্র এমএসসির তারাও অনেক বেশি নম্বর পেয়ে যাবে। কাজেই এগুলো খুব নিম্নমানের পরীক্ষা হয়। আপনার ব্যাচেলার লেভেল বা মাস্টার্স লেভেলের পরীক্ষা হয় না। এর ফলে পেশাভিত্তিক জ্ঞানের কোনো পরীক্ষা হচ্ছে না। বিসিএস-এর বিদ্যমান ব্যবস্থায় আমরা স্বল্প মেধার কতগুলো লোক নির্বাচন করি, তাদের জ্ঞানের গভীরতা আছে কি না, সেগুলো পরীক্ষা করছি না। একটা লোক যদি চটপটে হয়, ভালো বাংলা-ইংরেজি লিখতে পারে, বলতে পারে তাহলেই সে বিসিএস-এ পাস করে যাবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে করা হয়েছিল দুটো কারণে তখন তো এত বিষয় ছিল না। সুতরাং এই সব বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব ছিল না। এখন তো অসংখ্য বিষয় হয়ে গেছে। এমবিএ পড়তে গেলেই দেখেন সেখানেই কতগুলো বিষয় হয়েছে, কেউ মার্কেটিং স্পেশালাইজড করে, কেউ হিউম্যান রিসোর্স স্পেশালাইজড করে, এরকম অজস্র বিষয় হয়ে গেছে। আর একটা বিষয় হল, ঐ সময় খুব অল্প সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগ করতেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এত ভালো ছাত্র থাকত যে তারা গিয়ে অনায়াসে এই সব আইনকানুন পড়ে পাস করতে পারত। এখন তো আমরা আর সেই পর্যায়ের ছাত্র খুঁজে পাচ্ছি না, যে একদম সেরা ছাত্র। সুতরাং আমি ধরে নিতে পারতাম যে সে যে বিষয় থেকেই আসুক না কেন, আইনের ক্যাডারে হলে সে আইনে পাস করবে। এখনকার বেশিরভাগ ছাত্রই তো মধ্যমানের মেধাবী সুতরাং সেখানে গিয়ে দেখা যাবে যে তার হয়ত আর ভালো লাগছে না। যে হয়ত সারা জীবনে বাংলা কবিতা পড়েছে সে ভাববে এই মুহূর্তে কীভাবে আমি ইনকাম ট্যাক্সের আইন পড়ব। সুতরাং আমাদের বিসিএস নির্বাচনের পুরো সিস্টেমটাই ভুল। এগুলো সব পরিবর্তন করতে হবে।
বিসিএস নির্বাচনের এই ভুল শোধরানোর ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কী?
বিসিএস পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমাতে হবে। এত সংখ্যক পরীক্ষার্থী নিয়ে তো তাদের মধ্য থেকে সঠিকভাবে যাচাই করা সম্ভব নয়। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমানোর উপায় হল, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত মান বাড়িয়ে দিতে হবে। পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে কারা পাস করবে। যদি দেখা যায়, সব পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিপ্রাপ্ত না হলে পাস করতে পারে না তাহলে তৃতীয় শ্রেণিদের বিসিএস পরীক্ষায় সুযোগ দেওয়ার তো কোনো মানে হয় না। এরা হয়ত এক শতাংশ বা দুই শতাংশ পাস করবে। এই দুই শতাংশের জন্য আপনি সবারই পরীক্ষা দিতে দেবেন এতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে যাবে। কাজেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত মান বাড়িয়ে দিলেই যেখানে দুই লাখ পরীক্ষার্থী সেখানে পঞ্চাশ হাজারে নিয়ে আসা যাবে। সেই পঞ্চাশ হাজারের পরীক্ষা নিয়ে আপনি বার হাজারে নিয়ে আসতে পারবেন। আমাদের যে নিয়োগ প্রক্রিয়া এটা একেবারেই বাজে, পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে এই রকম নিয়ম নেই। আর একটি বিষয় হল, চাকরিতে গিয়ে সে কী করছে না করছে এগুলি মূল্যায়নের কোনো ব্যবস্থা নেই। ভালো কাজ করলেও কারও কপালে কোনো পুরস্কার জোটে না, খারাপ কাজ করলেও তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় না। সুতরাং এই অবস্থাতে যারা কাজ জানে তারাও কোনো কাজ করে না। এর ফলে প্রশাসনের নিয়োগ এবং প্রশাসনের মূল্যায়ন এগুলো যদি পরিবর্তন না করেন তাহলে পেশাদারিত্ব সৃষ্টি হবে না। আর কর্মকর্তা নিয়োগের পর যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এগুলো পুঁথিগত প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ একাডেমিতে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেখানে কী সুবিধা-অসুবিধা আছে? সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা থাকতে হবে। সেই গবেষণার ভিত্তিতে তাদের বলতে হবে যে তোমাদের এভাবে কাজটা করা উচিত। যারা প্রশিক্ষক তারা যে বইগুলো পড়ে প্রশিক্ষণ দেন সে বইগুলো হয়ত পঞ্চাশ বছর বা তারও আগের লেখা।
সাম্প্রতিক নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি আমাদের জন্য খুবই লজ্জাজনক। এটা অবশ্যই বন্ধ করা উচিত, সেটা করতে হলে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে। যারা একবার দুর্নীতি করেছে তারা যতক্ষণ পর্যন্ত ওখানে থাকবে ততক্ষণ সেটা করতেই থাকবে। তাই আমাদের টোটাল সিস্টেমটাই পরিবর্তনের দরকার।