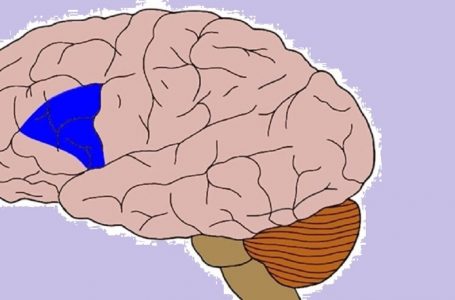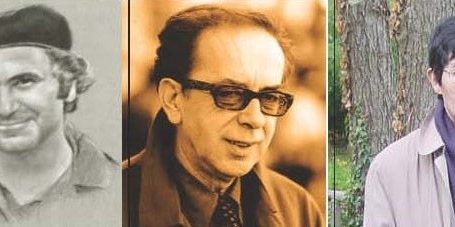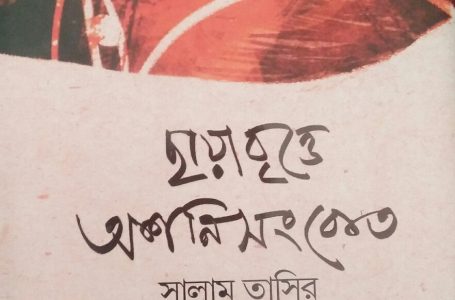ছেলের চাকরি-বাকরি হচ্ছে না। নিজামউদ্দিন সাহেব তার ছেলেকে কিছু একটা করে যাওয়া বা অভ্যস্ত হওয়াতে অবশেষে বাড়ি ভাড়াটা তোলার দায়িত্ব দিলেন। তিনি নিজেই এটাকে এতদিন একরকম অপকর্ম বলে আখ্যা দিয়েছেন। দুচারজন ভুল মানুষের পরামর্শে তার সমস্ত জীবনের পুঁজির বিনিময়ে বাড়ি নামক যেন এক নরকখানা তিনি গড়েছেন। ভাড়াটিয়ার থেকে হাত পেতে ভাড়া নিতে এখন তার নিজেরই রুচিতে বাধে। ন্যায্য টাকা তুলতে এত বাহাস! পারলে কপাল চাপড়ান নিজামউদ্দিন সাহেব।
নিজামউদ্দিন চাকরি করতেন একটি বীমা কোম্পানিতে। কোম্পানির একটি শাখা প্রধান হিসাবে তিনি রিটায়ার করেছেন। এক সময় কষ্টেসৃষ্টে ঢাকার এই উপশহর গোড়ানে দশ কাঠা জমি কিনে একরকম ফেলেই রেখেছিলেন। হিসেবে ধরেননি। কিন্তু বিধিবাম, চাকরিতেও যেমন তিনি কোনো হায়ার পোস্ট বাগাতে পারেননি, তেমনি পারেননি বিষয়-সম্পত্তিও গড়তে। শুধু স্ত্রীর প্রাণান্ত বায়না আর শ্বশুরকুলের সহযোগিতায় এই জমিটুকু কিনেই তিনি অসাধ্য সাধন করেছিলেন। না হলে এটুকুর তো জো ছিল না।
অবসরে যাওয়ার পর পেনশনের এককালীন যে টাকাটা তিনি পেয়েছিলেন, আনাড়ি অভিজ্ঞতা নিয়ে তা আর কোথাও খাটাতে ভরসা পেলেন না। অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে পড়ে থাকা নিচু জমিটুকু ভরাট করে দশ বাই দশ ফুটের বিশটি রুম করলেন। বিশটি পরিবারের জন্যে ছয়টি চুলোর ব্যবস্থা রাখলেন। আর বেশ কতখানি জায়গা শান করে ওয়াসার লাইনের সঙ্গে ফিট করলেন চাপকল। আর তাতেই হু-হু করে নতুন বাড়িটি ভরে গেল নানান রকম ভাড়াটিয়ায়। কালো চকচকে টিনের উপর হলুদ রং দিয়ে লিখে গেটটির ঠিক পাশে, দেয়ালে সেঁটে দিলেন ‘আমিনা ভিলা’। সব লোকসান উসুলের মতো এই নামই গলিটিকে পরিচিত করে তুলল। মানে গলিটি হয়ে গেল ‘আমিনা ভিলা’র গলি। তার স্ত্রী’র নামটি নিজস্ব একটি পরিচয় পেল। যদিও অদূরেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে একতলা, দোতলাসহ ক’টি বহুতল ভবনও। আর লাভ-লোকসানের ঊর্ধ্বে যে হিসাবটি প্রকট হয়ে উঠল তা হলো নিজামউদ্দিনের আয়ুর তীব্র ঘাটতি। তিনি ভালো খেয়ে, বিশ্রাম নিয়ে, এমনকি পরিবারের সবারসহ নিজের মনোবলটি আরও জাগ্রত করেও যেন শরীরটিকে সাবেক অবস্থায় নিতে পারছেন না। এক বছরেরও বেশি সময় গেছে তার বাড়িটির পেছনে। ঝড়-বৃষ্টি-রোদ সব তিনি নেশায় পড়ে বেপরোয়াভাবে কাটিয়েছেন।
দু’টো ছেলে নিজামউদ্দিনের। বড়টি এমএ পাস করে চাকরি খুঁজতে খুঁজতে সরকারি চাকরির বয়স হারিয়ে ফেলেছে। আর ছোটটি বাতাস বুঝে, ভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারা সত্ত্বেও এক অসৎ উপায়ে বিত্তবান, অতিশয় কুঁচুটে বাবার একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করে। কন্যাসহ বাবাকে জব্দ করতে বিনা নোটিসে সে বাড়ি ছাড়া হয়ে গেল। যা নিজাম উদ্দিন বা তার স্ত্রী আমিনা বেগমের দু’জনের কারও পরিবারের কুষ্ঠিতে নেই। নিজের আদর্শের সঙ্গে সন্তানের এই অমিলও নিজামউদ্দিন মানতে পারছিলেন না। তার ভেঙে পড়ার সেটিও একটি কারণ।
বিশটি রুম থেকে বিশ হাজার টাকা উঠে আসার কথা থাকলেও যেমন ওঠে না। তেমনি গ্যাস পানি-বিদ্যুৎ-ইনকাম ট্যাক্স, মিউনিসিপ্যালিটির বিল, তারপরও এর সব বিভাগের ওত পেতে থাকা দালালদের যা নয় তার চেয়ে বড় মাপের হুমকি, নিজামউদ্দিন ভালো করেই বুঝলেন এ বাড়ি নয় নিজের জন্যে তিনি এ নির্মাণ করেছেন এক গ্যাঁড়াকল।
ঠিক বাড়িওয়ালা সেজে নয়, নিজামউদ্দিনের ত্রিশ অতিক্রান্ত পুত্র ফিরোজ নিজাম বাড়িভাড়া সংগ্রহ করতে যেত বিনীত প্রার্থী হয়ে। কিন্তু এমনটি হলে কী হবে। মাসের পাঁচ, দশ, পঁচিশ তারিখ পার হয়ে গেলেও ছিঁড়ে-কুটে একমাসের ভাড়া তারও পরের মাসের পরের মাসে উঠে আসে না। সব কেমন নটখট বেঁধে যায়। হিসাবের জের টানতে টানতে খাতার পৃষ্ঠার সংখ্যা বাড়ে। তার ওপর প্রায় প্রতিমাসে আছে কোনো না কোনো রুমের ভাড়াটিয়ার পলায়ন। অথচ হাতে পায়ে ধরে যে সময় সে নিয়েছিল তাতে করে হয়তো আগামীকাল, পরশুই তার ভাড়া পরিশোধের কথা ছিল।
এমন ন্যক্কারজনক, খাবি-খাওয়া অবস্থায় পড়া ফিরোজকে তার ভাড়াটিয়ারা ধন্য হতে পরামর্শ বাতলায়। ‘এই বাড়িরতন একজন দ্যাপইট্যা ভাড়াটিয়া দেইহা তারে ম্যানেজার বানাইয়া দ্যান বাইজান। এগুলান আপনের কাম না। দেহেন আশেপাশের বাড়ি? কেমতে মাসের পাঁচ তারিখে সব ভাড়া উঠ্যা যায়? আর দশ তারিখের মধ্যেই তো সব কিলিয়ার।’ দশ তারিখের মধ্যেই আশপাশের বাড়ির ভাড়াটিয়াদের ভাড়া ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার বৃত্তান্তটি শুনে গা ঘিনঘিন করে ওঠে ফিরোজের, শুধু বাবার নির্বুদ্ধিতার জন্যে। বাবার এই উপায়ে অর্থ বিনিয়োগ মানে বংশপরম্পরায় চরিত্র হননের বীজ রোপণ করা আর কী।
আশপাশে যারা এ ধরনের বাড়ি করেছে তাদের প্রায় সবারই পৈতৃক জমি এবং তাদের একমাত্র পেশাই হচ্ছে বাড়িভাড়া তুলে খাওয়া, যাদের কোনো রুচি নেই, শিক্ষা নেই, নেই কোনো আদর্শের বালাই। পাওনা টাকাটা উসুল করতে পারাটাই তাদের জীবনের লক্ষ্য। আর কোনো অবস্থা বিবেচনার ধার তারা ধারে না।
মাসের পাঁচ তারিখ বাড়িভাড়া তোলার তাদের নির্ধারিত দিন। তার পাঁচদিন পর দশ তারিখটি হচ্ছে চূড়ান্ত দিন। এদিন বাড়ির মালিক ব্যক্তিটি অশ্রাব্য গালাগাল বর্ষণ করে ভাড়াটিয়াদের উদ্দেশে। ভাড়াটিয়ারা জানে আজ বাড়িওয়ালা মদ খেয়ে আসবে। টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে না পারলে মান নিয়ে টানাটানি। এমনকি জানটি নিয়েও। বাড়িওয়ালাকে তারা আজরাইলের মতো ভয় পায়। ভাড়া জোটাতে না পারলে পালিয়ে বেঁচে থাকে। যখন জোগাড় হয় বহুদিন রোগ ভোগের পর বেঁচে যাওয়া ক্লিষ্ট রোগীর মতো এসে ধরা দেয়। জীবনের মূল্য হিসেবে বাড়িওয়ালা নামক আজরাইলের হাতে গুঁজে দেয় বহু কষ্টে জোগাড় করা জীর্ণ টাকার সরু বান্ডিলটি। অবশ্য এর জন্যই বাড়িওয়ালাকেও হতে হয় সাক্ষাৎ আজরাইল। তা যে না পারবে বাড়িওয়ালা হিসাবে সে ব্যর্থ।
অতিষ্ঠ ফিরোজ নিজাম বিশঘর ভাড়াটিয়ার মধ্য থেকে শক্তপোক্ত, রাগী চরিত্রের রহমত উল্লাহকে ‘আমিনা ভিলা’র ভাড়া তোলার দায়িত্ব দিতে বাধ্য হলো। ঠিকঠাকভাবে সে কাজটি করতে পারলে তার অর্থাৎ রহমত উল্লাহর রুমের ভাড়া হয়ে যাবে পাঁচ’শ টাকা। অর্ধেক মাফ। এই পাঁচ’শ টাকা মাফ অমাফের জন্যে রহমত উল্লাহর তেমন কিছুই আসে-যায় না। কারণ পেশায় সে কসাই। বিরাট বিরাট গরু এনে একাই তড়াক করে ফেলে দেয়। দু’জন কর্মচারী আছে; তবু খাটুনির অন্ত নেই। কারণ মাপে ঘোরপ্যাঁচ, ভেজালের কসরত তারা ঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে উঠতে পারে না।
রহমত উল্লাহর মতে অমন আন্তরিক হাসিটি দিয়ে ক্রেতাকে ধন্ধ লাগিয়ে কাছে টানার ক্ষমতাইবা ওদের কই! রহমত উল্লাহ সরে গেলে দোকান চলে? ওদের কোনো চালেই ক্রেতা ভেড়ে না যদি না পূর্ণিমার চাঁদের মতো ডগডগে ভুঁড়িটি উচিয়ে রহমত উল্লাহ ঠায় দাঁড়িয়ে না থাকে। তাই তো রহমত উল্লাহ ওদের ‘ওয়াই ফকিন্নির পুত’ ছাড়া ডাকতেই পারে না, একরুমে দুই-দুইটা বউ রহমত উল্লাহর। একজন যুবতী একজন কিশোরী। প্রতিদিন বেলা বারোটার দিকে রহমত উল্লাহ কর্মচারী মারফত যে বাজার পাঠায় তাদের তিনজনের জন্যে, তা দেখে বাড়ির মানুষের চোখ চড়ক গাছে ওঠে। রহমত উল্লাহর ঘরের দরজার ছায়াটিতেও ‘আমিনা ভিলা’র অন্য কেউ তাকাতে গেলে তার দৃষ্টিতে সম্ভ্রম না ঝরে পারে না। পঁয়ত্রিশের রহমত উল্লাহর গাট্টা-গোট্টা শরীর ছুঁইয়ে তেল উপচে পড়ে। যেন সে রৌদ্রে দাঁড়ালে সূর্য চিকচিক করে ওঠে। দুই বউয়ের কারও এখনো ছেলেপুলে হয়নি তাতেই সবাই ধরে নিয়েছে রহমত উল্লাহ-ই বাঁজা।
একদঙ্গল শীর্ণকায়া মানুষের বসতস্থল ‘আমিনা ভিলা’ নামক ওই গুচ্ছ বস্তিটিতে রহমত উল্লাহর ভয় পাওয়ারই মতো একজন। একটিমাত্র গোসলখানা। তার মাঝখানে টিউবয়েল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভোররাত থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত ঠেলা-ধাক্কা করে গোসল করতে থাকে। রহমত উল্লাহর সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র সবাই ভাই ভাই করে নিজের জায়গাটুকু ছেড়ে দিয়ে খাতির করে। রহমত উল্লাহর একা কখনো গোসলখানায় যায় না। বেশির ভাগ সময় ছোট বউ-ই তাকে ডলে-ঘষে গোসল করিয়ে দেয়। আর বড় বউ আসে মাঝে মাঝে। তবে তাকে এ কাজে আগ্রহের সঙ্গে আনা হয় বলে মনে হয় না। কাজ না থাকলে হয়তো সে নিজেই সেধে আসে। রহমত উল্লাহর বউ দু’টিকে যেমন পর্দানশীন থাকতে দেখা যায়, তেমনি চুপচাপ। এ সৎকর্ম যে তাদের স্বামীর ভয়েই সাধিত হতে থাকে তা আর কাউকে বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। একটু অন্যথা হলে দু’টোকেই প্যাঁদাতে প্যাঁদাতে সে গেটের বাইরে নিয়ে যায়। কারণ আমিনা ভিলায় উঠোন বলতে কিছুই নেই। তিনজনের ধস্তাধস্তির পর্যাপ্ত জায়গাটি তো চাই। মাথায় রক্ত চড়তে সময় লাগে না রহমত উল্লাহর। বাড়ির কুঁচোকাঁচাগুলো ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে তাকে দেখে। পাঁচ’শ টাকা কমের জন্য নয়। দাপটের ব্যবহার করতেই ফিরোজের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল রহমত উল্লাহ। আমিনা ভিলার ভাড়াটিয়ারা পরে বুঝেছিল ছোট মালিককে, কাউকে ম্যানেজার করার উসকানি দিয়ে কী কুড়ালটাই না মেরেছে তারা নিজেদের পায়ে।
ফিরোজ যখন রহমত উল্লাহকে তার দরজার কাছে পেয়ে বলল ‘আমি আর এদেরকে নিয়ে পারছি না এবার দায়িত্বটা আপনি নেন ভাই। আপনিই ভাড়া তোলেন, আমি মাঝে মাঝে দেখাশোনা করতে এসে টাকাটা নিয়ে যাব। হিসেব মেইনটেইন করতে দু’টো খাতা আমাদের দু’জনের কাছে থাকবে।’ রহমত উল্লাহর নিমরাজি, আমতা আমতা স্বরটা যে মেকি, ফিরোজ তা ভালোই করেই জেনেছিল। ফিরোজ এও জানে কসাই রহমত উল্লাহ সব টাকা তুলে পালিয়ে গেলে, সে কেন তার চৌদ্দগোষ্ঠীরও কিছুটি করার নেই। এমনিতে যে মাসের এক-দুই তারিখের মধ্যে টাকাটা ছুড়ে মেরে দিচ্ছে তাও তার করুণা। দুর্বলের উপর জবরদস্তি চলে কিন্তু রহমত উল্লাহর মতো যখন তখন লাশ ফেলা মেজাজের খড়গহস্তের কাছে শুধু সে কেন গোটা জাতিই জিম্মি হয়ে আছে।
তাদেরই ভাই বলে ডাকতে হয় ফিরোজ নিজামদের মতো মানুষের। ফিরোজ লক্ষ করেছে এক-দুই তারিখে সবার আগে ভাড়াটা পরিশোধ করার তাগিদে রহমত উল্লাহর তাকে কত চটাং চটাং কথা শুনিয়েছে। টাকাটা ভালোভাবে দেয়নি, দিয়েছে ছুড়ে আর ফিরোজকেই তা থাবা দিয়ে গ্রহণ করতে হয়েছে প্রতিকারহীনভাবে। অযথা রকমারি গজগজ তুলেছে রহমত উল্লাহ ‘শালার দুফইরা বেলায় ঠিকমতন ভাত খাওন যায় না। আরও চাইরডা চুলা লাগানোর কাম আছিল। এতগুলান মানুষ একটা কলে অয়নি? আরোকটা লাগান! আমরা কি ফকিন্নি ঢেকুরন্নির পুতনি? কষ্ট কইরা থাকতে পারুম না। আগামী মাসে যামু গিয়া কিন্তুক।’ ফিরোজ সরে গিয়ে কান বাঁচিয়েছে কিন্তু মান বাঁচল কি? সেই তো রহমত উল্লাহর ক্ষমতার কাছে তাকেও বশ মানতে হলো।
পরের মাসে বোঝা গেল রহমত উল্লাহকে দায়িত্ব দেওয়ায় কাজ হচ্ছে। একমাসের ভাড়া আরেক মাসে হলেও উঠে যাচ্ছে। এতটা অবশ্য আশা করেনি ফিরোজ। ইদানীং তার চাকরি খোঁজার বেগেও ভাটা পড়েছে। তবে ধান্ধা বুঝতে ব্যবসায়ী বন্ধু-বান্ধবের শরণাপন্ন হচ্ছে সে। যারা ব্যবসা করতে পারছে তারা কে কীভাবে করছে, পারছে। বাবার মতো ফিরোজেরও তা মাথায় ঢোকে না।
ফিরোজের বিয়ের কথাটি প্রায়ই আত্মীয়স্বজন এসে এসে পেড়ে যায়। একটা চাকরি অথবা ব্যবসা কিছু একটা না ধরলে একটা পজিশন সৃষ্টি না করতে পারলে কে তাকে মেয়ে দেবে? চাকরি করা মেয়েই পছন্দ ফিরোজের। কিন্তু কোনো চাকরি করা মেয়ের তো আর বেকার স্বামী পছন্দ নয়।
নিজামউদ্দিনের পরিবারের ‘আমিনা ভিলা’র উনিশ হাজার পাঁচশ টাকা মাত্র সম্বল। রহমত উল্লাহকে ম্যানেজার করার আগে হিসাবটি ছিল বিশ হাজার। এখন রহমত উল্লাহর গলাবাজির ভাড়া বাবদ কমছে পাঁচশ টাকা। এই টাকা থেকে গ্যাস, পানি, বিদ্যুতের বিল, পরিশোধ করতে হয়। মিউনিসিপ্যালিটির বিল, ইনকাম ট্যাক্স তার ওপর রামপুরায় তাদের ভাড়া থাকতে হয়। সব মিলিয়ে সেখানেও খরচ ছ-সাত হাজার টাকা। বাকি খরচের জন্যও অন্য কোনো পথ নেই রোজগারের। ভাড়াটিয়ারা শুধু জানে বাড়িওয়ালারা গলায় পা রেখে টাকা তুলে নেয়। কিন্তু এখান থেকে তাদের থাকেটা কী? তার ওপর তাদেরও তো চলতে হয়। এসব তারাও বুঝলে রহমত উল্লাহর মতো মানুষকে দিয়ে আর বানর ডেকে পিঠা ভাগের মতো করাতে হয় না। রহমত উল্লাহকে ফিরোজ নিজেও ভয় পায়। যদিও তা হাবেভাবে সতর্কতার সঙ্গে টের পেতে দেয় না। খাল কেটে আনা কুমিরের সঙ্গে সে ভারসাম্য রেখে চলারই চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে যদিও অন্যান্য ভাড়াটিয়ার প্রতি বেশি রূঢ় হতে বারণ করে। তার এটুকু উদারতা শেষে দুর্বলতারই শামিল মনে না করে বসে ব্যাটা।
ফিরোজ প্রতি মাসের দশ তারিখে সন্ধ্যার পরপর আসেনি বা দেরি হয়েছে এমন কখনো হয়নি। এ সময়ে কারও ঘর থেকে একখানা চেয়ার নিয়ে তাকে বসতে দেওয়া হয় একেবারে গেটের কাছে। যদিও ঘণ্টাখানেক সবার চলাচলের অসুবিধা হয় কিন্তু ওইটুকু জায়গা ছাড়া উপায় নেই। সাত-সাতটি করে তিন সারি রুমের মাঝখানে ফুট তিন-চার করে চলাচলের জায়গাটুকু শুধু ছাড়া হয়েছে। এরই একটা মধ্যে ছ’টা চুলা বসানো আর একটু তেরচা জায়গা বেরুনোতে পানির কল লাগানো হয়েছে। সেখান থেকেই পানি নিয়ে যেখানে সেখানে চলছে ইতস্তত কাপড় কাচা, থালাবাসন ধোয়া, বাচ্চার গোসল। যত্রতত্র পানির ব্যবহারে থিকথিক করে আমিনা ভিলার প্রতি ইঞ্চি জায়গা।
ফিরোজের পাশে সমান কিম্বা তারও চেয়ে বেশি মর্যাদায় পেতে দেওয়া হয় আরেকখানি চেয়ার, সেটাতে রহমত উল্লাহর বসে পড়ার আগে কোনো মাতৃহৃদয়া অথবা ভগ্নিহৃদয়া কাঁধ থেকে আঁচলখানা নামিয়ে দৌড়ে এসে অযথা তা মুছে দিতে পারলে যাকে বলে কৃতার্থ হয়ে যায়। ফিরোজের কাছে দৃশ্যটি বিষদৃশ্য ঠেকে আর তাতেই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই জাতীয় চরিত্র।
‘আমিনা ভিলা’র গেটটি যেন বাঘের বাচ্চা বাঘ! সামনে এসে দাঁড়ালে মনে একটা রাজকীয় ইমেজ চলে আসে এবং তা ফিরোজের বাবা নিজাম উদ্দিন সাহেবেরও হয়। নিজাম উদ্দিন যখন তার বোরখা পরা সৌম্য-শান্ত স্ত্রীটিকে নিয়ে এখানে আসেন তখন ক’মিনিট চোখ স্থির হয়ে থাকে তাদের শুধু টিনের নেমপ্লেটটিতেই। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন বাইরে থেকে প্রতিটি রুমের দেয়ালের বালিকণাও। ভাড়াটিয়ারা পরস্পর আগ্রহস্বরে বলাবলি করে, ‘কী গো দ্যাহে-লো আমাগো বাড়িওয়ালা বাড়িওয়ালি। কারওর ঘরে এটটু ডোহে না, বেইল পার কইরা দ্যায় বাড়িটা গুইরা গুইরা। ঘরে বইলে তো আমরা এট্টু সমাদর করবার পারি।’
প্রতিটি রুমের দেয়ালে বাইরে থেকে নাম্বারিং করা আছে। গ্রিলে রং লাগানোর সময়টিতেই তা করে রাখা হয়েছে। এক, দুই, তিন করে বিশ পর্যন্ত। তবু হিসাবের খাতায় প্রতিটি ঘরের নাম্বারের সঙ্গে লেখা আছে ওই ঘরের কোনো সদস্যেরও নাম। সে নামগুলোও তাদের বাচ্চাদেরই। আর যাদের বাচ্চা নেই তারাই কেবল নিজের নামটি লিখিয়েছে। তাও কোনো স্ত্রী’র নয়, স্বামীর নামটি। ঘনিয়ে আসা মেঘের মতো ফিরোজের গমগমে কণ্ঠে নিজের পরিচয় বাচ্চার নামটির শুদ্ধ উচ্চারণ শুনে বাচ্চার মায়েরা আহ্লাদিত হয়ে ওঠে। বাচ্চার হাতেই টাকাটা দিয়ে মা শব্দ করে ফিরোজের দৃষ্টিতে আকর্ষিত হতে চায়— ‘যা, যা দৌড়াইয়া গিয়া দিয়া আয়।’
গেটের কাছে পোতা বাঁশের মাথায় লাগানো ইলেকট্রিক বাল্ব ঘিরে মৃদু ভনভন শব্দে সূক্ষ্ম পোকার ঝাঁকের নিচে বসে ফিরোজ ডাকতে থাকে— এক নাম্বারের সুজন, দুই নাম্বার মরিয়ম, তিন নাম্বার বাদল, চার নাম্বার তাসলিমা পাঁচ নাম্বার শহীদ, ছয় নাম্বার সুমন, সাত নাম্বার পুষ্প…। আদতে এটুকু লগ্নক্ষণের বাইরে ওদের নামগুলো এরকম সুমইন্যা, মইরমী, বাদলা, তাসলী, শহীদ্যা, সুমইন্যা। পুষ্পকে অবশ্য কেউ-ই নাম ধরে ডাকে না। সবাই ওকে মতিয়ারের মা বলে ডাকে। যদিও মতিয়ারের বয়স পুষ্পের চেয়ে বছর পাঁচেক বেশি। আমিনা ভিলার কেউ মতিয়ারকে দেখেওনি। তবুও।
বছরখানেক এক সঙ্গে বসবাসের ফলে সবারই জানা হয়ে গেছে পুষ্পের নিজের কোনো সন্তানাদি নেই। তার স্বামীর আগের ঘরের একটিমাত্র ছেলে আছে। সে দুবাই থাকে। জুট করপোরেশনের অতি অধস্তন কর্মচারী বাপের পেনশনের সব ক’টি টাকা খরচ করে সে দুবাইয়ে চাকরি করছে। অথচ বাবাকে সে একখানা চিঠিও লেখে না টাকাপয়সা পাঠানো দূরে থাকুক। তবে সে ওখানে ভালো আছে। দুবাইয়ে মতিয়ারের সঙ্গে চেনাজানা আরও যারা থাকে তারা কেউ দেশে এসেছে শুনলে সামাদ মণ্ডল তার ভগ্নদশা শরীরটি টানতে টানতে গিয়ে শুনে আসে। ছেলে তার ভালো আছে, এ কথা শোনার পর পৃথিবীতে কেন মরণের পরও তার চাওয়ার কিছু থাকে না।
তার বোজা কণ্ঠ ভেদ করে একবারও বেরোয়নি ‘তোমরা তাকে বলো সে যেন বাপকে সামান্য কিছু টাকা-পয়সা পাঠায়।’ কিন্তু ঘরে ফিরতে ফিরতে সামাদ মণ্ডলের পা জড়িয়ে আসে। ‘যুবতী মাইয়াডা… বিয়া কইরা কী ফ্যাসাদেই না পড়ছি…।’ একলা হলে যেদিকে চোখ যেত চলে যাওয়া যায়। কিন্তু চলে যেতে পারে না সামাদ মণ্ডল, চলে যাওয়ার মতো কোন অজুহাতই সে খুঁজে পায় না, ওত পেতে থাকেও। তন্নতন্ন করে খোঁজে ‘মাইয়াডা যদি কোনোভাবে বুজাইতে পারে আমি তার জইন্যে আপদ তাইলে সেইক্ষণেই তার পথ পরিষ্কার কইরা দিয়া যামু। কিন্তু না মাইয়াডা নিজে না খাইয়া অহনতরি আমারেই খাওয়ায়। নিজের জইন্যে বাবে না, বাবে আমার জইন্যে। গ্রাম ছাড়লো আত্মীয়স্বজন সব ছাইড়া শুধু আমারে লইয়া নিরুদ্দেশ পাড়ি জমাইলো।’ এইটুকু বুঝতে পারা ছাড়া সামাদ মণ্ডলের আর কোনো সামর্থ্য নেই যা দিয়ে পুষ্পকে শর্তাধীন করে রাখা যায়।
কতদিন পুষ্পকে কেউ নাম ধরে ডাকে না। কতদিন! বছরখানেক হলো সে মানিকগঞ্জের নিজের গ্রাম থেকে স্বামীকে হাত ধরে নিয়ে এসেছে। গ্রামে সামাদ মণ্ডলের পুরোনো ঝুরঝুরে টিনের একখানা ঘর ছাড়া আর কিছুই নেই। তার প্রথম স্ত্রী মারা গেছে প্রথম বয়সেই। মতিয়ারের বয়স যখন সাত বছর। বিয়েথা আর করেননি। রিটায়ার করার পর ভেবেছিল ছেলেকে বিয়ে দিয়ে গ্রামেই থাকবে তারা। আরও একটু জমিজমা কিনে-টিনে কিন্তু ছেলে মানতে চাইল না। তার কোনো রকমের বিএ পাসটি নিয়ে এদেশে বাবুয়ানা চলবে না ভেবে বিদেশি টাকার আগাম সৌরভে বাপকেও বিভোর করে চলে গেল।
ঢাকায় রওনা হওয়ার প্রাক্কালে পুষ্পের মা পুষ্পকে দুমড়ানো-মুচড়ানো শ-দুয়েক টাকা হাতে গুঁজে দিতে দিতে চোখের পানিতে তা ভিজিয়ে একসা করে ফেলেছিল। আর এই ‘আমিনা ভিলা’র বারো নম্বর রুমটিতে আজিজ মণ্ডলের ঠিকানায় এসে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তার প্রায় সবটা পথেই হয়ে গিয়েছিল। আজিজ মণ্ডল সামাদ মণ্ডলের জ্ঞাতি ভাই। পুষ্পরা এসে প্রথম ওয়াক্তটি তাদের খাওয়ার উপরই খেয়েছে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ‘আমিনা ভিলা’র সাত নম্বর ঘরটি খালি ছিল। রহমত উল্লাহর সঙ্গে কথা পাকাপাকি করে বিকেল বিকেলই টিনের বাক্স আর পুরোনো ইয়ার ব্যাগে বয়ে আনা জিনিসপত্র খোলে। এরপর ঢাকা শহরে নতুন সংসারটি সাজাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল একুশ বছর বয়সী পুষ্প। তারপরের দিনগুলোতে চলতে থাকে তা টিকিয়ে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা। প্রথম কদিন গার্মেন্টসে ঘুরে ঘুরেই বুঝেছিল সে, এ কর্ম তার নয়। বরং পুরোনো পেশাটাই তার জন্যে ভালো, কষ্ট যেমনই হোক আর ইনকাম যাই হোক। ‘আমিনা ভিলা’র স্কুলে যাওয়ার বয়সী ছেলে মেয়েগুলোকে হাত করে ফেলল পুষ্প।
এতে তাঁদের মা-বাবারা খুশিই হলো। কারণ বহুমুখী বিপর্যয়ের কবল থেকে এগুলো বাগে আনে সাধ্য কার? কিন্তু পুষ্প সেই অসাধ্যই সাধন করেছে। আশপাশে বাড়িগুলো থেকেও ছেলে-মেয়েরা এসে ভরে যায় তার ঘর। অনেকগুলো শিফটে চলতে থাকে পুষ্পের পড়ানোর কাজ। এ-কাজই তো সে গ্রামেই করতে চেয়েছিল। সে যা পরিশ্রম করত দুটি মানুষের বেঁচে থাকার মতো কিছু টাকা ওঠাতে পারলেও সে আর গ্রাম-ছাড়া হতো না। হুড়মুড়ের এই শহরকে সহ্য করতে তার সময় লেগেছে। জীবনে যা সে ভাবতেও পারেনি। না ধোয়া মুখখানা সকালে কতজন দেখে ফেলে। এতখানি পথ বদনা হাতে পায়খানায় যেতে হয়। তার উপর সার বেঁধে রান্না। এককাতারে গোসল মহিলা-পুরুষ ভেদাভেদ নেই। পুষ্প বুঝে গেছে এদের মধ্যে এমন অনেকে যারা গ্রামেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। কিন্তু এত মানুষের ভিড় ছেড়ে তাদের ফাঁকা ফাঁকা লাগে।
আদতে ভিড়ের মোহ নির্জনতার স্বাদের চেয়ে আরও বেশিই আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে। পুষ্পের এখন তাই মনে হয়। মাসের দশ তারিখ আলো-আঁধারের দোলাচলে, নানান বযসী সার বাঁধা মানুষে ঘেরা ফিরোজ যখন বলে সাত নম্বরের ‘পুষ্প’ সব নাম থেকে ফিরোজের কণ্ঠ থেকে নিজের নামটি ছেঁকে তুলে ওই ডাকটি প্রাণের গহন প্রকোষ্ঠে মাতাল ভ্রমরার গুঞ্জরণের মতো বন্দি করে রাখে সে। বৃদ্ধ স্বামীর হাতে টাকাটা ধরিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। যদিও বহু যত্নের ভাঁজগুলো সে টাকা থেকে করাল, নিষ্ঠুর থাবায় দুমড়েমুচড়ে যায় তখনি রহমত উল্লাহর হাতে। প্রতিবার নাম এবং নম্বর ধরে ডাকার সাথে সাথে মানুষের সহজাত অভ্যাসবশত ফিরোজেরও চোখ চলে যায় কে কোনখানে হেঁটে আসছে। আর যারা হুড়মুড় করে গায়ে পড়ে দিচ্ছে, তারা তো নারদীয় কৌলিন্যে খ্যাত। তাদেরকে আর চেনার জন্য চোখ তুলতে হয় না। পুষ্পের মনে হয় ফিরোজ তাকে চেনে। পুষ্প নামের পোড়া ধূপের মতো মেয়েটিকে সে আলাদা করে চেনে। সে মেয়েটি যেমন, ঠিক তেমন করেই চেনে।
কদিন থেকে অঘোর জ্বর বয়ে যাচ্ছে পুষ্প’র। কীভাবে বয়ে গেল দশ তারিখের হৈহট্টগোল পুষ্প বুঝতেই পারল না। আজিজ মণ্ডলের স্ত্রী এসে তার সেবাযত্ন করছে, মায়ের মমতায় নিজেদের ভাগের উপর থেকে তুলে এনে পুষ্পকে আর স্বামীকে খাওয়াচ্ছে। কিন্তু পুষ্প খেতে পারছে না কিছুই। জ্বরের ঘোরে সে ভুলেই গেছে দশ তারিখ পার হলেও পনেরো তারিখের ফাঁড়াটি রয়ে গেছে। তার থেকে যমও রক্ষা করতে পারে না। সেদিন ‘আমিনা ভিলা’য় কেউ মারা গেলেও বাকি বাকি ভাড়া শোধ না করে লাশ দাফন নিষেধ। আর এ নিষেধাজ্ঞা আজরাইলেরও অধম রহমত উল্লাহ। যে নাকি অন্যসব বাকির ভাড়াটিয়ার সঙ্গে পুষ্পকেও চোখ কাত করে কথা বলতে ছাড়ে না। তাছাড়া ছোট-বড় সবাই পুষ্পকে সমীহ করে কথা বলে। কারণ পুষ্প তাদের থেকে যে আলাদা এটা সে সবার কাছে প্রমাণ করেছে। বাচ্চারা পুষ্পকে আপা ডাকলেও তাদের মা-বাবারা তাকে ‘মাস্টার’ আপা বলেই ডাকে।‘আমিনা ভিলা’র কেউ ভালোমন্দ রান্না করলেও পুষ্পকে রেখে খায় না।
হাতে যে-কটা টাকা ছিল তাই নিয়ে পুষ্প বেলা পড়তেই আজিজ মণ্ডলের স্ত্রীর কাঁধে ভর দিয়ে ডাক্তারের কাছে গেল। সব ওষুধ কেনা হলো না টাকার অভাবে। বাকি আনার মতো পরিচয়ও নেই কোনো দোকানে। তবু দোকানদার জরুরিগুলো বেছে বেছে দু-চারটে করে সস্তাদরের-গুলো দিল। ‘আমিনা ভিলা’র সামনে ফিরে এসে পকেট গেটটি দিয়ে ঢুকে মুখখানা উঁচু করতেই মরণাপন্ন পুষ্প দেখল তার স্বামী সামাদ মণ্ডল বন্ধ দরজাটি আগলে নিচে বসে আছে। দরজায় বহু চেনা ঢাউস তালাটি ঝোলানো দেখে আর কিছু বুঝতে বাকি থাকে না পুষ্পর। সাপে কাটা মানুষের মতো তখনি সে ঢলে পড়ে গেল স্বামীর গায়ের উপর। সামাদ মণ্ডল একা পেরে ওঠে না, কেউ এসে তার স্ত্রীকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল সেই বারো নম্বর রুমটিতে। যেখানে তার প্রথম এসে উঠেছিল মেহমানের মর্যাদায়। পুষ্প ক্রমে সব আবার বুঝতে পারলেও চোখ দু’টো যেন কষ্ট করে বন্ধ করে রেখেছে। এই পৃথিবীর আলো, বাতাস, মানুষের মুখ সব কেমন বিষাক্ত ঠেকছে তার কাছে।
আজিজ মণ্ডলের স্ত্রী পানি দেওয়া শেষ করে মাথাটা মুছিয়ে দিচ্ছে নিজের আঁচলে। পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে তার কপালে। পুষ্প বুঝতে পারছে তাকে ঘিরে আছে অনেক মহিলা। দরজার বাইরে মানুষগুলোও তার চেতন এড়াল না। তবু সে হনহন করে হাঁটছে আলপথ ধরে। স্কুলের শেষের ক্লাসের ছাত্রী থাকাকালীন পরম ঔদ্ধত্যে যেমন উঁচু তালে হাঁটত দু’টি বেণি দুলিয়ে। গায়ের ফিনফিনে ওড়নাটি বাতাসে ঢেউয়ের মতো উড়ত। পুষ্প দৌড়াচ্ছে ঘন সবুজ বৃক্ষরাজিতে ছেয়ে থাকা তাদের জীর্ণ শনের ঘরখানার দিকে, যেখানে পৃথিবীর তাবত মমতা বুকে ধারণ করে বসে আছে তার জীবন্ত দগ্ধ প্রতিমার মতো উদ্বেগাকুল মা। কিন্তু ‘আমিনা ভিলা’র মানুষগুলোর সমবেদনার পঙক্তিগুলো তাকে আবার টেনে আনছে সুতোয় বাঁধা প্রজাপতির মতো নিয়তির করপুটে।
ওষুধগুলো কোথায় রেখেছে আজিজ মণ্ডলের স্ত্রী সায়রা বেগম অর্থাৎ পুষ্পের সায়রা বুজি। সায়রা বুজি তা যেমন মনে নেই তেমনি ওষুধ খাওয়ানোর পুরো ব্যাপারটি সে ভুলে গেছে এত বড় বিপর্যয়ে। আজিজ মণ্ডলের পাঁচ ছেলেমেয়ের মধ্যে মেয়ে তিনটি বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে দু’টোও তাদের ভাষায় বিয়ের লায়েক। এরই মধ্যে আছে নাতিপুতি ধকল। আজও বড় মেয়েটি এসেছে তার দু’টি বাচ্চা নিয়ে। রাতে নড়বড়ে চৌকিটির উপর ঠাসাঠাসি করে ছিল আজিজ মণ্ডলের দুই ছেলেসহ নাতি দু’টি ও মেয়ে। আর নিচে কোনো রকমে আজিজ মণ্ডল আর তার স্ত্রীসহ স্বামীকে নিয়ে পড়ে থেকে পাথরের মতো ভারী রাতটুকু পার করল পুষ্প।
রাতে কিছুই খায়নি পুষ্প, কেউ সেধেও খাওয়াতে পারেনি। ‘আমিনা ভিলা’র প্রায় সবাই ঘুমোতে যাওয়ার আগে দরজা গলিয়ে এক-একবার করে দেখে গেছে পুষ্পকে, তাতে পুষ্পের অস্বস্তিই বেড়েছে। কোনো নড়াচড়া নেই, মরার মতো পড়ে আছে পুষ্প। ঘুম আসেনি। চলন্ত ট্রেনের যাত্রীর মতো সব স্মৃতি তাকে ছেড়ে যাচ্ছে দ্রুত। ইচ্ছে করেও সে যেন থামতে পারছে না। তার চোখের পাতা নদীর কূলের মতো ভাসিয়ে নিচ্ছে বাঁধ ভেঙে আসা কোনো স্রোত। নড়ে না পুষ্প। ভেতরটা ডুকরে উঠতে চাইছে। নিশ্চল পড়ে থাকাটাই তা ঠেকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর মানুষ কেন জানবে তার অপ্রাপ্তির বেদনা? যে তৃষ্ণা মেটার নয়, যে গ্লানি ধুয়ে যাওয়ার নয় কেন তা জানবে মানুষ! নিজের প্রাণটিকেই সে উৎস ও মোহনার টানে নোঙ্গর করতে শিখে ফেলেছে। তবু নিয়তি তাকে এমন চরম প্রহসনে দাগী, হাস্যাস্পদ করে ছাড়ল? এটুকু না হলে বুঝি বিধির ষোলকলা পূর্ণ হতো না।
পুষ্প যখন বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল, সূর্যের আভা তখন ফুটি ফুটি করছে, সূর্য নয়। মানুষের বাড়ির দেয়াল, ছাদ টপকে সে যখন ‘আমিনা ভিলা’র পূর্বমুখী দরজাগুলোয় বিম্বিত হলো ততক্ষণে পুষ্প তার ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি ঘুরে একহাজার টাকা যোগাড় করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। উদভ্রান্তের মতো চেহারা দেখে কেউ আর পুষ্পকে ‘পরে দিচ্ছি’র অজুহাত দেখাতে সাহস পায়নি। সকালেরও আগে ওঠে রহমত উল্লাহ। কারণ তার কাজটিই হচ্ছে খুব সকালেই গরুটিকে খণ্ডখণ্ড করে দোকানে ঝুলিয়ে দেওয়া। পুষ্প রহমত উল্লাহর কাছে বাড়িওয়ালার ঠিকানা চাইতেই সে খেঁকিয়ে উঠল—‘টাকাগুলান আমারে দ্যান মতিয়ারের মা। তালা খোলনের মালিক আমিই।’ পুষ্প’র সেটা অজানা নয়। কারণ রহমত উল্লাহই ফিরোজকে দিয়ে ঢাউশ ঢাউশ একগাদা তালা কিনিয়েছে। এমনতরো কাজে লাগাতে এবং সেগুলো সংরক্ষিত থাকে রহমত উল্লাহর তেলচিটে শোকেসটিতে। কঙ্কালের দাঁতের মতোই তা বিষাক্ত সৌন্দর্য ছড়ায় কসাই রহমতউল্লা’র ঘরজুড়ে।
কারও কারও ফিসফিসানি থেকে ‘আমিনা ভিলা’র মালিকের বাসার ঠিকানাটা পেয়েই বড় রাস্তাটিতে এই প্রথম একা কোথাও যেতে উঠে এল। গোরান থেকে রামপুরার পথ একেবারে কম নয়। কিন্তু পুষ্প এতটুকু ক্লান্তিবোধ করল না। কিছুদূর এগোয় আর নিরীহ চেহারা দেখে ‘আমিনা ভিলা’র মালিকের বাসার নম্বর জানতে চায়। কখনও আবার ফিরোজ নিজামের নাম উল্লেখ করে থমকে দাঁড়ায়। আবার দ্রুত এগোতে থাকে। তার মনে হলো মুহূর্তে সে উড়ে এসে খুঁজে পেয়েছে গলির শেষ মাথার পাঁচতলা বিল্ডিংটি। যেটার দোতলায় নিজামউদ্দিনের ছেলে ফিরোজ নিজাম থাকে। একটা বয়স্ক মানুষকে বের করে দিয়ে যে কাল সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে থেকে তার ঘরের তালাবদ্ধ করেছে। সেই বিবেকহীন পাষণ্ডের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার মুখের ওপর এই টাকাগুলো ছুড়ে দিয়েই সে ফিরে আসবে।
এত সকালে কলিংবেল বেজে ওঠায় ঘুম জড়ানো চোখে সামনের রুমে এসে পিপহোলে চোখ রাখল ফিরোজ। তারপর দ্বিধা করার মতো ভদ্রতাটুকুও দেখানোর প্রয়োজন মনে না করে সম্পূর্ণ দরজাটি খুলে বলতে যাচ্ছিল— ‘চাবি কী আমি নিয়ে এসেছি নাকি? ওসব হ্যাপা তো রহমত উল্লাহ…।’ কিন্তু পুষ্প তাকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে, টাকাগুলো ফিরোজের অভ্যাসবশত মুঠোয় ধরিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগল, ‘মাসে একবার আপনি আমার নামটি ধরে ডাকেন, আর আপনার মুখে ওই ডাকটি শোনার জন্য আমি আপ্রাণচেষ্টায় টাকাগুলো গুছিয়ে রাখি। সারাটি মাস আমি ব্যাকুল হয়ে থাকি ওই সময়টুকুর জন্যে-ওই ডাকটির জন্যে…।’
সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে নিজেকে বড় ঠুনকো মনে হয় পুষ্প’র। পথে পথে অনবরত হোঁচট খায়, ক্লান্তি ও ঘেন্নায় পা গুলিয়ে ওঠে তার। যা সে গড়গড় করে বলে ফেলেছে ফিরোজকে, এরকম করে তো কোনো কথা সে ভেবে আসেনি! সে তো এসেছিল ফিরোজ নিজামের মুখের ওপর নিজের হাতের টাকগুলো ছুড়ে দিতে শুধু। পুষ্প খেয়ালই করে না তার হেঁটে যাওয়ার দৃশ্যটি সবার চোখে অস্বাভাবিক লাগছে। যে দোকানি দোকানের ঝাঁপ মাত্র খুলতে যাচ্চিলো, সেও থমকে আছে পুষ্পের প্রতিটি পদক্ষেপে অপলক নজর জড়িয়ে। পথচারীরা উদ্বেগ আকুল হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে রেখেছে হলুদবরণ, সোমত্ত মেয়েটির অমন টলোমলো গতির পায়ে। চোখের মুখে যার বিদ্যুতের মতো তেজ ঝলসে দিচ্ছে নরম ভোর। আলো সূর্যমুখী রঙ ধরার আগেই সে ঢুকে পড়ে সেই মোহনাহীন সেই উৎসে। যেখানে জীবন কেন্নোর মতো নিপাট কুণ্ডলীতে গুটিয়ে রাখে তার অসংখ্য পা।
আমিন ভিলা বা ওই ধরনের বস্তিগুলোতে চারজনের বেশি থাকার অনুমতি নেই। তবে নিজেদের ছেলেমেয়ে দু-একটা বেশি হলে সেক্ষেত্রে নিয়ম কিছুটা শিথিল। আবার যারা পরিবারের সদস্য শুধু দু-চারজন, তারা আবার ওই একরুমের মধ্যেও একজন ছাড়া অনেক সময় দু’জনকেও জুটিয়ে নেয় ঘরভাড়া কিছুটা উসুল করতে। ভাই, শালা, দেওর, মামা, বা ভাগ্নের ডাহা মিথ্যে এই পরিচয় একসময় প্রতিষ্ঠিতও হয়ে যায় এখানে। আবার এই একই নিয়মে কেউ কেউ মেয়েদের রাখে। আর ঠেকায় পড়ে থাকার এদের সংখ্যাই বেশি।
দুই নম্বরে মরিয়মদের রুমে একজনকে তেমনি সন্দেহ হওয়ায় রহমত উল্লাহ খেঁকিয়ে বেড়াচ্ছে ‘পানি খরচ অইতাছে, পায়খানা বইরা যাইতাছে, বাড়ি গিজগিজ করে আসল বাড়াইট্যায়। হ্যার উপর আবারকা ফাউ মানুষ।’ রহমত উল্লাহর কথায় যুক্তি আছে, কেউ টু-শব্দটি করছে না। মরিয়মের মা শুধু চুপ করে থাকলে রহমত উল্লাহর কথাই ষোল আনার উপর আঠারো আনা সত্যি হয়ে যায় দেখে, আশপাশের মানুষগুলোকে শোনাতে শুধু নিস্তেজ কণ্ঠটি সরব করে মিনমিনিয়ে বলে ওঠে, ‘বাই যে কী কন না? ইয়াকুইব্বা অইল মইরমীর বাপের আপন চাচাত বাই! আর আমাগো ঘরে আমরা মানুষইত্তো হুগলডি মিইল্ল্যা তিনজন। বাইরতন একজন-দুইজন তো রাহনই যায়।’
মরিয়মের মা শরিফার কথা রহমত উল্লাহর কানে পৌঁছানো দূরে থাকুক, কাছের মানুষও ঠিক শুনেছে কিনা সন্দেহ। রহমত উল্লাহকে শোনাতে তো শরিফা বলেনি। সে সাহস আছে কারও? শরিফা বলেছে ও বাড়িতে বসত করা অন্য মেয়েছেলের উদ্দেশ্যে। তারাও যেন ওকে ছুঁতো-নাতায় পেয়ে না বসে!
শরীর ছোটখাটো হলেও সময়ের আগেই নেতিয়ে পড়েছে শরিফা। তবে ওর চোপার জোর কুকুরের পানিতে নামার দশা। ছুঁলে কেটে লবণ খাওয়াও ভালো তার চেয়ে, যে খেয়েছে শরিফার চোপার ঝাল সেই কেবল বোঝে। ভিমরুলের চাকে ঢিল তাই সহজে কেউ আর মারে না। তবে ফিরোজের নমনীয় থাকার কারণ অন্য। তার কথা হচ্ছে, যেভাবে চলছে চলুক। কত অন্যায়ই তো মানুষ করেছে! এতকিছু দেখলে হয়? মাত্র ক’টা টাকার জন্য যে ঘরে অন্য লোক জায়গা দেয় তার কি ঝামেলা কম? লুকিয়ে-চুরিয়ে যদি কেউ থেকে যায় তো যাকগে। ফিরোজের দোষও রহমত উল্লাহর কাছে ক্ষমাহীন। গেটটি গলিয়ে ফিরোজ বাড়ির বাইরে না যেতেই সে আমিন ভিলার চৌহদ্দি কাঁপিয়ে তোলে। ‘কলপারে বিড়, চুলার কাছে বিড়, পায়খানা চাইপ্পা রহন লাগে… শালার আচুদা বাড়িওয়ালা… বাড়িতে মোটে পা ফেলন যায় না! গুষ্টি কিলাই তোর ম্যানেজারির! আমারে ম্যানেজারি দিয়া আবার ক্ষমতা হাতে রাহন চুদায়।’
‘আমিনা ভিলা’র কেউ কেউ আবার ফোঁড়ন দেয়— ‘হলো, এতগুলান মাইনষেরে দ্যাহাশুনা কম কতানি? মাত্রর পাঁচশ টাহা মাফ। পুরা ভাড়াই না লওনের দরকার আছিল ম্যানেজার ভাই, রতন।’ রহমত উল্লাহ এ সময় তার দিকে হীন দৃষ্টিতে তাকায় যে, মন রাখা কথায় রহমত উল্লাহর মনোযোগটি চাইছে। কারণ রহমত উল্লাহ লাই দিয়ে মাথায় ওঠানোর দুর্বল বিদ্যে শেখেনি। ওটা হলো শুধু ফিরোজ নিজাম আর তার বাপ নিজামউদ্দিনের মতো মানুষের চরিত্রের অপারগ দিক। বুঝিবা রহমত উল্লাহর এ ধরনের কথা ফিরোজেরও কান এড়ায় না। তবু আপনি মান আপনা রাখা। কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকার মতো ফিরোজ টেরই পেতে দেয় না তাকে হেয় করে বলা কথাগুলো সে কখনো শুনে ফেলেছে।
শুধু রহমত উল্লাহর বেহরমপনাই নয়, মইরমীর বাপ সিরাজ মিয়াও বলতে শুরু করেছে, আমি যেমন পারি গর বারা একলাই যুগামু। আমার গরে কেওরে রাহনের দরকার নাই। ইয়াকুইব্বারে তুই বাঘা। মাগী জোয়ান দেইখ্যা জোডাইয়া লইছোছ, ওরে আমরা চিনি না, জানি না, ওরে আমার গরে জাগা দিবার পারবি না।’ সিরাজ মিয়া এসব কথার উত্তর শরিফা যা দেয়, কান পেতে শোনা যায় না। তবু সিরাজ মিয়া যখন ডাক ছাড়ে ‘খাল কাইট্টা কুমির আনছি আমি… মাগী ছেমড়ায় তোরে হাঙা করলে যাইগগা।’ কিন্তু শরিফা সিদ্ধান্তে অটল। তার গলা বাড়তেই থাকে— ওই খানকি মাগীর পুলা, শইল্যের ত্যাজ কমোনে নামাজ ধরছো, ভালো হইয়া গেছো, না? এহন মাইনষেরে সন্দেহ করণ চুদাও? ইয়াকুইব্বারে রাহুম আমার কাপড়ের তলে, দেহি তুই কী করছ! আমার মাতার উপর তুই কাডল ভাইঙ্গা খাইছোস। আমারে দিয়া তোর জাউরা মানুষ করছোস। এহন আমারে তোর খালি বদনাম দিয়া গরের বাইর করনের বাকি রাখছোস। কাজডা বালো অইতাছে না। বুজিস!’
‘গর আমার। আমি না রাখলে থাহে কেমনে দেহিস!’ বলতে বলতে দরজার আগলা হয়ে যাওয়া খিলখানা নিয়ে তেড়ে যায় সিরাজ মিয়া। কিন্তু ঘরে-বাইরে দরজা বরাবর জটলা পাকিয়ে থাকা মানুষের হস্তক্ষেপে রক্তাক্ত হওয়া থেকে বেঁচে যায় শরিফা। কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র চিহ্ন ভাসে না তার তার মুখে। সে নাগিনীর ফণার মতো মুখ উঁচিয়ে ‘গোলামের পুত, আমার হাড্ডি-মাংস কালা কইরা ফালাইছোস। তোরা জাউরারে আমি বুকের দুদ খাওয়াইয়া মানুষ করছি, তোরে মাইনষের জুতা খাওনের তন বাঁচাইছি। তুই আমারে কি প্রত্তিদান দিছিলি? আমি তোরে ছাইড়া দিমু বাবছোস? এমতেই আমি পত্তিশোদ লমু, আমিও বাপের বেডি!’
পাঁচ বছরের শিশু মরিয়ম ডালুমালু করে একবার তার মায়ের ক্ষুব্ধ মুখখানার দিকে তাকায়, আরেকবার বাপকে খোঁজে, আর ঘন হয়ে থাকা মানুষগুলো শরিফার পরবর্তী ডায়লগের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। অথচ এত কথা যাকে নিয়ে ইয়াকুবের কোনো পাত্তাই নেই। একটু আগেও তো সে এখানেই ছিল। এমন অবস্থায় সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কূলকিনারা খোঁজে যেন। মরিয়মের জন্মরহস্যটা সবাইকে নারকেলের কাদার মতো শক্তভাবে পাকিয়ে রাখে শেষপর্যন্ত।
দীর্ঘদিন একই বাউন্ডারির মধ্যে থেকে, একই চুলা, বাথরুম, কল ব্যবহার করে বস্তিবাসীরা একেকজন একেকজনের কাছে বহুল পঠিত চরিত্র। দেখা যায় প্রতিটি ঘরেই প্রতিদিন একই বিষয় নিয়ে বাদাবাদি, হাতাহাতি, রক্তারক্তি।
পরদিনই ভোরে ক’দিনের আমাশয়ে দুর্বল হয়ে যাওয়া শরীর নিয়ে সিরাজ মিয়া রাজমিস্ত্রির কাজে বেরিয়ে গেলে পেছনে পেছনে দু’জনের দুপুরের খাবারে পূর্ণ টিফিন ক্যারিয়ার হাতে যুবক ইয়াকুব আলী হাঁটছে। যাকে নিয়ে শরিফা আর সিরাজ মিয়া স্বামী-স্ত্রীতে মাঝে মাঝেই সাপ নেউল হয়ে ওঠে। শরিফার সকালের ভেজা চুলগুলো ততক্ষণে খুলে দিতে সময় হয়। একনাগাড়ে অনেকক্ষণ শরিফা চুলগুলো নাড়াচাড়া করে আহ্লাদিত আঙুলে।
এই শরিফারই তখন শোকের সময়, তার মাত্র সাতদিন আগে তার একটা মেয়ে হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ধনুষ্টংকারে মারা গেছে। শরিফার বিলাপে যখন তখন মানুষ কাতর হয়ে উঠেছে। এর ভেতর একরাতে সিরাজ মিয়া শরিফার পা জড়িয়ে ধরে বলল, ‘আমি একটা অন্যায় করছি! তুই আমারে মাফ কইরা দিবি ক?’ শরিফা ধড়ফড় করে উঠে বসে সিরাজ মিয়াকে ধরে বলল, ‘কী অইছে কন! আপনে আমার স্বামী, আপনের সব অন্যাই আমার কাছে মাফ। সিরাজ মিয়া কাঁচা কথায় ছাড়ল না। কোনখান থেকে কোরআন শরিফ এসে বিনা অজুতে তা শরিফার মাথায় চেপে ধরল, ‘এবার ক! কুনোদিন কেওরে কইতে পারবি না।’
শরিফা আঁচ করতে পারে না তার সর্বনাশের পরিমাণ। তাই একেবারে ঝরঝরে কণ্ঠে বলল, ‘হ কমু না।’ সিরাজ তারপর নির্ভয়ে বলল, ‘জমিলার প্যাডে আমার বাচ্চা! অয়্যারে তুই উদ্দার কর, নইলে মাইনষে আমারে পিডাইয়া মাইরা ফালাইবো।’ জমিলা শরিফার দেশের মেয়ে, আবার শরিফার ছোটবেলার পাতানো সই। সে প্রায়ই শরিফার কাছে এসে থাকত, আর সেই সুযোগে সিরাজ মিয়া মইরমের বাপ হওয়ার বীজ রোপণ করে ফেলল শরিফার ঘুমিয়ে থাকার সুযোগে। সেদিন স্বামীর মুখে সব শুনে শরিফা ‘আল্লারে…।’ বলে একটা চিৎকার শুধু দিতে পেরেছিল। পরদিন হুঁশ ফিরে পেলেও ক’দিন কারও সঙ্গে কথাই বলেনি, বা বলতে পারেনি। তারপর পুরোনো বাসা থেকে নতুন বাসায় তাকে এনে তোলে সিরাজ মিয়া। জমিলা খালাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই রক্তমাথা শিশু মইরমকে এনে ওর কোলেও তুলে দিয়েছিল সিরাজ মিয়া নিজেই।
‘আমিনা ভিলা’য় তারা মাত্র ক’মাসের ভাড়াটিয়া। মইরমকে জড়িয়ে এখানে সবার চোখে ঘন রহস্য। তবু শরিফা ইয়াকুবের সঙ্গে পালিয়ে যেতে মইরমকে রেখে গেল না। সিরাজ মিয়ার ঘরে মন টেকে না। সে বাড়ি এলেই সবাই চোখ উঁচু করে তাকায়। ওর বিলাপে মন নিবিষ্ট করে শুনতে পায় ‘শরিফা তুই যেখানেই থাকোস, চইল্লা আয়, আমি তরে কিচ্ছু কমু না। খালি ওই গোলামের পুতরে খুন কইরা ফালামু… আল্লারে…।’
আঠারো নম্বর রুমের সামনে অচেনা দুই মেয়েকে হাস্য-কৌতুকরত অবস্থায় দেখে ফিরোজ কিছুটা রূঢ় স্বরেই জিজ্ঞেস করল, ‘এই মেয়েরা, তোরা কোন ঘরে থাকিস?’
—এই তো এই ঘরেই।
—কবে থেকে থাকিস?
—ওমা! আপনেরা এ বাড়ি করণের পর থেক্কেই তো এ গরে আমরা পথথম ভাড়াটিয়া। নাটুকে ভঙ্গিতে শুদ্ধ করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে হামিদা।
—ও তোর কী হয়? হামিদার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তেরো-চৌদ্দ বছরের হাজেরাকে দেখিয়ে বলল ফিরোজ।
—ও আমাদের বান্ধুবী, সখিনা আপা তার আগের স্বামী নিয়ে আগে যে বাড়ি থাকত আমরা দুইজন সেইখানেও থাকতাম, সবতে মিলে ভাড়া দিতাম। এখানেও আমরা এই তিনজনে মিলে ঘর ভাড়া দেই। তিনজনে কামও করি এক গার্মেন্টসে। সখিনা আপার আগের স্বামীও আমাগো সঙ্গে এক গার্মেন্টসে ছিল, কিন্তু বেশি বেতনের লোবে আরেক গার্মেন্টসে গিয়া আরেকজনের লগে লাইন… ফিরোজের বুঝতে বাকি থাকে না আর কিছুই। তাই প্রশ্নের ধরন পাল্টে যায় নিজের অজান্তে। ফিরোজ কিছুটা প্রগলভ হয়েও ওঠে, যা তার স্বভাবে নেই, বাড়িতে তোর কে কে আছে? হামিদাকে প্রশ্নটি করল ফিরোজ।
—শুধু মা আছে… আর আমারে তিন বছরে রাইখা, বাবা মরছে, আর পাঁচ বছরের ভাই আছে। তারা দ্যাশে থাকে।
—তোরে তিন বছরের রেখে তোর বাপ মরলে তোর আবার পাঁচ বছরের ভাই থাকে কেমন করে? প্রশ্নটি করে নিজেই বিব্রতবোধ করল ফিরোজ।
—আমাগো দ্যাশে যারা বল্লাকের কারবার করে তাগো বাপ মরলিও বাই অয়। ঝটপট উত্তর হাজেরার।
—তোদের দেশ কোথায়?
—রংপুর। ওয় আমাগের পাশের বাড়ির। হামিদাও হাজেরার একসঙ্গে দেওয়া উত্তর দু’টি ফিরোজের কানে একসঙ্গে ঢুকল কিনা ওরা তা বুঝতে পারল না।
দুপুরের খাবার খেয়ে কোমর থেকে গামছা খুলে হাত মুছতে মুছতে রহমত উল্লাহ এগোলো ওদের দিকে। ঢলেপড়া সূর্যের নিস্তেজ একফালি রোদে মাখামাখি তিনজনের দাঁড়িয়ে থাকা জায়গাটুকুর দিকে রহমত উল্লাহ এগিয়ে আসতেই ফিরোজ সবার ছায়া মাড়িয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল রহমত উল্লাহর দিকে। আগে ফিরোজ পরে রহমত উল্লাহ পকেট গেটটি দিয়ে বেরিয়ে গেল। ফিরোজের অসময়ে বাড়িটি চক্কর দিতে আসার কারণটি হাঁটতে হাঁটতে উপযাচকের মতো বলতে লাগল ফিরোজ, ‘বনশ্রীতে নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। ভাবছিলাম ওখানে একটা দোকান নিয়ে হার্ডওয়্যারের ব্যবসা করব। একটা দোকান পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু মাস্তানরা মোটা অংকের চাঁদা চায়…। যারা দোকানপাতি চালাচ্ছে তাদের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, রেগুলার চাঁদা না দিলে ব্যবসার কথা চিন্তাও করা যায় না।
— ‘আমারে পার্টনার রাহেন! চান্দা চাইতে আইলে দুই টুকুরা কইরা ফালামু।’ রহমত উল্লাহর কথা শুনে যত না তার চেয়ে ওর স্পর্ধা দেখে চমকে ওঠে ফিরোজ। দামি শার্ট-প্যান্ট, টাই, জুতো পরা ফিরোজের। যে-কেউ তার দিকে তাকালে সম্ভ্রম ঝরবে দৃষ্টিতে। তার পোশাক-আশাক রুচি মেজাজ সবারই আকৃষ্ট হওয়ার মতো। এখানে বাড়িওয়ালা-ভাড়াটিয়া সম্পর্ক হওয়ার পরও সবাই তার গুণমুগ্ধ। রূপ-ব্যক্তিত্বেও মুগ্ধ। সেই ফিরোজকে সে কোথায় নামিয়ে এনেছে! ব্যবসা করতে হলেও ওকে পার্টনার করতে হবে? কিন্তু ভেতরের প্রতিক্রিয়া কিছুই বুঝতে না দিযে বড় রাস্তায় উঠে সে রিকশা ডাকল। পেছনে রহমত উল্লাহ তখনো ওর ব্যবসার পার্টনার হওয়ার ইচ্ছে নিয়ে দাঁড়ানো ছিল কিনা তা আর দেখতে ইচ্ছে করল না।
সেদিন পুষ্পের আচরণ ফিরোজকে আলোড়িত না করতে পারলেও দমিয়ে দিয়েছে। পুষ্প যুবতী মেয়ে নাকি সে কী, তা ফিরোজের জানার কথাও নয়। ফিরোজ দুই-একজন ছাড়া আজও ঠিক করে জানে না ‘আমিনা ভিলা’র কোন পুরুষটির স্ত্রী কোন মহিলা। কোন মহিলার স্বামী কোন পুরুষটি। এখানে এলে কেমন তালগোল পাকিয়ে যায় তার। এখান থেকে বের হতে পারলে লম্বা করে নিঃশ্বাস টানতে থাকে প্রতিবার। আর কে পুষ্প, কে কুসুম, কে প্রসূন এটা তার জানার জন্যে জরুরি কোনো সাবজেক্ট নয়। চাচা, মামা, খালা, ফুপুরা, তাদের বিবাহযোগ্য মেয়েগুলোকে লেলিয়ে দিয়ে সবাই যে নীরব প্রতিযোগিতায় টোপ ফেলেছে তার দিকে, এটা ফিরোজ বুঝে উঠতে না পারলেও মা তাকে সাফ সাফ বলে দিয়েছিলেন, ‘দেখো বাবা আমি কোনো আত্মীয়-স্বজনের মেয়েকে বউ করে আনব না। কারণ আত্মীয়ের মধ্যে আত্মীয়তার দিন ফুরিয়ে গেছে। তুমি আমাদের বড় ছেলে। মেয়ে আনব আরও বড় ঘর থেকে। দেখে-শুনে।’
আত্মীয়েরা আমার যে যেমন আছে এমনিতেই সম্পর্ক ভালো থাক। বাধ্য ছেলে ফিরোজ আর এদিকে ওদিকে তাকায়নি, বা তাকানোর সাহস তার ছিল না। না হলে চাকরি না হলেও দু-একটা ছেলেমেয়ের বাপ সে বনে যেতে পারত এতদিন। এখনো চাকরি করা মেয়ে পছন্দ ফিরোজের। কিন্তু চাকরি করা মেয়ের তো আর বেকার স্বামী পছন্দ নয়। মা-বাবা একের পর এক ফিরোজের জন্যে পাত্রী দেখেই চলেছেন। ক্লান্তি নেই কিন্তু মনমতো নামাজি কালামি, পর্দানশীন এবং অভিজাত, ঘরোয়া মেয়ে এ সময়ে যে দুর্লভ তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে ফিরোজ। একটি মেয়ে দেখে এসে ওর মা-বাবা দু’জন যে বিবরণ দিতে থাকেন আরেকটি না দেখা পর্যন্ত, তাতেই ফিরোজ বুঝে গেছে আপাতত বিয়ে তার ভাগ্যে নেই। তাবে তার নিজস্ব আয়ের অবলম্বনটি থাকলে যে সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠত এটা সে বুঝে গেছে তার ছোট ভাই ফয়েজকে দেখে।
ফয়েজ যে মেয়েকে বিয়ে করেছে সে মেয়ে নাকি তার পছন্দের প্রতিটি ছেলেকে কাত করে সটকে পড়ে। ফয়েজকেও নাকি সেই ফাঁদে টেনে গলাধাক্কা দিতেই ফেঁসে গেল। বাপ-বেটি দু’জনেই এখন ফয়েজের হাতে জিম্মি। তবে শাশুড়ি পক্ষে থাকায় পরিস্থিতি এখনো বেসামাল হয়ে ওঠেনি।
ছোটবেলা দাদির মুখে শোনা একটি কাহিনী মনে পড়ে যায় ফিরোজের। একদল ডাকাত এক বাড়িতে ডাকাতি করতে ঢোকে। কিন্তু সে বাড়িতে একটি সুন্দরী মেয়ে দেখে ডাকাত সর্দারের চোখ আটকে যায় তার মুখে। দলের সবাইকে লুটতরাজে বিরতির আদেশ দিয়ে গৃহকর্তার কাছে নিজের জন্য তখনই মেয়েটির বিয়ের পয়গাম দিয়ে বসল সে। কিন্তু গৃহকর্তা তার জান দিতে রাজি তবু মেয়ে দিতে রাজি নয়। অগত্যা ডাকাত গেল মেয়েটির কাছে, তাকে পেলে বাকি জীবনে ভালো হয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাত জোড় করল। কিন্তু মেয়েটি সর্দারের মুখে থুতু ছিটিয়ে দিতেই ডাকাত সর্দার সব ফেলে শুধু মেয়েটিকে নিয়ে তাদের নৌকায় উঠে, নৌকা ভাসিয়ে দিল। সদলবলে চলে গেল তারা। বাড়িটি যেহেতু নদীর কূলে ছিল সেহেতু ডাকাতদেরও বেগ পেতে হয়নি পালাতে। এ ঘটনার বছরখানেক পর সেই সুন্দরী কন্যাটি ফিরে এসেছিল একটি পুত্রসন্তান নিয়ে। ডাকাত সর্দার নাকি বলেছিল, ‘যা এবার বাপের বাড়ি! ফিরলে ফিরিস না ফিরলেও আপত্তি নেই।’ কিন্তু সুন্দরী কন্যা তখন নাকি আর থাকেনি। সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে সন্তানের সেই ডাকাত পিতার কাছেই ফিরে গিয়েছিল। এটা তার দাদির আমলের গল্প হলেও ফয়েজের জিদটাও সে আমলের রয়ে গেছে।
নয় নম্বর রুমটির চার মাসের ভাড়া বাকি পড়ছে। এ নিয়ে প্রতি মাসেই রহমত উল্লাহর ঝাড়া উত্তর ‘জসীম্যার ভাড়া লইয়া চিন্তা কইরেন না তো! হ্যায় ইচ্ছা করলে এক বছরেরটা এক লগে দেওনের ক্ষেমতা রাহে। খুন, জখম থেকে শুরু করে হেন কাজ নেই জসীম করেনি। তবু দিব্যি বাইরে ঘুরে বেড়ায়। শুধু এক-একটা খুনের ঘটনা ঘটার পর গরম গরম কয়দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকে। এবার এলাকায় পুলিশের ইনফর্মার খুন হয়েছে তাই জসীমের পালিয়ে থাকার পালাটাও দীর্ঘ হয়েছে, না হলে এসব তার জন্যে পানি-ভাত! সবাই জানে পুলিশের সদিচ্ছা থাকলে এমন দিনে-দুপুরে ঘুরে বেড়ানো আসামি ধরতে বেগ পাওয়ার কথা নয়। এবং এই ছাড়া থাকার জন্যে গেটের কাছে এসে অপুষ্ট শরীরের কোনো পুলিশ যারা কিছু বখরা ওখান থেকে পাবে, তারা, মৃদু হুমকিও দিয়ে যায়—‘জসীমে কিন্তুক এ সপ্তাহ স্যারের সঙ্গে দেহা করে নাই। কাজটা বালো অইতেছে না কিন্তু…।’
ভাড়া তোলার নির্দিষ্ট সময় ছাড়াও ইদানীং ফিরোজ হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়ে। হয়তো তার মায়ের নাম লেখা বাড়িটা ক্রমে তাকে গভীর আকর্ষণে বেঁধে ফেলতে চায়। তাছাড়া এখন আর ভাড়া এবং ভাড়াটিয়া নিয়ে তেমন একটি হাঙ্গামা হয় না। রহমত উল্লাহই রফা করছে। কে কী করে খায়, তার চেয়ে বড় কথা কার ঘরে কী আছে। কোন ঘর খালি হলেই নতুন করে কেউ আসার আগেই জিনিসের ফিরিস্তি শোনে রহমত উল্লাহ। ‘টিভি, ফ্যান এগুলান থাকলে বাড়া দুই-চাইর মাসের বাকি পড়লেও দুশ্চিন্তা করণ লাগে না, নইলে হঠাৎ ফুটলে কী করণ যাইব!’ রহমত উল্লাহ এভাবেই দূরদর্শিতা জাহির করে ফিরোজের কাছে বলে বলে।
বাঘের বাচ্চা বাঘ গেটটিতে ভেতরে বাইরে দু’দিক থেকেই ঘটির মতো দুটো তালা লাগানো থাকে। ফিরোজের মায়ের নামটি থেকে চোখ নামিয়ে পকেট গেটটিতে মাথা ঢোকাতেই দামি, চকচকে জুতোর একজোড়া পা দেখল, ভেতরে ঢুকে হাঁটি হাঁটি পা’র একটি কন্যাসন্তানের পিতা রগটচা জসীমের চোখের দিকে তাকাল ফিরোজ। কিন্তু ফিরোজের দৃষ্টি যেন স্থির করতে পারছে না লিকলিকে জসীমের বিদ্যুত প্রবাহিত চোখে। তবু কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে হয়। না হলে ও-ই মনে মনে বলবে— ‘শালা, বাড়িওয়ালারা ব্যাডা বয় পাইয়া পলাইছে!’
‘ক’মাসের ভাড়া জমে গেছে জসীম মিয়া… এভাবে টাকা জমালে চলে?’ এর বেশি আর মুখ চলল না ফিরোজের।
—হ। আপনে গো থেইকা আমাগো চিন্তা বেশি।
—কিন্তু চিন্তা দিয়ে তো কাজ হচ্ছে না। এই টাকা দিয়েই আমাদের চলতে হয়।
—আতে আইলেই দিয়া দিমু! বেশি কথা শোনাইয়েন না।
—বুকটা কেঁপে ওঠে ফিরোজের। তা জসীমকে বুঝতে না দেওয়ার জন্যেই, যেন সে একটুও ভয় পাচ্ছে না সেই ভানই নিখুঁত করে দেখাতে বলল, ‘কী করো তুমি?’
—করি একটা কিছু…, বলতে বলতে আর দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন মনে না করে, দ্রুত রাস্তার দিকে হেঁটে গেল জসীম। যেন ছাগলে তার বাপের জমির ধান খেয়ে ফেলেছে, এমনই তার ভোকাট্টা দৌড়ের ধরন।
অযথাই চুলোগুলো দপদপিয়ে জ্বলত। কারও তাতে একটু অনুশোচনা নেই। ফিরোজ কতদিন সবাইকে একত্র করে বুঝিয়েছে, ‘এভাবে গ্যাস অপচয় মারাত্মক অন্যায়। এটা সবার ক্ষতি! সবকিছুরই শেষ আছে। তাই এই গ্যাস শেষ হয়ে গেলে আপনাদের সন্তানদের দুর্গতির সীমা থাকবে না। তাছাড়া আগুন ছড়িয়ে বিপদও হতে পারে!’ কিন্তু কে শোনে কার কথা। রহমত উল্লাহ বাড়ি থাকলে ফিরোজের কৈফিয়তের জো পেয়ে সে-ই তুলকালাম বাঁধিয়ে দিত। কিন্তু রহমত উল্লাহর এ সময় থাকার কথাও নয়। ফিরোজ তার মতোই ফের পুরোনো উপদেশগুলো ঝালিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই জসীম ফিরোজকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। হাতের পিস্তল দ্রুত পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। ওটা না লুকালেও ফিরোজের কিছু করার নেই। বরং তার বুকে ধড়ফড় শব্দ শুরু হয়ে যায়, কিছুক্ষণ আগে এরই সঙ্গে স্বাভাবিক কথা বলেছে ভেবে।
ফিরোজ আরও দেখল জসীম একগাদা টাকা থেকে কোনোরকম গুনে তাকে দু’হাজার টাকা হতে ধরিয়ে ‘বাকিটা আগামী মাসে দিমুনে, যান!’ বলে, সম্পূর্ণ শরীরটি বেঁকিয়ে নিচু হয়ে বাড়ি ঢুকল। মেঘ না চাইতে জলের মতো এমন প্রাপ্তি খুব একটা ঘটে না। তাও আবার এমন বস্তির ভাড়া? সে তো করুণা মিশিয়ে ভিক্ষের মতো দিতে হয়। ফেরার পথে, অসময়ে দু’হাজার টাকা? বড় রাস্তার দিকে এগোতে এগোতে ক্রমশ কারও আহাজারি প্রকট হয়ে ওঠে ফিরোজের কানে। শোরগোল হিম হয়ে আসে বুকের কোথাও। একসময় মানুষের জটলায় নিজেকে সেঁধিয়ে সে দেখল এক বৃদ্ধ বুক চাপড়ে আহাজারি করছে— ‘কয়দিন ধইরা পোলাপান লইয়া না খাইয়া আছি। অসুখে পরছিলাম, বাড়িওয়ালা ঘর তালা দিয়া রাখছে। দশ হাজার টাকার রিকশাখানা চার হাজার টাকা বেইচ্চা আইবার লাগছিলাম… আল্লাগো…।’
ফিরোজ অবচেতনে নিজের পকেটটি খামচে সামনের দিকে হাঁটতে থাকে। রাস্তায় যানবাহনের বিকট শব্দ, মানুষের কোলাহল, কিন্তু কিছুই আর তার মাথায় ঢুকছে না। শুধু এগাতেই প্রতিটি পদক্ষেপে তার পা জড়িয়ে যায়। আষাঢ় শেষ হলো ক’দিন আগে মাত্র। শ্রাবণের অবিরাম বর্ষণ ছাড়াও উপচানো পানি গড়াগড়ি যাচ্ছে। অথচ বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে বোঝা যায় না উপশহরের এমন সয়লাব অবস্থা। গলি-ঘুপচি ছাপিয়ে পানি উঠে যাচ্ছে প্রতিটি বাড়ি। একটু রোদে, বৃষ্টির বিরতি ঘটায় আবার পানি কিছুটা কমে আসে বলে রক্ষে। তবে ভাদ্রের আগেই রক্ষে পাওয়ার সব বাঁধ ভেঙে যাবে, তাতে এলাকাবাসী অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে এ ক’বছরে। অপরিকল্পিতভাবে খাল বিলগুলো ভরাট হওয়ায় বৃষ্টির পানি জমে সহসা সরে যাওয়ার পথ পাচ্ছে না। বড় রাস্তাগুলোয়ই বৃষ্টি একটু ঘন হলে পানি থইথই করে।
‘আমিনা ভিলা’র শান বাঁধানো চৌহদ্দিতেও পায়ের গোড়ালি ডুবে যাচ্ছে। তার ভেতেরই হাঁটা-চলা। কাঁচা অনেক বাড়িতে এখনই ঘর-দুয়ারে পানি উঠে হাঁটু সমান। জীবনের সব হাহাকার-প্রত্যাশা ও আনন্দ ছাপিয়ে এখন শুধু পানিরই শব্দ। পানি ভেঙে এগুনোর শব্দ।
সামাদ মণ্ডলের হাঁফের টানটা বেড়েছে, আর ক্রমে পুষ্প গুটিয়ে নিয়েছে তার নিঃশ্বাসের শব্দ। এতটুকু হয়ে গেছে মেয়েটির মুখ। তার ওপর রোগা শরীর নিয়ে রোগীর সেবা-যত্ন।
রোগগ্রস্ত সামাদ মণ্ডল যখন নিজেই বিড়বিড় করে ছেলের নাম জপে। তার মঙ্গল-অমঙ্গল ভবিষ্যৎবাণী পড়তে থাকে। পুষ্প যতটা পারে তখন নিজেকে আরেকটু দূরে নিয়ে যায়। সেটা ওই গোড়ালি ভেজা পানি কেন প্রয়োজনে সমুদ্রেও নেমে পড়বে সে। লজ্জায় দ্বিধায় শতধা বিভক্ত তার সত্তাটি।
যখন একমাত্র ছেলেকে নিয়ে গ্রামে গেল, তখন তার খাবি খাওয়া অবস্থা। পুষ্প’র মা সম্পর্কে সামাদ মণ্ডলের চাচি। ঘরদোর ভাঙতে সাজাতে বরাবরই তার ডাক পড়ে। কাঁচা চুলোয় ভাত চাপিয়ে আগুন জ্বালানোর সাধ্য যখন বাপ বেটা কারও হয় না সামাদ মণ্ডল নিজেই গলা ছেড়ে তখনই কাশতে কাশতে ডেকে ওঠে, ‘বড় চাচিজান’ বলে। কাদা-মাটি মাখা হাত ধুয়ে, বা নিজের দাউ দাউ জ্বালানো চুলোয় বলক ওঠা ভাত বা সালুনের কড়াইয়ের পাশে কাউকে ডেকে বসিয়ে ছুটেছে মাত্র ক’কদমের পথ উত্তর বাড়িতে।
ঝুপঝুপ ক্ষয়ে পড়া ঘরখানি এতদিন ছিল গাছ-গাছালির নুয়ে পড়া ডালে ঠাসা। পাশে একটুখানি বাঁশের ছোপ অযত্নে আর বুনো লতাপাতার আক্রমণে তারও জীর্ণদশা। সামাদ মণ্ডল তার দুঃসম্পর্কের চাচার শেষ বয়সে নিকার স্ত্রী, জোয়ান চাচিটির ছায়া দেখেও বুঝি ভরসা পায়। দীর্ঘ গল্প জুড়ে জুড়ে চাচিকে ধরে রাখতে চায় নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য। চাচা শেষ বয়েসে বিপত্নীক হলে এতটুকু একটা মেয়েকে বিয়ে করে এনে ছেড়ে দিয়েছিলেন নিজের মোষের মতো একপাল ছেলে-মেয়ের মধ্যে। কতদিন ভাত রাঁধতে গিয়ে রোমেছা বিবি কাপড়ে আগুন লাগিয়ে নিয়েছে। ভাতের ফেন ঝাড়তে তো পারেইনি বরং অসহ্য বঞ্চনায় কাতর হয়েছে রাতের পর রাত। তার কোমল শরীরে দু’মিনিটের পাশবিক তাণ্ডব নারী জন্মের ওপর ঘেন্না ধরানোর অবকাশ পর্যন্ত আর পৌঁছায়নি।
মেয়ে পুষ্পের জন্মের আগেই মারা গেছে তার স্বামী আহাদ মণ্ডল। রোমেছা বিবি কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার পেট আর নিতম্বের গড়নের পরিবর্তন দেখে বাড়ির বর্ষীয়সীরা আঙুলের কর গুনতে লেগে গেল। ক’মাসের ভ্রূণে পোয়াতির পেটের কতটা বাড়-বাড়ন্ত হতে পারে তা হিসাব মেলাতে। বিধবা রোমেছা বিবিকে ফিরিয়ে নেওয়ার কেউ ছিল না। তাছাড়া টানাটানির সংসারে তখনো সে তার স্বামীর ছেলে-মেয়েদের কাছে অপরিহার্যই ছিল। চারটি ছেলে, দু’টি মেয়ে তারা।
বাপের তিন বিঘে জমি। বাড়ির কাছে তরিতরকারির আবাদ। একটা দুধের গাভী, হালের দু’টো বলদ। বড় ছেলে দু’টির দিন-মজুরির বয়স হয়েছে আগেই। এদের মধ্যে ভালোয়-মন্দয় সেঁটে থেকে চারটি ভাত ফুটিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনে রোমেছা বিবি ওদের মা হয়েই থেকে গেল। পুষ্পের যখন হাঁটি হাঁটি পা পা অবস্থা তখনই পরপর বড় দু’টি ছেলে বিয়ে করল। বউয়েরা যে যার মতো হাতে হাতে সংসার ভাগ করে নিল ক’দিনের মধ্যে। বাঘের মতো ছেলেদের সম্মুখে রোমেছা বিবি তাদের বিয়ের আগেও মুখ খুলতেও সাহস পায়নি। এখনো পায় না। ছোট ছেলে দু’টো কামলা খেটে যা পেত, নিজেও এ-বাড়ি ও-বাড়ি টুকটাক কাজ করে টান সামালে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। একসময় সতীনের মেয়েরা পরের বাড়ির বউ হয়ে ঘর খালি করে চলে গেল। ছোট ছেলে দু’টোও ভালো ঘরের মেয়েদের বউ করে এনেছে। সবাই একত্র হলে বাড়িটা গমগম করে।
রোমেছা বিবি আজো ছেলে-মেয়ে-বউ কারও অভাজন হয়নি। পৃথিবীতে খুব কম মানুষই থাকে এমন, যার মন রেখে জীবন কাটাতে পারে। তবু চার ছেলের চার হাঁড়ি ভাগ হয়ে যাওয়ায় তারও গড়াগড়ি দশা হলো। এখন আর কারও ভাত ফুটিয়ে দেওয়ার জন্য তার ডাক পড়ে না। যখন শুধু চার ছেলের কারও ঘরে যদি হঠাৎ কেউ এসে পড়ে, অথবা কোনো বউয়ের বাপের বাড়ি থেকে হঠাৎ দু-চারজন এলে মোরগের ঢ্যাঙা বাচ্চাটা দৌড়ে ধরতে ধরতে সময় পার হলেই শুধু পুষ্পের মায়ের ডাক পড়ে। তাড়াতাড়ি বাটাকোটায় হাত বাড়াতে।
সেই সুবাদে আধপেটা খাওয়ানো বা প্লেটে করে ছেলেমেয়েকে দিয়ে তার বড় ছেলের জুড়ে দেওয়া ঝুল বারান্দায় পাতা সংসারে পাঠানো। আর তা ঢেলে রাখতে রাখতে রোমেছা বিবি বোঝে, কত কম ভাতে কত বেশি উঁচুর কসরত যায় বউদের ওপর। বউয়েরা তাকে সামনাসামনি আম্মা বলে ডাকলেও এমনিতে পুষ্পের মা বলে ডাকে। স্বামীর বড় ছেলে দু’টো তার থেকে বয়সে বড় হলেও এক সময় ক্ষুধার টানেই বোধহয় তাকে বাধ্য হয়েছিল মা বলে ডাকত। কিন্তু এখন তাদেরও তাদের বউদের মতো ডাক-খোঁজ নেওয়া।
পুষ্পকে ডেকে রোমেছা বিবি কাছে পায় না। সে এ-বাড়ি ও-বাড়ির মেয়েদের সাথে স্কুলে যায়। আহাদ মণ্ডলের বংশধর অশিক্ষায় ভুগলেও তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী শিক্ষিত। অবস্থাপন্ন কেউ কেউ। পুষ্প ভিড়েছিল তাদের সঙ্গে। নিজের থেকে বছর তিনেকের ছোট ভাইজি তার ভীষণ সঙ্গী। মেয়ের লেখাপড়া শেখার টান সামলাতে রোমেছা বিবির সারাক্ষণ প্রাণ ওষ্ঠাগত। তরি-তরকারি, দু-একটা ডিম জুটলে সব বিক্রি করে দেয় মেয়ের বই খাতা কিনতে। লুকিয়ে লুকিয়ে আরেকটু দূরে গিয়ে মানুষের মুড়িভাজা, চিড়ে কোটার কাজটিও করে। ছেলেরা জানতে পারলে বাপের সম্মানহানির দায়ে কেঁচে মারবে, সে ভয়ও আছে রোমেছা বিবির। পুষ্প’র বড় ভাই তমিজ মণ্ডলের বড় মেয়ে নূরীর সঙ্গে ওর গলায় গলায় ভাব। পুষ্প’র মেট্রিক পরীক্ষা ছ’মাস পরে। আর নূরী নবম শ্রেণির ছাত্রী।
পুষ্প স্কুল থেকে ছুটে এসে, এদিক-ওদিক থেকে ছুটে এসে মাকে না পেয়ে ছোটে সামাদ মণ্ডলের বাড়িতে। এইভাবে যখন-তখন যাওয়া আসা সামাদ মণ্ডলের ভেঙে সাজানো নতুন বাড়িতে। ঘনিষ্ঠতাও ক্রমে বাড়তে থাকে মতিয়ারের সঙ্গে। গ্রাজুয়েট মতিয়ার পুষ্প’র মা’র প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েই স্বেচ্ছায় দায়িত্ব নিল পুষ্পকে অংকগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার। কিন্তু পুষ্প’র অপটুত্ব সব সাবজেক্টেই। পুষ্প বারবার সামাদ মণ্ডলের মেয়েশূন্য ভিটেয় যাওয়া-আসা করলে মানায় না। তাই বুঝে মতিয়ার নিজেই ঝুল বারান্দায় পাতানো মা-মেয়ের তালপাতার সংসারে এসে তার পড়াগুলো বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু মতিয়ারের উপর চোখ পড়ে নূরীর মায়ের। নূরীর মা নূরীকে একরকম লেলিয়েই দেয় মতিয়ারের পেছনে। প্রায়ই সে মতিয়ারকে ডেকে বলে ‘নূরীকে ওর মামার বাড়ি এট্টু বেড়াইয়া আনো। বেইল যাওনের আগে আবার লইয়াইয়ো।’ কিন্তু বেলা পড়ার যত পরে ফেরে মতিয়ার ততই খুশি হয় নূরীর মা। ভালো কিছু রেঁধেও সে মতিয়ারকে ডেকে আগে খাওয়ায়।
ক’দিন না যেতেই পুষ্প টের পায় ওর দিকে মতিয়ারের আগের মতো আগ্রহ নেই। এখন নূরীকে নিয়ে মেতে আছে সে। তাতেই কী, সে তো কোনোদিন ওকে নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি স্বপ্ন দেখেনি। বরং সেধে গায়ে পড়ে ওই তাকে অংক শেখাতে চেয়েছে। রোমেছা বিবি বারবার মেয়েকে মতিয়ারের সম্পর্কে বলছে, সম্পর্কি ফুপু-ভাগনি অইলেও রিস্তাডা অইতে পারত মতিয়ারের লগে। কারণ ওরা আমাগো দূরের সর্ম্পকির। কিন্তুক মা’রে, ওই দিক আর নজর দিবার যাইও না। দুর্নামে ঢি ঢি কইয়া দিবো তোমার বড় বাউজে। বিষ খাইয়া বিষ অজম কইরাই তো ইজ্জত রাখছি। নইলে দৌড়াইয়া বাইর করত আমারে। সয়-সম্পত্তি কীই-বা তোমার বাপের আছিল… আর একপাল পোলাপানের মইদ্যে কীই-বা লোভ করুম। এ যেন মাইনষের পাহারায় থাহনের লাইগাই মাইয়ামানইষের জীবন।
নাইলে একে একে বউ লইয়া আইল আর আবার জায়গা অইল তালপাতার ছাউনির বারান্দাটুকু! হগল জায়গাই এক রহম। নইলে বাপের বাড়ি গেলে হ্যারাও কি আর আমারে এগোরতন বালো রাখতো? কই, ভাইয়েরা তো কনুদিন খবর নিল না এট্টুহানি বইনডারে নরকে পাঠাইছি, দেইহা আসি এতদিনে কেমুন আছে? মা’রে মনেরে বান্দো! পোড়াকপালির গরে জন্ম নিয়া এরতন বালো কী আশা করবা!’ পুষ্প সেদিন মায়ের কথা শুনে লজ্জায়-ঘেন্নায় কুঁচকে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল। আজও স্বপ্নভাঙা সেই দুপুর বেলাটা মনে হলে তার গায়ে কাঁটা দেয়।
তখন থেকে উঠতে-বসতে মায়ের মুখে শুধু সাতকাহন শুনতেই থাকে পুষ্প। যা সে আগেই অনেকখানি জানত। নূরী এহন আর তার ধারে-কাছে থাকে না। থাকে আড়ালে আবডালে। স্কুলে যাওয়াও তার বন্ধ। মতিয়ারকে সারাদিন ঘরে এনে নূরীর মা নূরীকে দিয়ে নতুন জামাইয়ের মতন আটকে রাখে। সারাদিন বাড়িতে এ নিয়ে গুজুরগুজুর ফুসুরফুসুর। মতিয়ারকে যেন ছেড়ে দিলেই হাতছাড়া হয়ে যাবে। বাজার থেকে কেনা মোরগ পলো দিয়ে আটকে রাখার মতো অবস্থা তখন মতিয়ারের।
ক’দিন পরই পুষ্পের পরীক্ষা শুরু। কিন্তু বড় ভাই তার আগেই সামাদ মণ্ডলের সঙ্গে কথা পাকাপাকি করে তার সঙ্গে পুষ্পের বিয়ের আয়োজন করে বসল। কথাগুলো কানে আসতেই বাড়ি কাঁপিয়ে আর্তনাদ করে উঠল রোমেছা বিবি। আবার তার জীবনের পুনরাবৃত্তি তার মেয়ের জীবনে ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু শত আহাজারি করেও সে নিবৃত্ত করতে পারল না। নিজের মেয়ের জন্যে পথ পরিষ্কার করে রাখল তমিজ। এটা অনেকে বুঝলেও এগিয়ে আর এল না কেউ-ই। গ্রামের দশজনের মনোভাব ‘যার গরু সে যেদিকে খুশি জবাই করুক তাতে আমাগো কী?’ আর এসবই যে হচ্ছে নূরীর মায়ের চাপে তাও পুষ্প আর ওর মা বুঝেছে। কারণ অবস্থা এমন কিছু হয়েছে মতিয়ারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে না হলে সমাজে টেকা দায় হবে ওদের। পুষ্পও বোবা বনে ছিল। কোনো বাদানুবাদ করার তেজটুকু কে যেন তার কেড়ে নিয়ে নিয়তির হাতে সঁপে দিয়েছিল।
কচি মেয়েটা সামাদ মণ্ডলের বউ হয়ে আসার পর ছেলেটাও আর ঘরে ঢোকেনি। তাহলে কি সেও এটা চায়নি? তাহলে কী চেয়েছিল সে? না পুষ্প’র আর কোনো প্রশ্ন কারও কাছে নেই। সামাদ মণ্ডল বারবার বলেছে ‘পরীক্ষাডা দেও তুমি। তোমার জীবনডা পইড়া রইছে। আসলে আমি বিয়াডা করবার চাই নাই, কিন্তু তোমার বাইয়েরা সবটি মিল্লা কী বয় যে আমারে দেহাইলো! মাইরা ফালাইবো কইছিল, তা ফালাইলে ফালাইতো। কিন্তু মারণের তো তোমারে বিয়েডা দেওনেরই তাগো বেশি দরকার আছিল। আসল কথা তাগো মাইয়াডা মতিয়ারের লগে দিবো বইল্লা পথ পরিষ্কার করল। তা ও করলে দিউগগ্যা। কিন্তু এই অন্যায় কামডা আমারে দিয়া করাইলো ক্যান? তুমি তো জানোই ওর মা মরছে কবে, জীবনডা আমার এমনিই শ্যাষ করলাম। ইচ্ছা অয় নাই সেই মানুষডার জায়গায় আর কেওরে আনি! না-না এড় বড় অন্যায় ঠেকতাছে আমার কাছে। তুমি তোমার পথ তৈয়ার কইলা লও! তাতে আমার সাহায্যই পাইবা, আমি তোমারে আটকামু না।
জড়সড় পুষ্প নিরুত্তর। পুষ্প দোষ দেয় না কারওরই। সামাদ মণ্ডলের কথার কোনো উত্তরও দেয় না। অনাহারে অর্ধাহারে আর অমানবিক খাটা-খাটুনির বিধ্বস্ত শরীরটা টানতে টানতে মাত্র চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশের রোমেছা বিবি যখন তার আঠারো-উনিশ বছরের কন্যাটির সামনে আসে তখন তার চোখে আষাঢ় মাসের বর্ষণের অবস্থা। আর মেয়েটি তার নির্বিকার। কোনো অভিযোগ অনুতাপের ধার তার চোখে নেই। মাকেও সে কাঁদতে মানা করে না। রোমেছা বিবির কান্নার তোড় যত বাড়ে সামাদ মণ্ডল ততই নিজেকে গোটাতে গোটাতে বাড়ির দক্ষিণ পাশে হাঁটুমুড়ে বসে মিইয়ে থাকে। একসময় অবশ্য স্রোতের মতো কষ্টের তোড়ও কমে আসে। রোমেছা বিবি ও মেয়ের কাছে আর যখন তখন আসে না। এটাও হয়তো তার মৃত স্বামীর ছেলেদের চোটপাটে। ব্যাপারটা সবার কাছে গা সওয়া করে তুলছে অল্প সময়ের পলিই। আর ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ডুবে থাকা মানুষের একই বিষয় সুরাহার আগ্রহ-কৌতূহল থাকে না বেশিদিন।
যে মাধ্যমটিকে অবলম্বন করে বিদেশে যাওয়ার কথা ছিল হঠাৎ তাদের চিঠি পেয়ে ঢাকায় এসে আর ফিরে যায়নি মতিয়ার। বাপের টাকাগুলো আগেই ঢাকায় এ্যাকাউন্ট করে ওর নামে রাখা ছিল। বাপের সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার ধারও সে ধারল না। চলে গেল। আর হায় হায় রব উঠল নূরীর মা-বাবার। কলংকে গ্রাম ভাসতে লাগল প্রায়। শেষে টোটকা চিকিৎসায় গুণে সপ্তাহ না ঘুরতেই লাশ হলো মেয়েটি। শোক-তাপ উপচেও তমিজ মণ্ডল আর তার বউয়ের চোখে মুখে ছিল ভিন্ন উদ্বেগ। মেয়ে ডায়রিয়ায় মরে গেছে বললেও তার কাফন ভাসছিল রক্তে।
বছর না ঘুরতেই সামাদ মণ্ডলের হাত একেবারে শূন্য। শরীরেও জোর নেই কাজকর্ম কিছু করার। ছেলের কৃপার আশার থেকে তার প্রহর কাটে। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিদ্যেটুকু নিয়ে পুষ্প বাড়িতেই গড়ে তোলে পাঠশালা। গ্রামে নগদ টাকার মুখ দেখা সোজা কথা নয়। পরিশ্রমই সার। শেষে কারও কারও পরামর্শ শুনে মনটা তৈরি করে ঢাকায় আসার। তাছাড়া ও গ্রাম ছাড়তে তার মনটা তো কবেই উচাটন হয়েছিল। অথর্ব স্বামীর মতামত কী? তবু বিষয়টি আলোচনা করতে করতে একদিন নেমে এসেছিল ‘আমিনা ভিলা’কে উদ্দেশ্যে করে জ্ঞাতি ভাই আহাদ মণ্ডলের ছায়ায়।
ভাদ্র মাস আসার আগেই পানি বেড়ে ঘরের সামনে হাঁটুসমান হয়ে গেল। যার যার দরজায় নিজ নিজ উদ্যোগে ইট গাঁথে সবাই। প্রায় প্রতিদিন একসারি গাঁথতে হয়। দুর্দশার অন্ত নেই ভাড়াটিয়াদের। চুলোগুলো রহমত উল্লাহ মিস্ত্রি ডেকে বুকসমান উঁচু করে দিয়েছে, পানির কলও। কিন্তু পায়খানার অবস্থা শোচনীয়। অনেকে তাই চলেই গেছে এখানে ওখানে, সুজনের মাকে তার তিন বাচ্চাসহ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ফরিদপুরে। ওদের এলাকায়। পুষ্প’র একেবারে পাশের ঘর তাদের। রাতে পুষ্পের এমনিতেই ঘুম আসে দেরিতে। তার ওপর সামাদ মণ্ডল বেশি অসুস্থ। স্যাঁতস্যাঁতে অবস্থার কারণে তার অবস্থার অবনতিই ঘটছে শুধু। বাইরের নিস্তব্ধ অবস্থা। আবার কার হাঁটার শব্দ কানে আসে। নিঃশ্বাসের শব্দও বুঝিবা। পুষ্প ভয়ে ভয়ে দরজাটা এতটুকু ফাঁক করে দেখল একঠায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে। সে অনুমান করেই ডাক দিল, সুজনের নানি খালা না? কিন্তু কোনো প্রতি উত্তর পেল না। অন্ধকার তত নয়। মধ্যরাতে ঝুলে থাকা আধখানা চাঁদের আলো একটা একটা মানুষকে দশ-বারো হাত দূর থেকে চেনার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু সুজনের নানির মূর্তিটি অনড়। দু’হাতে শাড়ি গুটিয়ে হাঁটু পানিতে দাঁড়ানো সে। পুষ্প আর চোখ পাততে পারে না, তার হাত-পা হিম হয়ে আসে। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খায়। নিচে পাতা ভিজে ওঠা বিছানা ছেড়ে দ্রুত সামাদ মণ্ডলের পায়ের কাছে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ে। ঘুম আসে কখন তা সে জানে না।
ভোর রাতে জসীমের হাঁক-ডাকে বাড়ি শুদ্ধ জেগে ওঠে। বহুবার বহু রকম সময়ে বহু কারণে অবশ্য সে বাড়ি মাথায় তুলেছে। কিন্তু এবার তা একেবারে অন্যরকম। ভোর রাতে দরজায় দাঁড়িয়ে প্রসাব করতে করতে তার চোখ যায় সুজনদের ঘরের সামনে। ওখানে কাউকে অমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে নেমে এসে মানুষটিকে থাবা দিয়ে ধরে ফেলল। আর তাতেই সুজনের নানি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। হয়তো সুজনের নানি তার জীবনের ঘটনাটি কাউকেই বলত না। হজম করে যেত। কিন্তু জসীমের ধমকে সব কথা বের হয়ে গেল পেট থেকে। ‘রাইতে জামাই শুইছে ঘরে খাডে, আর আমি পাশে ভাঙা চকিটাতে শুইছি। এমনি শরমে ঘুম আহে না। মাইয়ার জামাইয়ের লগে এক ঘরে কেমনে শুই? আবার ভাবি জামাই আর পুলাতে এক ঐ কতা! মাইয়াডাও নাতিগুলানরে লইয়া পানির ডরে মাত্র কাইল দুইফরে দ্যাশে গেল। আমারে আমার মাইয়াই কইলো, ‘তুমি আইয়া এইহানে থাহো। সুজনের বাপেকে কে রাইন্দা বাইড়া দিবো…।’
‘আসল কথা ক বেডি!’ জসীম আচমকা প্রচণ্ড ধমক দিল সুজনের নানিকে। ‘হ, তারপর জামাই চকিরতন নাইম্যা আইস্যা আমারে আত ধইরা টান দিল। আর ফিসফিসাইয়া কইলো, ‘আমার লগে আইয়া হোন! নাইলে আপনের মাইয়ারে তালাক দিমু।’ ডরে আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুইল্যা তয় বাইরে আইয়া দাঁড়াইয়া রইলাম… দোয়া পড়তেছিলাম… আজানডা দিলেই বাবছিলাম বাড়িরতন বাইরাইয়া যামু…।’
জসীম এক লাফে সুজনদের ঘরে ঢুকল। কিন্তু ঘর খালি। হট্টগোল শুনে টেম্পু চালক আনোয়ার ভেগে গেছে। হাঁটুসমান পানিতে ছপছপ শব্দ তুলে জসীম চকচকে ছুরিখানা বাটের ভীতর ঢুকাতে ঢুকাতে দাঁতে দাঁত চেপে বলতে লাগল, ‘উজুরিডা আইজই আতে দরাইয়া দিতাম শালার পুতেরে। এইডার বিচার না অইলে আমি গর ভাড়া দিতাম না। অই রহমইত্যা তর বাড়িওয়ালারে ডাইক্কা এইডার বিচার কর! নাইলে দেহিস, খবর কইরা দিমুনে।’
বাড়িওয়ালা পানি ভেঙে খবর নিতে আসার আগেই দু’দিনের ভেতর সুজনের মা ছেলেমেয়ে তিনটিকে নিয়ে চলে আসে। সুজনের নানিকে জসীম বলে দিয়েছে, ‘এইডার বিচার না অওন পর্যন্ত বেডি তুমি বাড়িরতন লড়বা না। তাইলে তোমারে খারাপি কইরা ছাড়ুম।’ সুজনের নানি তাই শরমে নেতানো অবস্থায় রয়েই গেল ‘আমিনা ভিলা’য়। সুজনের মা পানি ভেঙে আমিনা ভিলায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ভিড় করল তাদের দরজায়। সবার শাড়ি-লুঙ্গি হাঁটুর উপর তোলা। কারও তারও উপরে। তবু সুজনের মা এই দুঃসংবাদ পেয়েই এসেছে মনে হয়। সে ফ্যাকাসে চোখে মুখে, দড়িতে বাঁধা কাঠের তাক থেকে কোরআন শরীফ টেনে নিয়ে তার মায়ের মাথায় তুলে দিয়ে বলল, ‘সত্যি কইরা ক’ মা। সুজনের বাপে তোরে কিছু করছেনি!’
সুজনের নানি কোঁকাতে কোঁকাতে বলল, ‘তুই আমার প্যাডের মাইয়া, তোর সোয়ামি আমারে কিছু করলে আমি বিষ খাইয়া মরতাম না লো! এহনো এই জীবন রাখতাম।’ সুজনের মা তার মায়ের কথায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও উদগ্রীব হয়ে রইলো জটলাবাঁধা মানুষগুলো। তারা যা ভাবছে তাই সত্যি করে তুলতে চাইছে, নানান প্রোপাগান্ডায়।
বন্যায় হিম হয়ে আসা রক্ত তাতে যদি একটু চনমনে হয়। জসীম যত মারমুখী হয়ে উঠেছে সুজনের বাবা পালিয়েছে তত দূর। ঘটনাটি ফিরোজ কানে শোনামাত্র রহমত উল্লাহকে বলে দিয়েছে ‘এসবের বিচার করতে আমাকে ডাকবেন তো আপনি আছেন কেন? কিন্তু জসীমের চাপেই রহমত উল্লাহ ফিরোজকে হাজির করতে ব্যস্ত। আর জসীম চাইছে বাড়িওয়ালায় দেহুক অঘটনের বিচার বাড়িওয়ালার করণের ক্ষ্যামতা নেই, কিন্তু তার আছে। সে ইচ্ছে করলে বাড়িওয়ালার এই ব্যর্থতার শাস্তি হিসেবে তাকে বাড়ি ভাড়া না দিয়েই চলে যেতে পারে। আবার বিনে ভাড়ায়ও থেকে যেতে পারে ইচ্ছেমতো। কিন্তু যা হয় হোক, বিষয়টি নিয়ে ফিরোজ মাথাই ঘামাল না। সে রহমত উল্লাহকে বলে, ‘আপনি সামাল দ্যান, এসব শোনা কি আমার কাজ? জসীম মাস্তানি শুরু করেছে এখন? তখনই হাতেনাতে ধরে আছাড় মারল না কেন? এসবের বিচার ঠাণ্ডা মাথায় হয় না।’
পানিরও বাড়াবাড়ি অবস্থা। তার ওপর অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝরছে। রহমত উল্লাহ প্রতি দরজায় হুংকার দিয়ে যাচ্ছে— উডানে পানি বইল্লা কিন্তু বাড়া দেরিতে দেওন চলব না। পউরকা দশ তারিখ মনে যেনি থাহে।’ কিন্তু জসীমের এক কথা— ‘তর বাড়িওয়ালা নিজে আইয়া অই নফরমানির বিচার করব, তারপর আমি বাড়া দিমু, নইলে একপয়সাও পাইব না। কইস গিয়া।’
—ছয় মাসে আবার ছয় হাজার জমাইছে জসীম্যা, রহমত উল্লাহ বুঝতে পারছে ভাড়া না দিয়া কাডনের অজুহাত। তাও যদি ভালায় ভালায় নামে। কিন্তু বাড়িওয়ালার পুতেরে কই কেমনে?’ নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে ফিরোজকে তার ছোট ধারণা দিতে ইচ্ছে করে না। সে তাই হাল ছাড়ে না। বারবার একই কথা শুনতে শুনতে একবার খেঁকিয়ে ওঠে— ‘ওই জসীম্যা, ওই! তোরা কে কী করবি, আর বাড়িওয়ালা পোলা আইয়া কি তোগো নুনু ধইরা বইয়া থাকবোনি!’
—মুখ সামলাইয়া কথা ক শালার পুত। বাড়ি ভাড়া দিলে সব খবরই রাহন লাগে। বাড়িতে আকাম কুকাম অইবো আর দূরে বইয়া বাড়া খাইবো, এইডা অইবো না।
—তোর বালা না লাগলে তুই নাইম্যা যা।
—হ যামু, তয় টাকাপয়সা যা পাবি, দিমু না।
—দেহি তুই না দিয়া নামোস কেমনে…।
রহমত উল্লাহকে হাত ধরে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যায় দু-চারজন মহিলা কিন্তু জসীমকে নিবৃত্ত করার সাহস কেউই রাখে না। একটা রক্তারক্তির বিপজ্জনক আভাস সবার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে।
ওদিকে সুজনের মা আর নানি মিলে ঘরের খুচরো জিনিসপত্র যা ছিল, নিয়ে কখন চলে গেছে দু’দিনে কেউ টের পায়নি। খবর পেয়ে রহমত উল্লাহ ছুটে এসে দেখল একটি খাট আর একটি টেবিল পড়ে আছে। সস্তা দরের খাট। তবে নতুন। টেবিলখানাও টেকসই। দুই মাসের ভাড়া উঠবো না এটায়। দুইটা মিল্লা হাজার দেড়েক অইবো। ভাবতে ভাবতে তার মাথায় আকাশ ভেঙে না পড়লেও বিপদ ঝুলে থাকে। এত লোকসান! ‘এগুলান কে কিনবো!’ হাঁক ছাড়ে রহমত উল্লাহ। বাড়ির সবাই এসে তাতে লোভাতুর দৃষ্টি বুলাতে থাকে। সাধ আছে সবার, কিন্তু সাধ্য নেই এদের কারওর। এই সাধ সাধ্য একত্র করতে রহমত উল্লাহর প্রাণ ওষ্ঠাগত। আরও এক রুমে একজন বিয়ে করে নতুন বউ নিয়ে উঠেছিল। দু’মাস না যেতেই স্বামী পলাতক। বউ না খেয়ে মরে। অবস্থা বুজে রহমত উল্লাহ তাড়িয়েছে মেয়েটিকে। তারপর নতুন মিটসেফ আর নতুন ফ্যানখানা বিক্রি করে রহমতুল্লা ফিরোজকে দু’মাসের ভাড়া বুঝিয়ে দিয়েছে। মাসের পনেরোও নয়, দশও নয়, একেবারে প্রথম দিন ফিরোজের হাতে টাকাগুলো বুঝিয়ে দিতে দিতে রহমত উল্লাহ বলছিল ‘কী লোকসানতন বাঁচাইয়া দিলাম! আপনে অইলে পারতেন না। বাপের ব্যবসা লাটে উডাইতেন।’
‘কী রকম!’
চমকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল ফিরোজ। ওই ঘরে এক নতুন জামাই-বউ আইয়া উডছিল। কয় মাস পোচপাচে আছিল। সপ্তাহখানেক দইরা ব্যাডারে দেখি না, মাইয়াডাও কান্দে। খাওনও জোডে না। শুনতে পাইয়া জিগাইলাম কাবিন আছে? কইলো, ‘না’ খালি হুজুর ডাইকা কলমা পড়াইয়া দিছে দুলাভাই।’ জিগাইলাম প্যাডের বাচ্চা কয় মাস। কইলো ‘চাইর মাস’ হুইন্না লগে লগে নামাইছি…।’ রহমত উল্লাহর কথা শেষ না হতেই ফিরোজ উৎকণ্ঠিত হয়ে জানতে চাইলে, মেয়েটা কোথায় গেল? অবশ্য টাকাটা সে আগেই ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিয়েছে।
—মাইয়্যাডা কই গেল সেই হিসাব রাহনের দায়িত্ব তো আমার না! আমার কাম অইলো আপনের টেকা তুইল্লা, বুঝাইয়া দেওন। ফিরোজের কণ্ঠ কেমন আমতা আমতা লাগছে তার নিজের কাছেই। আরও কিছু কথা বলার থাকলেও ওই মুহূর্তে সে চুপ করে নিজের চরিত্রের স্ববিরোধী দুর্বলতাটুকু প্রকাশিত হতে দিল না।
তিন বেলা চারটে খাবার আর বাসা ভাড়া যোগাতে ছাত্রছাত্রী নিয়ে পুষ্প সারাক্ষণ ব্যস্ত। তাছাড়া ওটাই তার কাছে ভালো লাগে, এভাবে এদের মধ্যে জীবনটা যেন কেটে যায়, তাই চায় সে! সামাদ মণ্ডল ঘর থেকে বেরোতে পারে না। তারও উসখুস অবস্থা। নাহলে পানি একটু কমতেই অসুস্থ শরীর নিয়ে সেও সটকে পড়ে। যতক্ষণ পারে দূরে দূরে কাটিয়ে দেয় ঘর ছেড়ে। কোলাহল ছেড়ে। দু’বছরের বিবাহিত অথচ এখনো কুমারী স্ত্রী ছেড়ে…
পাশের বাড়ির একজনের চিৎকার কান্নাকাটি শুনে এ বাড়ির সবাই হুড়হুড় করে দৌড়ে যায়। এরকম যাওয়া-আসা ওদের প্রায় প্রতিদিনের। এ বাড়ির বেলালের মা ডালুমালু চোখে এর মধ্যে খবর এনেছে— নান্টুরি ওয়ার মা ধরতি পারলি জান কাইড়ে নেবে না! কেউ কেউ সমস্বরে কারণ জানতে চাইল, বেলালের মা বলল, পোলাডা বাজারে মিস্ত্রির কাম কইরে বালোই পয়সা পায়। কিন্তুক কাম-কাইজের দারে কাছে নাই, ওইটুকু পোলা খালি জুয়া খেলবি। এট্টা টেকা ওর মারে দেয় না। সিয়ানা মাইয়েডাও কীসব কইরে বেড়ায়! মার কতা কেউ বাবে না। বাপটা পইড়ে রইছে আরেকখান হাঙ্গা…।’
বেলালের মা’র বয়ান শেষ হওয়ার আগেই নান্টু দৌড়াতে দৌড়াতে চিৎকার করে তার মা’র উদ্দেশ্যে বলে যেতে লাগল, মাগী তুই ম্যাছের ব্যাডাগো লগে কী করছোচ, তর কাছে বাত চাইতে গিয়া বেড়ার ফুড়া দিয়া আমি সব দেখছি! দাড়া মাগী বাবারে কইয়্যা লই!
—জাউরার পোলা, কবেই তগর বাপ তগরে ফ্যালাইয়া গ্যাছে। জানডারে মাডি কইরা তগরে আমি বাঁচাইয়া রাখছি, তোগো মোখতন এই কতা শোনোনের লাইগ্যা? তোর জান আমি আগে শ্যাষ কইরা পরে আমি মরুম…। তরকারি কাটাকুটিতে ব্যস্ত ভরা দুপুরে আরেকজন। তার সামনে থেকে দা তুলে এনে নান্টুর মা নান্টুকে উন্মাদের মতো তেড়ে যেতেই, সাহস করে ঠেকিয়ে দিল আরেকজন পুরুষমানুষ। পুরুষমানুষ হলেও সে সমবেদনা ঝাড়ল কতক্ষণ— ‘কী করবা বইন, প্যাডের পোলাপানেই মার দুঃখ বোজে না আর মাইনষে কী বোজবো? মা ক্যামতে বাঁচাইয়া রাহে, মাঐ জানে! আমরা তো দ্যাখতাছি। বেডায় বারো জাগায় হাঙা করে, আবার আলগা মাইয়া মানুষ লইয়া গোরে। পোলা-মাইয়া দুইডের দিকি খেয়ালও হরে না। আর সেই পোলায় তোমারে বাপের বয় দেহায়!’
চারদিকের হিজিবিজি খবর পুষ্প রাখে না। তবু চোখের পাশ দিয়ে গড়িয়ে যায় কত ঘটনা! মায়ের মুখখানা মনে হলে বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। সামাদ মণ্ডলকে ক’দিন হলো তার ছেলে মতিয়ার বিদেশ থেকে ফিরে এসে নিয়ে গেছে। এ বাসা খুঁজে পেতে তার নাকি অনেক কষ্ট হয়েছিল। গ্রামে ঢোকার উপায় তার নেই, খুন হয়ে যাবে পুষ্প’র ভাইদের হাতে। সে গ্রামের একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে এখানকার ঠিকানা পেয়েছিল। মাসখানেক আগে সে ফিরে এসেছে। মিরপুরে দু’রুমের একটা বাসাও নিয়েছে। মতিয়ার দুপুর বেলা এসেই বাপকে নেয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। আর সামাদ মণ্ডলের তো তখন দম বন্ধ হয়ে মরণ দশা ছেলেকে দেখামাত্র। তার সেই জ্ঞাতি ভাই আজিজ মণ্ডল আর তার স্ত্রী ছুটে এসে সেবা-শুশ্রূষায় এ যাত্রাও ঠেকিয়ে রেখেছে। এখন যে কোনো ধরনের ধকল তার জন্য বিপদ। শরীরের জীর্ণ দশা দেখে তখনই মতিয়ার বাপকে তুলে নিয়েছিল। না হলে কী হতো কে জানে!
শফি মিয়া এসেছিল বছরখানেক আগে। কিন্তু মজুরের কাজ করে যা পেত তাতে ওর মনে হয়েছিল, কথা তো একই। শেষে বাড়ির পাশের, গ্রাম সম্পর্কের চাচা মোতালেব মিয়ার কাছে এসে পরামর্শ চাইল, ‘এইখানতন টাকা রোজগার কইরা তারপর দ্যাশে পাডামু, আর ওরাও তো চাইল-ডাইল কিইন্নাই খাইবো। নিজের বাপে তো এক কাডা জাগা-জমি রাইখ্যা যায় নাই, যেইহানে পোলা দুইডা দাঁড়াবো। দ্যাশে ফ্যালাইয়্যা রাহনতন ওগোরে নিজের কাছেই আইন্না রাহি। তুমি কী কও চাচা?’
মোতালেব মিয়া কাঠমিস্ত্রি। পঞ্চাশ পেরোনো বয়স। দীর্ঘদিন ধরে সপরিবারে ঢাকা থাকে। ‘আমিনা ভিলা’র কাঠের কাজ সেও করেছে অন্যান্য মিস্ত্রির সঙ্গে। নতুন বাড়িতে বসত করতে ভালোই লাগে। তাই সে প্রথম দিকে চলে এসেছে। সতেরো নম্বর রুমের সে প্রথম ভাড়াটিয়া। মাঝে মাঝে গ্রামের বাড়িতে যায়, আবার আসে। গ্রামে সে জমি-জমাও করেছে কয়েক বিঘে। পুকুর কেটে নতুন টিনের ঘর জুড়েছে এবার। ছেলে বিয়ে দিয়ে দেশে রাখবে, সেই দেখবে জমি-জমা। দেশের গেরস্থ ঘর, ভালো বংশ দেখে ছেলের বিয়ে দিচ্ছে। শহরের বাতাস গায়ে লাগা মেয়ে গ্রামে থাকতে চাইবে না। তাই মোতালেব মিয়ার এই পরিকল্পনা। আপাতত নিজের মেয়েই তার সংসার সামলে রেখেছে।
মোতালেব মিয়ার বুদ্ধি তারিফ করার মতো। শফি মিয়ার বয়স কম হলেও ছেলে আছে দু’টো। আলাল আর হেলাল। ঢাকায় আসার পর শফি মিয়া প্রায়ই প্রাণের টানে চলে আসে মোতালেব মিয়ার বাসায়। কারণ, এখানে এলে বউ আর তার ছেলে দু’টোর নগদ খবর সে পেয়ে যায়। এখানে গ্রামের প্রায় সবারই যাতায়াত। শফি মিয়া আরও পাঁচ-ছজন নিয়ে থাকে এক রুমে। সারবাঁধা ঘর সেখানেও। এক একখানা কাঁথা নিয়ে সেখানে তারা কারও একজনের ছেঁড়া মশারির মধ্যে কয়েকজন করে কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকে। একঘেয়ে কোনো কোনো সন্ধ্যার পর শফি মিয়া মেস থেকে নিজের ভাগের খাবার খেয়ে আসে। আবার কোনোদিন মোতালেব মিয়ার বাসা থেকে খেয়ে যায়। কোনোদিন আবার মোতালেব মিয়ার স্ত্রী’র সাধাসাধিতে খেয়ে আসার পরও খেয়ে যায়। আর তার রেশ থাকে নিজের তেলচিটে কাঁথার ভেতর ঢুকেও। ঘুম না আসা পর্যন্ত।
মোতালেব মিয়ার খবর পাঠাতে হয় না শফি মিয়ার স্ত্রী’কে। মোতালেব মিয়ার বাড়ি আসার বাতাসে ভাসা খবর পেয়ে নিজেই দৌড়ে আসে হাজেরা। এসে বলে, আলালের বাপে টাকা-পয়সা দিছে চাচা? মোতালেব মিয়া হাজেরাকে টাকা নিতে পরে আসতে বলে। হাজেরা বোঝে ঘরের ভিড় কমলে আসতে হবে। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই মোতালেব মিয়া বলে, ‘এই কয়দিনের মইদ্যে আমরা আবার যাইতাছি, তোমাগেরে শফি লইয়া যাইতে কইছে। ঘর ভাড়া লইছে আমাগো বাসারতন এট্টু দূরে।’
হাজেরার মুখে খুশির ঝিলিক। কিন্তু সূর্য ঢাকা মেঘের মতো মুখ করে বলল, ‘কিন্তুক চাচা, আমার আলালের যে জ্বর! টাকাপয়সার অবাবে ওষুদ-পত্তি কিনবার পারতাছি না। ‘আমাগো যাইতে দেরি আছে আরও কয়দিন, নতুন গরের পিড়ি বান্দন লাগবো। তোমার চাচায় নকসি কইরা দরজা দিবো। এর মইদ্যে তোমার পোলা বালো অইয়্যা যাইবোনে। অষুদ-পত্যি খাওয়ায়া গিয়া!’
নিজের তালাবন্ধ ঘরের জিনিস-পত্র থেকে অনেকদিনের ধুলোবালি ঝারার কাজে ব্যস্ত মোতালেব মিয়ার স্ত্রী চানবানু বলল হাজেরাকে। এদিকে পাশের ঘর থেকে তাদের জন্য খাবার বয়ে আনছে মেয়ে তহুরা। মোতালেব মিয়া মেয়ে বিয়ে দিয়েছে নিজের ভাইয়ের ছেলের সঙ্গে। বাড়ি এলে এটুকু যত্ন-আত্তি যেন পায়। গরম ভাতের গন্ধে নিজের পেটে মোচড় নিয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকা সঙ্গত মনে করে না হাজেরা। সে গাছ-গাছালির ফাঁক-ফোকর গলিয়ে দ্রুত বাড়ির পথ সংক্ষেপে করে। আলালের জ্বর কমে না। যে ক’টা টাকা শফি মিয়া পাঠিয়েছে তাতে কিছু সদাই-পাতি কিনে বাকিটা গেছে ডাক্তার দেখাতে। ওষুধের জন্য আর থাকল না কিছু। ডাক্তার বলে গেছে, টাইফয়েড হয়েছে ছেলেটির। মোতালেব মিয়া দুইদিন দেরি করছে। আর কত? খালি মাথায় পানি দিয়ে হচ্ছে না কিছুই। লঞ্চের ভাড়া নেই। কূল-কিনারা না দেখে শেষে হাজেরা মোতোলেব মিয়াকে বলল, ‘চাচা লঞ্চের খরচডা আপনে দ্যান, অসুইক্যা পোলাডারে আমি ডাকায় লইয়া চিকিচসা করাই। নাইলে পোলাডা আমার মরবো।’
মোতালেব মিয়া আমতা আমতা করে রাজি হলো। আর তার উপর ভর করে ছোট ছেলে বেলালকে নিয়ে হাঁড়ি-পাতিল কাঁথা-বালিশ যা বাঁধাছাদা করল হাজেরা, তার সবই নিল না। এ-বাড়ি ও-বাড়ি রেখে দিল কিছু। কারও একার ঘরে বেশি কেউ রাখতে চায় না। আবার হাজেরা এতটুকু ঘরও রাস্তার খাস জমিতে, শফি মিয়ার নিজের হাতের তালপাতার ছাউনি। এরকম খালি ঘর ক’দিনেই উপড়ে দেবে দৃশ্যমান ভূতেরা। এতে কারও কিছু করার নেই। ঝাঁকা ভরে পাতা কুড়োতে যারা আসে তারাও একখান একখান করে তালপাতা খুলে নেবে ছাউনি থেকে।
একজন একখানা নিয়েছে ধরা পড়লে, আরেক জনের নেওয়াটা নির্বিঘ্ন হয়। ক্ষুধাভর্তি পেটের মানুষেরা কখনো পরস্পরের সমব্যথী হয় না। নিজের এক ওয়াক্তের ভাত ফোটাতে অন্যের শেকড় উপড়ে আনতে পারে এরা।
লঞ্চে ওঠার অনেকক্ষণ আগের থেকেই একবারও চোখ খোলেনি আলাল। হাজেরা ক’দিন থেকে বলে আসছে, ‘তাড়াতাড়ি সাইরা ওঠ বাজান! আমরা তর বাপের কাছে ডাকা যামু।’ আলাল তার গলা শুকিয়ে আসা ভাঙা ভাঙা স্বরে মাকে আশ্বাস দিয়েছে, ‘দেইখ্যো কাইলই আমি বালো অমু, আমার কাইলতন আর জ্বর আইবো না।’ যে ছোঁয় তারই ঘাম ছোটে, এমন জ্বর নিয়ে আলালকে পাঁজাকোলা করে লঞ্চে তুলে দিয়ে গেছে শফির ছোট ভাই গ্রামে সেও থাকে শফি যেভাবে থাকত। দিনটায় ছেলের কোঁকানো শুনে আশ্বস্ত থেকেছে হাজেরা। মাথায় পানি দেওয়ার সুযোগ নেই। শেষে মোতালেব মিয়া কোমরের গামছাখানা নিজেই খুলে ভিজিয়ে এনেছে। হাজেরাকে বলেছে, ‘এইডা দিয়া তোমার পোলার মাথাডা চাইপ্যা রাহো!’ ভেজা গামছাখানা ছেলের মাথায় কপালে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিতে দিতে নিজের চোখে দুটি ঘুমে বুজে এল। হেলাল পড়ে আছে মোতালেব মিয়ার স্ত্রী’র গায়ের ওপর। লঞ্চের টিমটিমে বাতিটি শুধু জেগে আছে সবাইকে দেখার জন্য। রাত কত হবে অনুমান করতে পারে না হাজেরা। তার ঘুম ভেঙে গেছে, কিন্তু এভাবে বসে আছে কেন ঠাহর করতে পারে না সে চোখ খোলে। পা দু’খানা ঝিম মেরে আছে, পা থেকে ভারটিকে নাড়া দিতেই চিৎকার করে ওঠে, ‘চাচি, আমার আলালে শক্ত অইয়া গ্যাছে ক্যা চাচি?’
মোতালেব মিয়ার স্ত্রী বসে বসে ঢুলছিল। হাজেরার চিৎকারে আচমকা জেগে ওঠে, শক্ত-লম্বা হয়ে যাওয়া শিশুটির আপাদ-মস্তক দ্রুত হাতড়ে তাড়াতাড়ি হাজেরার মুখ চেপে ধরল। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, চুপ কইরা যা পোড়ামুহি! মাইনষে টের পাইলে লাশ পানিতে ফালাইয়া দিব! হাজেরা আলালকে কোলের উপর মাথা রেখে শোয়ানো থেকে ধীরে ধীরে টেনে বুকে এনে চেপে বসে থাকল। কেউ যেন তার কোল থেকে আলালকে কোনোদিন কেড়ে নিতে না পারে। যেন এভাবে বুকে চেপে রাখলে পৃথিবীর আর কোনো শক্তিই তাকে মায়ের কোল ছাড়া করতে পারবে না। হাজেরার আচমকা কান্নার বিলাপে দু-একজন যারা চোখ খুলে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল, তারা আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল। মোতালেব মিয়া আর তার বাকি সময়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ভয়ানক বিষয়টি আলোচনা করতে লাগল খুব নিচুস্বরে। হেলাল দু-একবার নড়েচড়ে উঠলেও আবার ঘুমিয়ে গেল। মোতালেব মিয়ার স্ত্রী তাকে কিছুটা চেপে বসে আছে, যেন তার ঘুম ভেঙে না যায়।
সামাদ মণ্ডলের কাপড়-চোপড়ের পোটলার ভেতর পুষ্প, বাপ-বেটা দু’জনের চোখ বাঁচিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছিল মাতিয়ারের আনা আরেকটি পোটলা। মতিয়ার তা ওর হাতে তুলে না দিলেও, ব্যাগের মুখ ফসকে যেটুকু বেরিয়ে আসছিল তাতেই পুষ্প বুঝেছিল ওগুলো ওর জন্যই আনা। মতিয়ার কেমন উসখুস করছিল পুষ্পকে দেখে। হাতে ধরিয়ে দেওয়ার সাহস তার হয়নি। বিদেশ থেকে আসা মানুষগুলোর চেহারায় প্রথম দিকে একধরনের চেকনাই থাকে। দরিদ্র এলাকায় এমন মানুষেরা ঢুকলে সবাই তাদের আপাদ-মস্তক সমীহের সঙ্গে লক্ষ করে। তার উপর আবার বিদেশি জিনিসের ঘ্রাণ! সবাই সেখানে ভুরভুর করতে থাকে। পুষ্প ঘোমটা টানেনি এমন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে। বরং কোমরে আঁচলের মতো দুপুরের রান্নার ব্যস্ত আয়োজনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল। বাড়ির মানুষ একবার রান্নাঘর আরেকবার বাপ-বেটার মুখোমুখি বসার ঘর একাকার করে ফেলতে লাগল, আসল কথা, পোটলা। ওই পোটলা খুললে তবেই কৌতূহল নিবৃত্ত হয়। যে যার কাজে মন বসাতে পারে।
বাড়ি থেকে ক’কদম হেঁটে বড় রাস্তায় গিয়ে রিকশায় উঠতে হয়। ‘আমিনা ভিলা’র সব ধরনের বয়সী মহিলাদের প্রায় সবাই দাঁড়িয়ে গেটটি ধরে থাকে, তাদের কেউ একজন বলে ফেলে, ‘যাউক অসুইক্যা মানুষডা ইবার এট্টু আরাম পাইবো। খাওনডা বালো পাইলে বাঁইচ্যা যাইবো। পোলাডা আওনে বালোই অইছে!’ শেষে ওই একজনের সঙ্গে কণ্ঠ মেলায় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা অনেকে। তবে পুষ্প ভিতরে দাঁড়ানো। জটলার পাশে। সামাদ মণ্ডলের রিকশা চোখের আড়াল হওয়ার আগেই মহিলারা ফিরে দাঁড়ালো, কেউ একজন বলল ‘পোলা দেহি কোনো কথাই কইলো না তর লগে? পোলার বাপেও তো কিছু কইয়া গেল না, কবে আইয়্যা তরে নিবো, কী করবো? পুষ্প সবাইকে আর্বজনার মতো ঝেড়ে দরজা পর্যন্ত আসার আগেই হুহু করে কেঁদে উঠল। কীসের এ কান্না কেউ জানে না। পুষ্প নিজেই কি জানে? তবে এটা সে জানে সামাদ মণ্ডল আর ফিরে আসবে না। তাকে দায়মুক্ত করে দিতেই আসবে না। তবু মানুষটার উপর তার অভিমান হলো, তাকে কার কাছে রেখে গেল? হঠাৎই মায়ের জন্য মনটা কেমন করে উঠল পুষ্প’র। সে বালিশের মুখ চেপে দু’হাতে খামচে ধরল জীর্ণ কাঁথার বিছানাটি।
সকালে লঞ্চ সদরঘাট টার্মিনালে ভিড়লে যাত্রীদের সঙ্গে জগন্ময়ীর মতো আলালকে কোলে নিয়ে নেমে গেল হাজেরা। আগে ভীত-সন্দিগ্ধ মোতালেব মিয়া আর হেলালকে হাত ধরে পরে নামছে তার স্ত্রী। সবাই রিকশা-ভ্যানের কাছে এসে দাঁড়াল, মোতালেব মিয়া আজিমপুরের উদ্দেশে একটা তিন চাকার ভ্যান এমনভাবে দামাদামি করতে লাগল, যেন সব জীবিত মানুষ যাচ্ছে। লাশের কথা শুনলে ঠেকিয়ে ভাড়া গোনাবে। হাজেরার মুখ সেই যে বন্ধ করে দিয়েছে মোতালেব মিয়ার স্ত্রী চানবানু, ভয়ে সেও আর ওর মুখে চোখ পাতছে না, শেষে কেঁদে উঠে সবখানে হাঙ্গামা বাঁধায়।
লাশসহ দু’জন মহিলাকে গোরস্থানে রেখে, শিশু হেলালকে নিয়ে চলে গেল মোতালেব মিয়া। হেলালকে বাসায় রেখে, শফি মিয়াকে খুঁজে গোরস্থানে ফিরে যেতে যেতে বেলা তখন ঢলে পড়েছে। শফি মিয়া পথে আগেই কেঁদে-কেটে একসা হয়েছে বোঝা যায়। খবর গোপন করা যায়নি তার কাছে। গোরস্থানে পৌঁছে সে একখণ্ড কাঠের উপর রাখা ছেলের লাশের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। মোতালেব মিয়ার স্ত্রী তাকে টেনে সরাতেই সে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগল। মোতালেব মিয়া এখন সান্ত্বনার খেই হারিয়ে ফেলেছে। কারণ আসল কাজ বাকি। কত টাকা যাবে কাফন কিনতে, কত যাবে টাকা গোর খুঁড়তে, আর কত যাবে গোসল দিতে, এর কিছুর দর কষাকষি হয়নি। তবু শফিকে তুলে বলতে লাগল, ‘ওয়্যার মার দিকি চাইয়্যা দেহো! বুহি পাষাণ বাইন্দ্যা আছে! আর তুমি তো বাপ।’
শফি তক্ষুনি চোখ খুলল না। উঠল আরও পরে। এখানে যারা লাশের সঙ্গে আসে, তারা বাড়িতেই লাশের উপর অশ্রু-শোকের অনেকটা নিপাত করে আসে। তাই শফির অতটা শোক ওখানে সবাইকে আবার কিছুটা কাতর করে তুলেছে। মোতালেব মিয়ার স্ত্রী’র বারবার চোখ মোছার সঙ্গে তার মতো এর ওর কাছ থেকে পান চেয়ে মুখে পুরছে। দু’কাপ চা কিনে খেলো দু’বারই নিজের আঁচল খসিয়ে। দু’বারই হাজেরাকে সেধেছে নম্রভাবে, ‘খা বউ! যা যাওনের তা তো ছাইড়্যাই গ্যাছে। ওয় তো আর ফিরবো না। রাইততন কিচ্ছু প্যাডে পড়ে নাই তর।’ হাজেরা কোনো কিছুই বলেনি মোতালেব মিয়ার স্ত্রীর কথায়। সে বসে একমনে তাকিয়ে আছে গামছা দিয়ে ঢেকে রাখা বস্তুটির দিকে। যা সে কবে কখন থেকে আগলে আছে তা আর এখন তার মনে নেই। মোতালেব মিয়া শফি মিয়াকে নিয়ে গোরস্থানের লোকদের সঙ্গে যখন কথা পাকাপাকি করে ফেলল, তখনই তখতা খণ্ডসহ প্রায় হেঁচকা টানে আলালের লাশ দু’জন আধাবয়সী মানুষ এসে তুলে নিয়ে গেল। যেন এখন ওদেরই জিনিস। ওরা এখন যত্ন নিয়েই বাকি কাজ সমাধা করবে। প্রয়োজনমতো যারা দোয়-দরুদ পড়ে, মুখে শোক ঘনায়।
সারবাঁধা সবার সঙ্গে এবার হাজেরাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। তবে শোকের কোনো ছাপ তার কপালে নেই। সে দাঁড়িয়ে আছে। শফি মিয়া একবারও স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেনি। তাকে ধরে কাঁদেনি। যেন নিজের যেটুকু বিলাপের কমতি ছিল তাই একা একা আগে পুষিয়ে নিয়েছিল। গোরস্থানের লোকের সঙ্গে মোতালেব মিয়া আর শফি মিয়া মুঠো মুঠো মাটিতে ভরে দিল আলালের কবর। উঁচু হয়ে ওঠা কবর পেছনে ফেলে ফিরে আসতে আর একবার কেঁদে সয়লাব হলো শফি মিয়া। মোতালেব মিয়া দু’খানা রিকশা করে নিজে স্ত্রীসহ উঠে পড়ল, আরেকটিতে শফি মিয়া আর হাজেরাকে তুলে দিয়েছিল। দুটি রিকশাই গোড়ান ‘আমিনা ভিলা’র উদ্দেশে নেওয়া। শফি বাসা নিয়েছে আরও কম ভাড়ায়, আর একটু দূরে। যেখানে এখনো গ্যাস পৌঁছায়নি। লাকড়ি কিনে রান্না করতে হবে।
হাজেরা রিকশা থেকে নেমে স্বামীর সঙ্গে হেঁটে এসেছে। মোতালেব মিয়ার মেয়ে আগেই সবার জন্য রান্না করে রেখেছিল, সে হেলালকে গোসল করে খাইয়ে ঘরে বসিয়ে রেখেছে। শফি মিয়ার আবার কান্না আর বিলাপে হেলালও এই প্রথম প্রাণ খুলে কাঁদল। কারণ, মোতালেব মিয়া তাকে এখানে রাখতে এসে তার মেয়েকে হেলালের মরে যাওয়ার কথা বলেছে। আগে সে গোরস্থান পর্যন্ত ঘুরে এলেও, কারও মরণ টের পায়নি। তাদের বাপ-বেটা দু’জনের অশ্রুতে নতুন করে আবার ভিজে উঠছে ‘আমিনা ভিলা’রও অনেকের চোখ। তাদেরই কেউ একজন অনেকক্ষণ থেকে খেয়াল করে মোতালেব মিয়ার স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বলে উঠল ‘ও বইন, পোলার মায়ে কান্দে না!’
চানবানুর এতক্ষণে ভয় ভেঙে গেছে, সে হাজেরার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, ‘ইবার এট্টু কাইন্দ্যা হালকা অ বউ! এবার এট্টু কান!’
দু’পা ঝুলিয়ে চৌকির উপর বসে থাকা হাজেরার হাতে তখনও তার সদ্য মৃত সন্তানের তেলচিটে গেঞ্জি আর প্যান্ট। সে যেভাবে বসেছিল, একটুও না নড়ে সেভাবেই বসা থেকে বলতে লাগল ‘ক্যা, কান্দুম ক্যা? কী অইছে অগো? ওরা এত কান্দে ক্যা?’ প্রথম কেউ কেউ, পরে সবাই একসঙ্গে বলে উঠল ‘বেডি পাগল অইয়্যা গ্যাছে রে…!’ শফি মিয়া সন্তানের শোক ভুলে মুহূর্তেই স্ত্রী’কে দু’হাতে জাপটে ধরে বলতে লাগল, ‘কান হাজেরা! একবার কাইন্দ্যা উঠ! তর পোলাডারে কেমনে মাডির নিচে থুইয়া আইলি মনে কর! মনে কর…।’
রাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে আজ আর নিজের জন্য নিচে আলাদা বিছানা করতে হলো না। খাটের উপর কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে থাকল। যেখানে এতদিন সামাদ মণ্ডল একার কুণ্ডলিতে রাত পার করে দিত। কিন্তু আজ রাত গভীর হয় না। চোখও খোলা। বাইরের চেঁচামেচি। রাত বারোটা পর্যন্ত কলের কাছে হৈ চৈ। এরপর সমস্ত রাত ধরে তো আছেই একের পর এক মানুষের প্রতি প্রকৃতির ডাক! সকালে কখন ঘুম আসে টের পায় না পুষ্প। সমস্ত শরীর তখনো জড়িয়ে আছে আসন্ন শীতের পরশ। ঘুম ভাঙে লতিফার ডাকে। লতিফার ভাইটিও পড়তে আসে ওর কাছে। সেই সুবাদে ঘরে ঢোকা। দুঃখগুলো ফসলের মতো মনের গোলায় তোলার আগে পুষ্প’র কাছে ঝেড়ে বলা ইদানীং তার আরেক নেশা হয়ে গেছে। লতিফার বয়স ওরই মতো। পেটে বিদ্যেও প্রায় পুষ্প’র সমান। কিন্তু সবার চোখে ওর কথাবার্তা চলাফেরা পুষ্প’র থেকে সবকিছুতে আলাদা।
চোখের পানিতে কাজল ধুয়ে যায় লতিফার, মাঝে মাঝে দুধ পড়ে বুক ভাসে। তবু ডগডগে একটা টিপ পরে বাইরে না বেরুলে চলে না লতিফার। লিপস্টিকের টকটকে জেল্লার এতটুকু রাত অব্ধি আর কোথাও অবশিষ্ট থাকে না। যে রাতে লতিফা ঘরে না ফেরে, সে রাতের ভোরে লতিফার কদর ওর ঘরের মানুষের কাছে বেড়ে যায়। কারণ, এ পথে রোজগারের প্রতিদ্বন্দ্বীও কম নয়। আর এইসব এ-বাড়ির কারও অজানা থাকে না। তাদের অনুমানকে খোলাসা করে দেয় শরিফা। শরিফা লতিফারই বোন। লতিফার ছোট তমিজা, তার ছোট শরিফা। শরিফাই ঝগড়া লেগে সব ফাঁস করে দেয়। না হলে কে জানত তমিজাকে নিয়ে লতিফার স্বামী সটকে পড়েছে! ওদের কথা কাটাকাটির বিপজ্জনক সময়ে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে ওদের মা এসে গলা চেপে ধরে শরিফার। ঝাঁটা, বেলুন, খুন্তিতে মেয়ের কিশোরী শরীরটাকে কেচে ফেলে সে। কিন্তু ধনুক ছিলা তীরের মতো বিপজ্জনক যা, তা মানুষের কানে ঢুকে গেছে আগেই। রহমত উল্লাহও এ নিয়ে কথা তোলে না। বরং ওদের দু’বোনের নধরকান্তিতে সে আশার আলো দেখতে পায়। ওদের কাছ থেকে ভাড়া তুলতেও ওর ভোগান্তি কম হয়। ‘সময়েতে, অসময়ে কামও সারণ যায়’ এটা অবশ্য মনের একেবারে ভেতরকার কথা রহমত উল্লাহর।
ক’দিন আগে রাত-দুপুরে পাশের বাড়িতে নান্টুর মার কান্না পুষ্পকে ধস নামিয়ে দিয়েছে। এরপর থেকে ভীষণ মনে হয়েছে, ডেকে কথা বলে। কিন্তু ডেকে কারও কাছে যাওয়াও তো সহজ নয়! নিজের মায়ের মুখখানা বড় মনে পড়ছে। এই বছরখানেক সময়ের মধ্যে একবারও মার মুখখানা দেখা হয়নি। মা যে ভালো নেই, তা ওর চেয়ে আর কেউ ভালো জানে না। একমাসের ভাড়া শোধ না হতেই আরেক মাস এসে হামলে পড়ে। তার ওপর আবার অসুস্থ একটা মানুষের ভার। অনেকদিন পর বাড়ির ভেতর সকালের দিকেই ফিরোজের ঘোরাঘুরি করতে দেখে এই প্রথম ডেকে ঘরের সামনে দাঁড় করাল পুষ্প, বলল, আমি ক’দিনের জন্য আমার বাড়ি যাব, কিন্তু আমার দেরিও হয়ে যেতে পারে। তাই ঘর ভাড়ার টাকাটা নিয়ে যান! পুরোনো স্মৃতি মনে পড়েই হয়তো, ফিরোজ অবচেতনে বলে ফেলল— ঠিক আছে এসেই না হয় দেবেন।
—কিন্তু দশ তারিখ পার হয়ে গেলেই তো রহমতুল্লাকে দিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেবেন।
—না, দেবো না।
—তার বিনিময়ে আবার কী মূল্য চেয়ে বসবেন? ক্যাকটাসের মতো ক্ষীণ হাসি ফোটে পুষ্প’র ঠোঁটে। কষ্টের স্বেদঝরা।
—কী মূল্য দিতে পারেন আপনি? সহসা রগচটা উত্তর দেয় ফিরোজ।
—কী নেন না আপনি? বলেই পুষ্প আবার বলে, ‘রোদে দাঁড়িয়ে কথা না বলে ঘরে এসে বসবেন? ছোট হলেও আপনাদেরই তো ঘর!
পুষ্প সরে দাঁড়ালে ফিরোজ ঢুকে পড়ে। পুষ্প বসতে বলার আগেই স্টিলের নতুন চেয়ারখানায় সে একাই বসে বলে উঠল, ‘কী নিই না মানে?’ পুষ্প কিছুই না বলে, বিছানার নিচ থেকে টাকাগুলোর ভাঁজ খুলে সবচেয়ে বড় নোটটি বের করল। তারপর কপাল কুঁচকে বলল, এই টাকাটা চেনেন? এটা কিন্তু আগে আপনার কাছেই ছিল! এই দেহেন রহমতুল্লা আঁকাবাঁকা অক্ষরে আপনার নাম লিখে রেখেছে। বান্ডিলে কত টাকা ছিল তাও লেখা আছে। আপনাদের এ-বাড়ির ঠিকানাও লিখেছে। বান্ডিলের এটা প্রথম নোট ছিল বোধহয়।
—লিখেছে তো হয়েছে কী? আর এটা যে আমারই হাতে থাকতে হবে এর কোনো মানে আছে? রহমতুল্লার কাছ থেকে আপনার হাতে আসতে পারে না? খেইহীন বিষয় নিয়ে, একজন সস্তাদরের ভাড়াটিয়া মহিলার কাছ থেকে প্যাঁচাল শুনতে ভালো লাগে না ফিরোজের। পুষ্প কথা নিয়ে প্যাঁচে কষতে এমনিতে জোর পায় না। কিন্তু চোরের বড় গলা শুনে, চোরকে সরাসরি ঘায়েল করল অসময়েই। বলল, একশ টাকার এই নোটটি আমি লতিফার কাছ থেকে পাল্টে নিয়েছি। ওটা আপনি ওকে দিয়েছেন।
—আমি দিয়েছি মানে? আর লতিফাই-বা কে? চমকে ওঠে পাল্টা প্রশ্ন করে ফিরোজ।
—লতিফা এ বাড়িরই ভাড়াটিয়ার মেয়ে। আপনি তাকে চেনেন না। চিনলে আপনার এ টাকা তার কাছে হয়তো যেত না। অন্য কেউ পেত। লতিফা এ বাড়িতেই ভাড়া থাকে ওর ছোট দু’টি ভাইবোন আর মা-বাবাকে নিয়ে। বাবা প্যারালাইসিসের রোগী। ওকে আপনি খেয়াল করেননি নিশ্চয়? খেয়াল করলে এমন অমার্জিত কাজটি ওর সঙ্গে ঘটাতেন না।
—‘পুষ্প!’ অনেকক্ষণ ধরে চিলের মতো তাকিয়ে ছিল ফিরোজ পুষ্প’র মুখের ওপরে।
—নামটি জানেন দেখছি! মনেও রেখেছেন। কিন্তু এ-বাড়ির সবাই আমাকে মতিয়ারের মা বলেই ডাকে। যতদিন এ বাড়ি থাকি আপনিও তাই ডাকবেন। কারণ কোনো সাধই কারও বেশিদিন জিয়োনো থাকে না… সাধও লালিত্য চায়!
ফিরোজ পুষ্প’র ঘরে বসে গল্প করছে, খালি দু’জন জোয়ান বয়েসের মানুষ। সবার কৌতূহলী নজর দরজা পর্যন্ত গড়াগড়ি খেলেও সাহসে ভর করে স্থির হয় না কেউ দরজার কাছে। তবু দু’জনার স্বর নিচু। কারণ কারও কারও পা জোড়া দরজার সামনে দিয়ে অযথাই এদিক-ওদিক যাচ্ছে। ফিরোজ অকপটতার ভান ছাড়ে না। পুষ্প বহুদিনের আক্রোশে তাড়িয়ে ধরার মতো আবার চুপসানো বেলুনের মতো ফিরোজের চোখের দিকে তাকিয়ে দ্রুত বলে ফেলল, ‘লতিফাকে আপনি আর আপনার এক বন্ধু, সেই বন্ধুর বাসায় পরপর দু’জন ভোগ করে একশ’ করে টাকা দিয়েছেন। লতিফাই তা আমাকে বলেছে। আসলে কষ্ট যখন ভারী হয়, তখনই মানুষ কাউকে বলে বাঁচে। ওরও অনেক কষ্ট। ওর স্বামী ওর ছোট বোনটিকে নিয়ে পালিয়েছে। দুধের শিশুটিকে পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে গেছে। বাবা পঙ্গু। বাসা ভাড়া, ভাত-কাপড়, কিছু ওষুধের প্রয়োজন… ছোট ভাইবোন… মা… সবকিছু বলে ফেলেছে। আমারও তাই অন্যের চোখ দিয়ে দেখা হলো অন্য আরেকজনকে। যার মুখে নিজের নামটি শুনতে আমি অনেক ক’টা দিন তীব্র অপেক্ষায় কাটিয়েছি। অবশ্য সে বিলাসিতা আমার তখনই ধুয়ে গেছে!
ফিরোজের ঘাম ছোটে, উত্তর দিতে কথা গুছিয়ে উঠতে পারে না পুষ্পের শেষের কথাগুলোর ধারে। ওর আমতা আমতা ভাবটি পুষ্পকে কিছুটা শক্তি জোগায়। সে টাকাগুলো বিছানার ওপর এমনভাবে ফিরোজের হাতে ধরিয়ে দিল, যেন বুঝিয়ে দিল শোনানোর মতো আর কথা নেই। এখন যেতে হয়। এক ফুঁয়ে নেভা অন্ধকার চোখে ফিরোজ পুষ্প’র ঘর থেকে নেমে গেল। যেতে যেতে তার অযথাই টাইয়ের নব ধরে টানাটানি, আর তার ন্যূব্জ ভাবটি পুষ্প’র নজর এড়াল না। অনেকদিনের পুষে রাখা অপমানের যন্ত্রণায় অন্যের দম্ভ থিতু করে দিতে যে সতর্ক প্রহরীকে সে সৃষ্টি করেছে নিজের ভেতরে, তারই হাতে অব্যর্থ তীরের চকচকে ফলার মতো বড় বিপজ্জনক ঠেকে নিজেকে।
ফিরোজ বেরিয়ে যেতেই একে একে অনেকে এসে দরজা আগলে দাঁড়ায়। বড়দের থম ধরে থাকা অবস্থা দেখে ছোটদের চোখে ভয়ার্ত ভাব ভেসে ওঠে। মধ্যবয়সিনী কারও সহমর্মিতার স্বর শোনা যায়— ‘কী কইলো মা তোরে বাড়িওয়ালার পোলায়? জোয়ান বয়স্যা মাইয়্যা…।’
নিজের দু’হাতে তোলা দরজার ঠাস্ শব্দটি নিজের দু’কানে বেজে ওঠায় বিমূঢ়তা ঘুচে যায় পুষ্পের। কিন্তু বিমূঢ়তা ঘোচে না বাইরের মানুষদের। সবার অমঙ্গলসূচক কথা কান থেকে তাড়াতে তাড়াতে ব্যাগটি গুছিয়ে নেয় সে। তারপর দরজা খুলে দ্রুত পায়ে আজিজ মণ্ডলের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সায়রা বানুকে সামনে পেয়ে বলে ওঠে, ‘বুবু আমি আমার মায়ের কাছে যাচ্ছি!’
ডগডগে সূর্য। গেটের কাছে গড়াচ্ছে সোনার পাতের মতো চকচকে হেমাঙ্গ তারই আভা। মন টেনে নিয়ে যায় স্মৃতির আলপথ। ওর বুকের কোথাও চরের মতো জমাট হতে থাকে ক্ষিপ্র হওয়ার নেশা, যা সব শঙ্কাকে বহমান নদীর মতো তীব্র ঢেউ হয়ে ধুয়ে নেয় অবিরাম ধারায়।