একটি ছোটপত্রিকার সম্পাদক প্রথম প্রেম নিয়ে একটি গল্প লিখে দিতে বলেছেন। খুব খেটেখুটে গল্পটা লিখে পাঠানোর পর মনে পড়ল, মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি। ওই গল্পের প্রেমটা দ্বিতীয় ছিল! প্রথম প্রেম যখন অনুভূত হয়েছিল, তখন আমার বয়স আট। ওই যে ঊনসত্তরে যখন চাঁদের মাটিতে মানুষের পা রাখার খবর শোরগোল ফেলেছিল।
যা হোক, হিসাবমতে তখন আমার বয়স আটই হয়। কিন্তু এখনকার চেয়ে তখনকার শিশুরা খোলা পরিবেশে মানুষ হওয়ার কারণে সম্ভবত তাদের সংবেদনশীলতা এখনকার চেয়ে তীক্ষ্ন ছিল। না-হলে এখনকার আট বছরের শিশুর তো এই অনুভূতি হওয়ার কথা নয়! আমরা তখন খুলনার দৌলতপুরে। ওখানে আমাদের পাশের বাড়ির আকতার নামে পনেরো-ষোলো বছরের এক ডাঙর ছেলে সব সময় আমাকে টিজ করত! পানিতে নামলে হৈচৈরত এক দঙ্গল ছেলেমেয়ের ভিড় থেকে আমাকেই ঠ্যাং ধরে সে টেনে পানির অনেক ভেতরে নিয়ে কচলাকচলি করত। তখন এতে আমার দম যায় যায় দশা হতো! শেষপর্যন্ত ওকে আমার যমের মতো ভয় নয় শুধু, কেঁচোর মতো ঘেন্নাও হতো।
একবার কী করলাম, আকতারের একটা বিড়াল ছিল। ভীষণ আদর করে পুষত সে। আকতারকে শোধ নিতে সেই বিড়ালকে ধরে এনে ভাড়াটিয়া চলে যাওয়া এক খালি ঘরের আড়ার সাথে বেঁধে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে পিটিয়ে মেরেই ফেললাম।
মরে যখন গেল, সে মরা বিড়াল দেখে আমার মা’র আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হওয়ার দশা! মা আমাকে বকতে বকতে বলতে লাগল, দেখিস, আকতার কী করে! মা’র ভয় পাওয়ার কারণ আমরা তো আমরা, আমাদের বাড়িওয়ালাদের থেকেও আকতাররা ওখানে প্রভাবশালী।
তবু মা’কে তো বলতে পারি না, ও আমাকে কিছু একটা করে বলেই তো আমি তার প্রতিশোধ নিলাম!
সত্যি সত্যি কিছুক্ষণের ভেতর আকতার কেঁদেকেটে হাপুস চোখে সেখানে এসে হাজির! পুঁচকেপাচকাদের কেউ একজন তাকে গিয়ে নিশ্চয় বলে দিয়েছিল। না-হলে লাশ গুম করার আগে সে এল কী করে, আজও ভেবে পাই না! আর বন্ধু-সতীর্থদের ভেতরই যে বিশ্বাসঘাতক থাকে, তাও আমার সেই তখনই জানা হয়েছে।
আকতার কারও সাথে কোনো কথা না বলে, হাউমাউ করে কেঁদে উঠে তার বিড়ালের লাশ দু’হাতে তুলে নিয়ে চলে গেল। এরপর আমি আর পারলে ঘর থেকে বেশি দূরে যাই না। পুকুরে গোসল করতে তো যাই-ই না। কিন্তু অনেকদিন পর, পরিস্থিতি একটু থিতিয়ে এলে এক অসময়ে, যখন পুকুরে কেউ ছিল না, তেমন এক টইটুম্বর লগ্নে পুকুরের পাড় দিয়ে যেতে আমাকে যেন সে পুকুর তার সমস্ত জলের স্ফটিক ইশারায় আয় আয় করে ডাকতে লাগল।
পানির প্রতি আমার অসম্ভব একটা টান ছিল। যা এখনো আছে। আমি সুযোগ পেলেই মা’কে লুকিয়ে ইচ্ছেমতো ডুবিয়ে, সাঁতার কেটে, পুকুরপাড়ে খুলে রাখা শুকানো প্যান্টটা পরে বাসায় ফিরতাম। মনে করতাম মা টের পাবে না। কিন্তু শরীরের খরখরে অবস্থা দেখে মা বিষয়টা বুঝতে পারত। আর ইচ্ছেমতো মার দিত!
সেই দুপুরেও আমি আমার হাফপ্যান্টটি সিঁড়িতে রেখে সাঁতরে একটু শুধু কয়েক গজ দূরে মাত্র গেছি। তখনো একটি ডুবও দিইনি। এর ভেতর দেখি, বিশাল পুকুরটির যেই পারে আকতারদের বাড়ি, সেই পাড় থেকে বড় বড় পাতার একটি ডুমুর গাছ এমনভাবে পুকুরের ভেতর ঝুলে পড়েছে, যেন কলঙ্কের ভারে সে ডুবে মরতে চাইছে! ছাতার মতো সেই ডুমুর গাছের একেকটি পাতার ফাঁক দিয়ে দেখি জীবনানন্দ দাশের কবিতার চিত্রকল্প সম্বলিত বিশাল এক পেঁচার মতো আকতারের ভয়ঙ্কর নেকড়েমুখ ঠা ঠা রোদে নতুন টিনের মতো চকচক করছে!
ভয়ে আমার বুক চৈত্রের মাঠের মতো চৌচির হয়ে গেল অথৈ পানিতে থেকেও! আমি কীভাবে যে পুকুর থেকে উঠলাম, মনে নেই। তারপর সিঁড়ি থেকে প্যান্টটা হাতে তুলে নিয়ে বাসার দিকে ভোঁ দৌড় দিলাম। আর মুহূর্তে একটা তীর ছুটে এসে আমার বাম হাঁটুর নিচে বিঁধে গেল!
এখন বুঝি তীরটা আকতার অত মসৃণ করে আমার বুকে মারার জন্যই পাকা বাঁশের শক্ত চটা চেঁছে বানিয়েছিল। তীরটা আমার হাঁটু থেকে টানাটানি করে খুলতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। চৈত্রের সে দুপুরটা এত নিঝুম ছিল, যে একটা মানুষ সেখানে কোথাও ছিল না, যে দৌড়ে এসে আমাকে সহযোগিতা করে! এখনো মনে আছে, রক্তশূন্য মুখ কিন্ত পা রক্তে মাখামাখি। উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতেই আমাকে ঘিরে ধরল অনেকে। আমি শুধু বলতে পারলাম, আকতার…।
ক’দিন ধরে বাড়ি সরগরম হয়ে থাকত মানুষে, এর ভেতর একদল আমার আব্বাকে উসকে দিত মামলা করতে। আরেক দল হাতে-পায়ে ধরত, আমরা যেন কোনো আইন-আদালত না করি!
আয়ুর শেষ সীমানায় হলেও আমলটা তো তখন পাকিস্তানের। একটু রক্তারক্তিতেই তখন খবর হয়ে যেত। তাই শালিস-দরবার, মাফ চাওয়া-চাওয়ির ভারে পরিবেশ ভারী হয়ে উঠল। আকতারকে এ জীবনে আর আমি চোখের সামনে দেখিনি। ওকে বোধহয় কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
এই আকতারেরই বড় ভাই হায়দার। নায়কের মতো ছিল চেহারা, চাল-চলন। তখন মাত্র কলেজে উঠেছে। খুলনার মহসীন কলেজে পড়ত। তাকে দেখলে আমার খুব ভালো লাগত। সেদিন রাতে হারিকেন হাতে আকতারের মা-বাবা আর সেই বড়ভাই হায়দার এসেছিল আমাকে দেখতে। আর আমার তখন মনে হয়েছিল, ভালো করেছে, আকতার আমার পায়ে তীর মেরেছে! না-হলে হায়দারকে কোনোদিনও এত কাছে থেকে দেখতে পারতাম না। কোনোদিনই সে আমার পায়ে হাত দিয়ে দেখত না!
হায়দারকে যেদিন কাছে থেকে দেখলাম, বুঝলাম কাছে থেকে দেখতে সে আরও সুন্দর! কী সুন্দর করে সবার সাথে কথা বলছে! আমাকে চোখের ঝিলিক মেরে বলল, ‘তুমি কেন ওর বিড়াল মেরেছ? সেটাও কিন্তু কম অপরাধ নয়! ওটা ওর খুব ভালোবাসার বিড়াল ছিল। খেতে বসে সে নিজের ভাগের মাছ-মাংস লুকিয়ে বিড়ালকে খাওয়াত। আকতার তোমাকে তীর না মারলে আমি তোমাকে জেলে ঢুকিয়ে দিতাম। ও, তোমার তো আবার জেল হতো না। তুমি ছোট মানুষ!’
হায়দারের এমন অনুযোগে তার প্রতি আমার ভালোলাগাটা আরও গাঢ় হয়ে উঠল। মাত্র আট বছরের মানুষ প্রেমে পড়তে পারে এ আমার বিশ্বাসই হয় না! কিন্তু হায়দারের কথা মনে হলেই বিশ্বাস হয়, আমি মাত্র আট বছর বয়সে তার প্রেমে পড়েছিলাম!
আমি সম্পাদককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, প্রথম প্রেমের গল্প আহ্বান করে বই করলে না কেন? তিনি উত্তর দিয়েছেন, আপনি ছাড়া দুই বছরে কারও সাহস হয়নি ‘প্রথম প্রেম’ নিয়ে গল্প লেখার! একমাত্র আপনিই সেই বীর যিনি গল্পটি লিখেছেন!’ ছোটকাগজের সম্পাদকের কথায় এত বছর পরেও আমি সেই হায়দারকে আরেকবার ধন্যবাদ দিলাম।
আকতারের দাদি মারা গেলে ওর দাদা আরেকটা বিয়ে করেছিল। সেই মহিলার কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। তার মাথায় ছিট ছিল। কখনো তাকে পাগলামি করতে দেখিনি অবশ্য। তবু পাগল না হলে আকতারের মার হাতে বড় বড় চেলাকাঠের অমন মার খেয়েও, কেন সে পড়ে থাকত ওই বাড়ি? তবু কেন হায়দার, আকতার ও ওদের ছোট ভাই রিয়াজুলকে সে অকারণে অত ভালোবাসত? কেন কারও কিছু কুড়িয়ে পেলে তাকে খুঁজে জিনিসটি পৌঁছে দিয়ে আসত? পাড়া-প্রতিবেশীও সবাই তাকে পাগলি বলেই ডাকত। যেহেতু আকতারের বাবা স্বয়ং তার মা’র অবর্তমানে বাবার বিয়ে করে আনা এই দ্বিতীয় স্ত্রীকে খুঁজে না পেলে নিজেই ‘পা-গ-লি-ই…’ বলে সুর করে ইতিউতি ডেকে বেড়াত! আর তার সে সৎ মা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে ছুটে কাছে এসে খিনখিনে কণ্ঠে বলত, ‘আমি তো এইহানেই আছি!’
পাগলি ওদের সব কাজ করে দিত। কুড়াল দিয়ে আস্ত গাছ থেকে লাকড়ি বের করা থেকে, পুকুরে নিয়ে আকতারের মার একেক বোঝা পানও নরম ন্যাকড়া দিয়ে ডলে ডলে ধুয়ে দিত। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা; আজও পান ধুতে হলে আমি সেই আকতারের দাদির মতো করে ধুই। যাকে হায়দার ছাড়া আর সবাই বলত পাগলি। হায়দার একাই বলত দাদি! হায়দারের পৌরুষদীপ্ত চেহারার সাথে এইটুকু ভব্যতা যুক্ত হওয়ায়ই কি হায়দারকে আমার অত ভালো লাগত কিনা, জানি না!
পাগলির হাত-পা সব সময় সাদা দগদগে থাকত। মানে সারাক্ষণ ক্ষার ছাই দিয়ে থালা-বাসন মাজা, কাপড়-চোপড় ধোয়া আর কাঁচা মাটির বাড়িঘর লেপাপোছা করতে করতে হাতে ঘা হয়ে থাকত!
সত্তরের শেষের দিকে আমরা ঢাকা চলে আসি। এর ভেতর খুলনার সাথে আর কোনো যোগাযোগই নেই। ২০০৯ সালে কোরবানি ঈদের রাতে আমার ছোট মেয়ে ফারজানা আমাকে বলল, ‘আম্মা, আমি কাল আমার অফিস থেকে খুলনায় যাব, তুমি কি আমার সাথে যাবে? গেলে সকালে রেডি থেকো!’
সকালে ঘুমের ভেতর টের পেলাম আমার ছোট মেয়ে ফারজানা স্যুটকেস টেনে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি মাথা তুলে বললাম, তুমি না বললে আমাকে নিয়ে যাবে?
ফারজানা বলল, তুমি তো রেডি হওনি? আমাকে নিতে নিচে গাড়ি চলে আসছে!
আমি মুহূর্তে শাড়িটা পাল্টে ব্লাউজ পাল্টাতে আর সাহস পেলাম না। চাবিটা নিচে রিসেপশনে রেখে আমার ছোটবোন নাসিমাকে ফোন করে বললাম, আধকাঁচা মাংসসহ ঘরের যা অব্যবস্থাপনায় আছে, সব ঠিকঠাক করে রেখে যেতে।
শ্যামলী থেকে বাসে উঠে বিকেল নাগাদ খুলনায় নেমে, ওখানকার ওয়েস্টিন হোটেলে গিয়ে উঠলাম। কিছুক্ষণের ভেতর দেখলাম সেখানে খুলনা ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার সৈয়দ মিজানুর এসে হাজির। বয়সে তিনি আমার সমান। তবু তাকে চাচা ডাকি। কারণ কবি সৈয়দ হায়দারের তিনি সম্পর্কে ভাতিজা! তাই ভাতিজা না ডেকে চাচাই ডাকি। তিনি ভীষণ ব্যস্ত তখন। তার ছেলের তখন প্রাইমারি বৃত্তি পরীক্ষা। আগামী দু’দিনেও সময় দিতে পারবেন না। তাই একঘণ্টা সময় আমার জন্য হাতে নিয়ে এসেছেন।
এই লেখা সেই তখন লিখলে অনেকটা ঠিকভাবে লিখতে পারতাম। তবু একটু একটু করে মনে পড়ছে, চাচা একঘণ্টা চুক্তিতে রিকশা ভাড়া করে আমাকে কোথায় কোথায় নিয়েছিলেন।
ঢাকা থেকে যেতে যেতে পথে তার সাথে ফোনে নিশ্চয় কথা হয়েছিল। না-হলে আমি গিয়েছি, সে খবর তিনি পেলেন কী করে! তবে এটা ঠিক মনে আছে, সেই একঘণ্টা সময় অচেনা রাস্তা আর নদীর পাড় ধরে অভূতপূর্ব কেটেছিল।
পরদিন সকালে আমাকে তেমনি আমার ঘুমের ভেতর আমার ছোট মেয়ে বলতে লাগল— আম্মা, আমি আমার কলিগদের সাথে বেরিয়ে যাচ্ছি। ফিরতে রাত হবে! তুমি তোমার ছোটবেলায় এখানে কোথায় কোথায় ছিলে, খুঁজে বের করে বেড়িয়ে এসো!
একা কোথায় ঘোরা যায়? হোটেলের নিচে রিসেপশনে গিয়ে রিসেপশনিস্টদের বললাম, আমি এখানে কোথায় ঘুরতে পারি? ওরা আমাকে বলল, এখান থেকে বিশ টাকা রিকশা ভাড়া দিয়ে রূপসা ব্রিজের গোড়ায় চলে যান। তারপর ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে দেখতে দেখতে পার হয়ে নদীর ওপারে চলে যান। সারাদিন ওপারের শান্ত পরিবেশে ঘোরাঘুরি করেন। আসার সময় নৌকোয় করে পার হয়ে এই পাশে আসেন।
সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ওই পারে একাই ঘুরে বেড়িয়েছি। বসে থেকেছি। দরিদ্র দুটি পরিবারের উঠোনে বসে তাদের সাথে গল্প করেছি। আসার সময় হেঁটেই ব্রিজ পার হয়েছিলাম। কিন্তু আবার এপাশে আসতে ডিসির বাংলোর সামনে যখন নৌকা ভেড়াল, তখন আসন্ন বিকেল। ডিসির বাংলো তখন খালি ছিল। নৌকা থেকে নামার পর আমি তাই অভয় মনে ওই বাংলোর শূন্য আঙিনাতে ঘুরছিলাম। শানবাঁধানো একটি বকুল গাছের গোড়ায় দেখলাম লেখা রয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র তার ‘কপালকুণ্ডলা’ এই বকুল গাছের নিচে বসে লিখেছেন! আমি অভিভূত হয়ে ক’খানা সরু ডাল ভেঙে মহৎ স্মৃতি হিসাবে হাতে নিলাম। তারপর সন্ধ্যা নামতে নামতে হোটেলে ফিরে গেলাম। পরদিন তেমনি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে একটি রিকশা নিলাম। দৌলতপুরের কোন বাড়িতে ছিলাম তা তো ভুলে গেছি। জানতাম না, সে বাড়ি খুঁজতে হলে রিকশাওয়ালাকে কী বলতে হতো।
আগের দিন ডিসির বাংলো থেকে যখন ওয়েস্টিন হোটেলে যাই, রিকশাওয়ালাকে বলেছিলাম, আমি আগামীকাল দৌলতপুরে যেতে চাই। কিন্তু এলাকা চিনি না। তবে মুক্তিযুদ্ধের আগে দেখে গিয়েছি তো, বিশাল এলাকাজুড়ে ভাড়া দেওয়ার গোলপাতার ঘর। মাঝখানে দীঘির মতো একটা পুকুর। আর একটি মাত্র টিউবওয়েল ছিল। রাস্তার পাশে একটা রাইস মিল ছিল। বাড়িটাকে আতিয়ার মিয়ার বাড়ি বলত। বাড়িওয়ালার কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না।
আমারই সমবয়সী রিকশাওয়ালা বলল, ‘হ, চিনছি! আতিয়ার মিয়া যুদ্ধের আগেই আরেকটা বিয়ে কইরেছেলো। এহন আতিয়ার মিয়া নাই। এই ঘরে পাঁচ ছাওয়াল-মাইয়ে। তারা এ্যাকাকজন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অইছে। বালো আছে তারা!’ আমি বললাম, ধুর তুমি চেনোনি! কারণ ওই বাড়িওয়ালা তার পাটরানির মতো স্ত্রীর দাপট টপকে আরেকটা বিয়ে করতে পারে, এ তখনকার যে কারও ভাবনার অতীত।
বিশাল এলাকাজুড়ে গোলপাতার ঘর হলেও, আতিয়ার মিয়া ও তার স্ত্রী জাহানারা বেগম নিজেদের জন্য দু’রুমের একতলা একটি বিল্ডিং করেছিলেন। যা আমার চোখের সামনেই ক’দিনের গড়ে উঠেছিল। রুম দুটির ছিল বিশাল এক বারান্দা। সামনে ছিল গোলাকার এক পুরোনো গোলাঘর। অন্যপাশে গোয়ালভরা গরু। বাড়িওয়ালাকে আতিয়ার মিয়া বলে সবাই ডাকত। কিন্তু তার নাম ছিল আতিয়ুর রহমান মিয়া। খুব সুদর্শন দেখতে ছিলেন তিনি! বড় চাকরি করতেন। ছিলেনও স্ত্রী’ বিপরীত স্বভাবের, খুবই মিষ্টভাষী। তাদের কোনো ছেলেমেয়ে না থাকায়, ছোটবেলায় ওই বাড়িতে কাজ করতে আসা বাড়ির চাকর যখন বিয়ের উপযুক্ত হলো, তাকে বিয়ে দিয়ে দুধে আলতা গায়ের রঙ, ফুটফুটে চেহারার যে বউ এনেছিলেন তারা। বিল্ডিংয়ের দু’টি রুমের একরুমে জাহানারা বেগম আর আতিয়ুর রহমান থাকতেন, আরেক রুমে সেই রাখাল কাম রাইস মিলের চালক মোর্শেদ তার স্ত্রী ও অন্য দুটি সন্তানকে নিয়ে থাকত। আর মোর্শেদের প্রথম ছেলে তমাল থাকত আতিয়ুর রহমান ও জাহানারা বেগমের মাঝখানে। গদির ওপর আরেকটি গদি দিয়ে তমালের বিছানা হতো। সাথে রাবার ক্লথও যখন বিছানোর কথা মনে পড়ছে, তার মানে, তমাল অনেক ছোট থাকতেই তার পিতার মনিব দম্পতির মাঝখানে জায়গা করে নিয়েছিল।
বেবী সাইকেলের সাথে নিত্যনতুন খেলনা ও কর্তা-কর্ত্রীর অখণ্ড মনোযোগের জন্য তমাল ভাড়াটিয়াদের শ’খানেক ছেলেমেয়ের মধ্যে মধ্যমণি হয়ে থাকত! তমালের বাপ সর্বসাকুল্যে ও বাড়ির কেয়ারটেকারের পদমর্যাদা লাভ করলেও তমাল ছিল জাহানারা বেগম ও আতিয়ার রহমান মিয়ার পুরোপুরি সন্তান বাৎসল্যে!
মোর্শেদ ভাইয়ের সব সময় শুধু মুখে নয়, মনে হতো সারা শরীরে একটা উৎফুল্ল ভাব ফুটে থাকত। সুন্দরী বৌ। বছর বছর বাচ্চা হচ্ছে বলে পিতা-মাতারও অধিক মনিব দম্পতি তাতে প্রসন্ন হচ্ছেন, নিঃসন্তান তারা চোখের সামনে নতুন বাচ্চকাচ্চার মুখ দেখছেন বলে। অথচ ফর্সা, শক্তপোক্ত, চেপ্টা শরীরের লড়াকু চেহারার মোর্শেদ ভাইয়ের সেই খালি গা। মুখে পান। কোমরে গামছা বাঁধা। কখন কীসের কোন কূল টলে ওঠে আর একমাত্র তাকেই যে সব রক্ষে করতে হয়! সম্মুখসমরে ঝাঁপ দেওয়া সৈনিকের মতোই ছিল তার সব সময়ের ভাব!
রিকশা খুলনা ওয়েস্টিন হোটেল থেকে দৌলতপুর আসার পর কোথায় যাবো বুঝে উঠতে না পেরে পার্কে নেমে গেলাম। কিন্তু সেখানে জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েদের আচরণ দেখলাম ঢাকার চেয়ে খারাপ। সে অবস্থায় বেশিক্ষণ বসা গেল না। তখন আমার মামাতো ভাই বিএম এনামুল হক ছিলেন রংপুরের ডিসি। আমি তাকে ফোন করে বললাম— দাদা, তুই যে একবার যশোর থেকে বিরাট একটা রুই মাছ নিয়ে দৌলতপুর আমাদের যে বাসায় এসেছিলি, সেই বাসাটা দৌলতপুরের কোথায়?
দাদা বলল, তুই এখন কোথায়?
আমি বললাম, দৌলতপুর পার্কে। তারপর দাদা কোনদিকে যেতে বলল, আমি না বুঝেই আরেকটা রিকশা নিলাম। এবং কয়েক গজ গিয়ে অনুমান করে এক গ্রিলের দোকানের গিয়ে বাড়ি ও বাড়িওয়ালার বর্ণনা দিতে লাগলাম। একজন বলল, আমি চিনি! সে হাতের কাজ ফেলে আমাকে নিয়ে ত্যাড়াব্যাঁকা এক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে লাগল। আমি ভাবতে লাগলাম, আমি যে বাড়ির কথা বলছি, সে বাড়ি ছিল মেইন রোডের পাশে। এই ছেলে নিশ্চয় আমাকে গলির গলি তস্য গলির ভুল কোনো বাড়িতে নিয়ে তুলবে! তবু তার পেছনে হাঁটতে লাগলাম। বেরিয়েছিই তো পাব না জেনে! তাহলে নতুন যে কোনো ঠিকানায় পৌঁছালেই হলো।
ছেলেটি অতঃপর যে বাড়িতে আমাকে নিয়ে থামল, সেটা আভিজাত্যহীন, অতি নিম্নবিত্ত এলাকার টিনশেড দুটি রুম আর তার বারান্দার দু’পাশে আরও দুটি পকেট রুম। বারান্দার সে পকেট রুমের একটি থাকার রুম। আরেকটিতে রান্নাবান্নার কাজ করা হয়।
বাইরে মানুষের সাড়া পেয়ে ভেতর থেকে যে ক’জন একসাথে বেরিয়ে এল, তার একজনকে চিনতে পেরে বুকের ভেতর তিরতির করে উঠল। মুহূর্তে তিরতির নদীতে বানডাকা জোয়ার এল। চোখ উপচে পানি উঠছে আমার। কথা বলতে গেলে গলা দিয়ে কথা না বেরিয়ে কান্না উথলে উঠছে। কিন্তু সেই পাটরানির মতো গা-ভরা ভারি গয়নায় সেজে থাকা অথচ প্রচণ্ড মেজাজিই নয় শুধু, বদমেজাজিই যাকে মনে হতো, তাকে এখানে খালি গা আর সাধারণ একখানা মোটা কাপড়ে দেখে আমার কেন কান্না আসবে? আমি তো তার শ’খানেক ভাড়াটিয়ার ছেলেমেয়ের সাথে তার কাছে পোকা-মাকড়ের অধিক কিছু ছিলাম না!
নিজের কান্নার জন্য নিজেই লজ্জা পাচ্ছিলাম। কথা জড়িয়ে যাওয়ার জন্য আমি বেশ ক’বার বলার পর তিনি আমাকে চিনলেন। কারণ এত বছর পর চেনার জন্য সেই ছোটবেলায়ও তিনি আমাকে সেভাবে দেখেছেন, সেভাবে বলতে হবে তো!
তাদের বাড়ির একটা পাশের পুরোটা আমরা ভাড়া নিয়ে থাকতাম! সেখানে ছিল আমাদের ‘সিমোডিন ইউনানী দাওয়াখানা’ নামে ওষুধ তৈরির বিরাট কারখানা এবং রাস্তার পাশের দিকটায় নিজেদের করা বিক্রয় কেন্দ্র। আমার মা’র সাথে জাহানার বেগমের খানিকটা ভাব ছিল। আমার মা অত্যন্ত কোমল মেজাজ ও শিল্পগুণের অধিকারী হওয়ায়, কেন যেন সবাইকে তার কাছে আসতে হতো। আসতেন গা-ভরা গয়নায় মোড়ানো এই জবরদস্ত জাহানারা বেগমও।
গতকাল রিকশাওয়ালা যা বলেছেন, তাই ঠিক। আতিয়ুর রহমান মিয়া আরেকটা বিয়ে করেছিলেন। তারপর সে ঘরের ছেলেমেয়ে বড় হতে হতে বা আগেই মোর্শেদকে তার ছেলেমেয়ে বউসহ বেরিয়ে আসতে হয়েছে। ২০০৯ সালে আমি যখন গিয়েছি, তখন সেই সদা হাসিখুশি, বাড়ি মাতিয়ে রাখা শক্তপোক্ত শরীরের মোর্শেদ পরপারে চলে গেছে।
জাহানারা বেগমের কী নিয়তি, তার নিজের সেই পাকা মহল ছেড়ে দিয়ে তাকে বাড়ির সেই চাকর মোর্শেদের ছেলেমেয়ের সাথে এসেই থাকতে হয়!
আর নিয়তি আমারও! যে আমি গেছি, অতি শিশুকালের শুধু পুরোনো বাড়িটা আর আকতারকে এক নজর দেখার টানে, যে আকতারের ছুড়ে দেয়া তীরের দাগ আমি সারাজীবন হাঁটুর নিচে বহন করছি!
ছোট ভাইবোন সবার বিয়ে হলেও তমাল বিয়ে করেনি। কেন বিয়ে করে না, তা তার মা আর দাদি কেউ কারণ জানে না। তমাল একাই বারান্দার পকেট রুমটিতে থাকে!
তমালের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, জীবনের এত বড় উত্থান আর পতন দেখা দোটানার স্মৃতিতে যে ভোগে, তার তো অনেক কিছুতেই হিসাব না মেলারই কথা! সেখানে বয়স পঞ্চাশ পেরোলেও বিয়ে না করা আর এমন কী!
আমার কান্না দেখে খালাম্মা আশ্চর্যই হয়েছিলেন। হয়তো কোনোদিনই কেউ তার জন্য কাঁদেনি! তার পরিবর্তন ও বিপর্যয়গুলো আমার চোখের সামনে ঘটলে আমারও গা-সওয়া ঠেকত! চোখের সামনে ঘটেনি বলে কল্পিত দানবের জাদুর কুফল মনে হচ্ছিল।
মাটিতে বিছানো পাটিতে সবার সাথে ভাত খেয়ে জাহানারা বেগমকে বললাম, খালাম্মা, আমি একটু আকতারদের বাড়িতে যেতে চাই। খালাম্মা তমালের ছোটভাই শরিফুলকে আমার সাথে দিলেন, আমরা দৌলতপুর ছাড়ার আগে সেই সত্তর সালে যার বয়স বছর তিনেক ছিল। শরিফুল সেই তাদের পুরোনো বাড়ির ভেতর দিয়ে আমাকে নতুন করে সব দেখাতে দেখাতে আনছিল। শরিফুল একজনকে দেখিয়ে ইশারায় বলল, দাদার দ্বিতীয় স্ত্রী!
শরিফুল না বললে, আমি হয়তো আরেকবার ফিরে তাকাতাম না, কাজের লোক মনে করে। আর আমার কাছে মনে হচ্ছিলো, কেন ছোটবেলায় এই একতলা বিল্ডিংটাকে এত রাশভারি মনে হতো? বাড়িওয়ালার গোলাঘর তবু ওটা দেখলে মনে অভূতপূর্ব এক শান্তি অনুভূত হতো! ওই গোলাঘরে কেউ ঢুকলে আমরা হুড়মুড়িয়ে পড়তাম, ওর ভেতর এক নজর অন্ধকার দেখতে। কিচ্ছু দেখা যেত না ওতে। যে ধান বের করে আনত, সে অনুমান করেই ধামাভরে ধান তুলে বাইরে মইয়ের ওপর যে দাঁড়িয়ে থাকত, তার হাতে দিত।
তারপর পুকুরটাকেও আর প্রশান্তির লাগছিল না। সারাজীবন সে কি এভাবেই ছিল নাকি এখন সে জৌলুস হারিয়েছে বুঝতে পারলাম না!
মামাতো ভাই বলছিল, ‘বাড়িটা চিনে যেতে পারলে দেখে আসিস, পুকুরপাড়ে সেই কদবেল গাছটা আছে কিনা! ঠাস করে একটা বেল পড়লে একদঙ্গল ছেলেমেয়ে ওই পুকুরে একসাথে ঝাঁপ দিত বেল তুলতে! পেত একজনে কিন্তু সবাই মিলে ভাগ করে খেত!’ চল্লিশ বছর পর দেখলাম, গাছটি আছে। কিন্তু ন্যাড়াভাব। নেই সেই রাইস মিলটা। যেখানে মানুষ ধান ভাঙাতে এলে আমরা ছোটরা ঢুকে পারলে মোর্শেদ ভাইকে ফাঁকি দিয়ে তুষসহ মেশিন থেকে বের হওয়া একেক মুঠ গরম চাল থাবা দিয়ে নিতাম। তারপর বাইরে এনে এক হাতের থেকে আরেক হাতে গড়িয়ে ফুঁ দিয়ে তুষ বেছে ফেলে সে চাল খেতাম! আহা, অমৃত হার মানে তছরুফ করে আনা সে একমুঠো চালের স্বাদে!
আকতারদের বাড়িতে ঢুকেই হায়দার ভাইকে খুঁজলাম। শরিফুল বলল, এখন তো তাকে বাড়ি পাবেন না। তিনি প্রফেসার মানুষ আবার রাজনীতিও করেন। বললাম, তাহলে বউটা দেখে যাই! ঘরের ভেতর মুখ ঢোকাতেই যাকে নজরে পড়ল; দেখলাম, তাকে দ্বিতীয়বার দেখার মতো কিছু নেই। এতে অন্তরে শান্তি নয় শুধু, মহাপ্রশান্তিই বোধ হলো। মনকে বললাম, বউ যেমনই হোক, তোর কী তাতে? নাকি পুরোনো নেশা এখনো চোখে কুয়াশার মতো রয়ে গেছে! আসছিস তো তার ছোটটাকে দেখতে!
আকতারদের বাড়িতে ঢুকেই দেখলাম খুব হ্যান্ডসাম একজন যুবক উঠোনে দাঁড়ানো। পাশেই বেশ বড়সড় একখানা মোটরসাইকেল। এতে তার সৌন্দর্য যেন আমার চোখের ভেতর বিজ্ঞাপনের মডেলের মতো আরও বেড়ে গেল। জিজ্ঞেস করে জানলাম, ওটা রিয়াজুল। আকতারের ছোট ভাই। বেলা তখন ডুবে গেছে। বাড়ির একপাশে একবোঝা থালাবাসন নিয়ে দেখলাম বয়স্ক একজন মহিলা ছাই দিয়ে মাজামাজি করছে। কিন্তু হাত চলতে চাইছে না তার। দেখলাম, হাত থেকে থালাবাসন পড়ে পড়ে যাচ্ছে! ওটা সেই পাগলি তা ভাবার কারণ ছিল না। কারণ এতদিনে পাগলির বেঁচে থাকার কথা নয়। আমি অনুমান করে বললাম, উনি খালাম্মা না?
রিয়াজুল বলল, হ্যাঁ!
আমি ছুটে সালাম করতে গিয়ে তার হাত-পা গতিক-মতো পেলাম না। বরং বুকের থেকে হাঁপানির শোঁ শোঁ শব্দ শুনে আমি রিয়াজুলকে বললাম, এ কী করছো? বেশ শীত পড়ে গেছে। ওনাকে ওঠাও!
রিয়াজুল বলল, আপা, আমার বউ এগুলো পারবে না। তারও শরীর ভালো নেই!
রিয়াজুলের বউকে ডেকে দেখার রুচি আর আমার থাকল না! আমি তবু বললাম, আকতার কই? শরিফুল আর রিয়াজুল একসাথে বলল, সে আমাদের সবার থেকে ভালো আছে। এই বাড়ি আমাদেরকে ছেড়ে দিয়ে সে নতুন আরেকটা বাড়ি করেছে। আমি রিয়াজুলকে বললাম, বান্দরটা করে কী?
রিয়াজুল বলল, তারা হাজবেন্ড-ওয়াইফ দু’জনই ডাক্তার।
বললাম, আকতারকে ফোন করো!
রিং বাজতেই ফোনটি রিয়াজুল আমার হাতে দিয়ে দিল। আমি বললাম, তুমি একজনকে তীর মেরেছিলে, মনে আছে?
আকতার বলল, মনে নেই আবার! খুব আছে। কিন্তু নামটা ভুলে গেছি।
বললাম, তীর মারার দোষটা এতদিনে ক্ষমা করতে পারলেও নামটা ভুলে যাওয়ার দোষ ক্ষমা করতে পারলাম না!
ওপাশ থেকে ভেসে আসছে, ‘কিন্তু এখন আমি কার সাথে কথা বলছি, যাকে তীর মারছিলাম তার সাথে, নাকি তার মায়ের সাথে?’
মেজাজটা খারাপ ভীষণ হয়ে গেল আমার। মনে মনে ভাবলাম, এই নাম আর কারও আছে নাকি ব্যাটা, যে তুই আমাকে ভুলে যাবি? আমি রিয়াজুলকে ফোনটা ফিরিয়ে দিয়ে শরিফুলকে বললাম, চলো, আমাকে ওয়েস্টিন হোটেলে যেতে একটি রিকশা ঠিক করে দাও!
কতক্ষণ একসাথে ঘুরে, এক পাটিতে বসে ভাত খেয়ে শরিফুলকে মনে হচ্ছিল একেবারে নিজের ভাইয়ের মতো। ওই পরিবারের সবাইকে সেদিনের পর থেকে মনে হচ্ছিল আমাদের নিজের কেউ। পারলে ওদের মনোবেদনা থেকে একবোঝা বেদনা তুলে এনে ওদের ভার কিছুটা হলেও লাঘব করে দিয়ে আসি। আমি ওদেরকে খুব আন্তরিকভাবে ঠিকানা দিয়ে আসছিলাম, যারা ঢাকাতে থাকে, তারা অন্তত যেন আমার বাসায় যাওয়া-আসা করে!
আকতারদের বিধ্বস্ত মাকে যখন দেখলাম, একগাদা থালাবাসন নিয়ে ভরা সন্ধ্যায় ঝামা আর ছাই নিয়ে ঘষাঘষি করছেন, আর কারও তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, সেই দৃশ্য মনে পড়লে আমার আজও বুক ভার হয়ে ওঠে। মনে হয়, উনি অনন্তকাল ওভাবেই বিপর্যস্ত হয়ে কূলহীন অবস্থায় বসে আছেন শীতের অন্ধকারে মশার কামড় খেতে খেতে। যেখান থেকে তার কোনো উত্তরণের আশা নেই! কারণ তার সুস্থ-সবল ছেলে-মেয়ে-বৌয়েরা তাকে একাজ থেকে তরিয়ে নেবে, আসলে সে সাধ্য তাদের তিনিই প্রতিহত করেছেন পাগলির গায়ে হাত তুলে। তাকে খেতে না দিয়ে। তাকে প্রাপ্য সম্মান না দিয়ে। তাই মা ও সন্তান তাদের দু’পক্ষেরই এই অধম পরিণতি অনিবার্য! আর এই সবকিছুজুড়েই পাগলি প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে তাদের সবকিছুতে।
আকতারের মা পাগলিকে চেলাকাঠ দিয়ে পেটাত তো পেটাতই, পোড়া কটা ভাত ছিটিয়ে দিত, এ আমার নিজের চোখে দেখা। ক’দিন পরপর এক বিড়া করে পান পাগলি ধুয়ে নিত, সেই পাগলি দুটো পান সরিয়ে না রেখে এর-ওর কাছ থেকে একটু পানের কোনাকানা চেয়ে খেত। অথচ, পাগলি কারও কাছেই একটু বদনাম করেনি পরিবারের কারওর। একটু অযত্ন করেনি কিছুর। জান দিয়ে তাকে স-ব আগলে রাখতে দেখেছি। আসলেই এটা সুস্থ মাথার মানুষের কাজ নয়!
সে রাতে মেয়ে বলল, কাল আমাদের কর্মসূচি গোপালগঞ্জে। তুমিও চলো। তোমার বাপের বাড়ির থেকে বেড়িয়ে এসো। তাই হলো, খুব ভোরে রওনা দিয়ে মেয়ের সাথে গেলাম। রাতে নতুন বাড়ি ঘোষেরচরে থাকলাম। আগেই দাওয়াত দিয়েছিলেন সৈয়দ মিজান চাচা। গোপালগঞ্জ থেকে সরাসরি খুলনা ইউনিভার্সিটির ভেতর তার বাসায় যেতে হলো। আকাশ ছিল থমথমে। কৃষ্ণপক্ষ চলছিল। তাই খাওয়া ছাড়া ওখানে দেখার কিছু ছিল না! গোপালগঞ্জ থেকে সরাসরি মিজান চাচার বাসায় ঢুকেছিলাম। বেশ রাত হয়েছিল। কিন্তু আগেই যেহেতু দাওয়াত কবুল করা ছিল, না গিয়ে উপায় ছিল না। বারবার চাচাকে বলছিলাম, চাচা, দিনের বেলা এলে, খাওয়ার চেয়ে খুলনা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসটা ঘুরে দেখাই বড় লাভ ছিল।
আমার থেকে বয়সে বেশ ছোট সুন্দরী চাচি খুব সুস্বাদু করে অনেক রকম তাজা মাছ রান্না করেছিলেন। এ লেখা সেই তখন হলে চাচির সেই রান্নাই সাহিত্যের উপাদানে কতরকম বাগাড় দেওয়া যেত!
আর প্রথম প্রেমের ব্যর্থ এমন গল্পে খুলনা ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার এই সৈয়দ মিজানুর রহমান চাচাই কিছুটা রসদে রক্ষে করে রেখেছেন অন্তত।



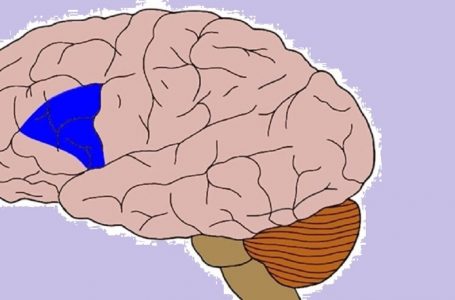



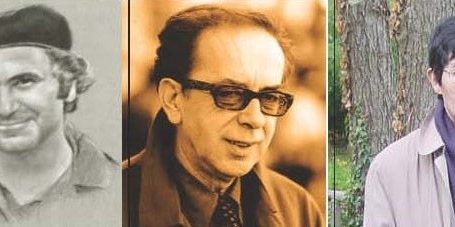




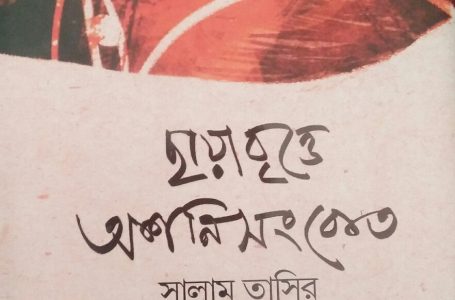


One Comment
[…] দীলতাজ রহমান – দ্বিতীয় প্রেম […]